| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
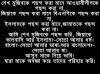 কাউসার আলম
কাউসার আলম
কতজনের কত কিছুই হল আমার না হয় পান্তা ভাত আর নুন, কত কী যে হওয়ার কথা ছিল আমার না হয় পাগলামিটাই গুণ।।
আজ ২৬ শে মার্চ । বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস । ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে হঠাৎ করে থেমে গেল ঢাকা । নেমে এলো কবরের নিস্তব্ধতা । শুরু হয় পাকবাহিনীর বর্বরোচিত এবং কাপুরুষোচিত ক্রেকডাউন । এই ভয়াল ‘কালরাত্রি’র পর রক্তে রাঙা নতুন সূর্য উঠেছিল ১৯৭১ সালের এই দিনে । পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল । বঙ্গবন্ধুর ডাকে উজ্জীবিত বাঙ্গালী ২৫শে মার্চের পর নতুন করে উজ্জীবিত হয় । এ ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জাতি। প্রস্তুত হয় পৃথিবীর ইতিহাসের নৃশংস হ্ত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেয়ার । দীর্ঘ নয় মাস রক্তপাত আর অজস্র প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে প্রিয় স্বাধীনতা । লাল-সবুজের পাতাকা নিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ । এবার জাতি স্বাধীনতার ৪২ বছর পূর্তি পালন করছে।
বীর বাঙ্গালি দেশমাতার জন্য প্রিয়জন, পরিবার, ঘরবাড়ি ছেড়ে অসীম অনিশ্চয়তায় জীবনকে বাজি রেখে রক্তিম পথচলা শুরু করে । এ এক অপার্থিব অনুভূতি, এটিই দেশপ্রেম। যার ফলাফল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। নতুন প্রজন্ম বুকে এমন দেশপ্রেম ধারণ করুক।
বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মফিদুল হক বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ যেমন ছিল কঠিন ও কঠোর লড়াই, যার পেছনে ছিল দীর্ঘ সাধনা ও অধ্যবসায়, সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও নবায়নও তেমনি কঠিন ও কঠোর সাধনার বিষয়। এটা নিরন্তর পরিচালিত এক সংগ্রাম, যা এখন রূপ নিয়েছে নির্মাণ ও বিকাশের, ব্যাপকতর মানুষের জীবনে মুক্তি অর্থবহ করে তোলার বহুমুখী আয়োজন ও প্রয়াসের। আর তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের জন্য বিমূর্ত ধারণা নয়, অতীতের গৌরবের সঙ্গে বর্তমানের করণীয়ের তা বাস্তব সেতুবন্ধ, এই যোগসূত্র নিবিড়ভাবে ধারণ করার মধ্য দিয়ে আমরা পেতে পারি সুন্দর আগামী নির্মাণের প্রেরণা ও শক্তি।' আর এ প্রেরণার শক্তিই হলো আমাদের নতুন প্রজন্ম।
আমার মনে হয় তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে আজও অন্ধকারে। তাদের ধারণা নেই কিভাবে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। আমি অনেক নতুন প্রজন্মকে জিজ্ঞেস করেছি, মুক্তিযু্দ্ধ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা আছে কি নেই। তাদের বক্তব্য, 'বেশি কিছু জানে না, তবে এটুকু জানে ৩০ লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন ।' আবার কেউ কেউ অত্যন্ত সচেতন। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের নতুন নতুন ঘটনা শুনে তা নিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে।
আমরা চাই সকল বিভ্রান্তি দূরে ঠেলে মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ সঠিক ইতিহাসটি বিশ্বের সব নাগরিক জানুক। নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা প্রচুর, আশা অনেক, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তারা জানতে চায়। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই অসাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসমুক্ত, শোষণমুক্ত ও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য তারা সদাজাগ্রত।
মার্চ বা ডিসেম্বর এলেই আমাদের তর্ক জমে ওঠে কে স্বাধীনতার ঘোষক আর কেই বা জাতির পিতা। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখেন এবং লেখার সময় বাটখাড়াটা তার দিকেই ভারী করে দেন। তাই লেখাটা বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে একতরফা হয়ে ওঠে। আবার যে দল ক্ষমতায় আসে সে দল তার হয়ে লিখতে বসে। সত্যিটা কেউ স্বীকার করতে চায় না। ফলে স্কুল-কলেজের কোমলমতি ছাত্রছাত্রী একেক সময় একেক ইতিহাস পড়ে এবং বিভ্রান্ত হয়। বুঝে উঠতে পারে না কোনটা সত্যি।
আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য কিছু বই:
১। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর: একটি নির্দলীয় ইতিহাস— গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি ২০১০, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা। অনেক তথ্য ঘেঁটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন গোলাম মুরশিদ।
২। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের তালিকা
©somewhere in net ltd.
১| ২৬ শে মার্চ, ২০১৩ সকাল ৯:২৩
২৬ শে মার্চ, ২০১৩ সকাল ৯:২৩
কাউসার আলম বলেছেন:
এই গ্রন্থ থেকে একটি নির্বাচিত অংশ এখানে দেয়া হলো।
১৯৭১ সালের মার্চের ২৫ তারিখ রাত একটার অল্প পরেই শেখ মুজিবর রহমানকে সেনারা গ্রেপ্তার করে তাঁর বাড়ি থেকে। গ্রেপ্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লে. ক. জহির আলম খানকে। তিনি তাঁর অধীনস্থ মেজর বিল্লালকে নিয়ে যান ৩২ নম্বরে। জহির আলম তাঁর গ্রন্থ দ্য ওয়ে ইট ওয়াজ (১৯৯৮) গ্রন্থে লিখেছেন যে গ্রেপ্তারের আগে তাঁর সেনাদের ওপর পিস্তলের একটা গুলি ছোড়া হয়েছিল। তার জবাবে তার সেনারা মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি ছোড়ে এবং একটা গ্রেনেড ফাটায়। শেখ মুজিব তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে হাবিলদার মেজর খান ওয়াজির তাঁকে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় দেয়। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। সেখান থেকে আদমজী স্কুলে। তিন দিন পরে পশ্চিম পাকিস্তানে। (গ্রেপ্তারের আগে পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুড়ে সেনাদের প্ররোচিত করা হয়েছিল—ধারণা করি, এ কথা একেবারে বানোয়াট। পিস্তল দিয়ে এক প্লাটুন সৈন্যকে আটকে রাখা যায় না—এটা মুজিবের মতো বিচক্ষণ নেতা কেন, একটি অপরিণত বালকও বুঝতে পারে।) সিদ্দিক সালিকের লেখাতেও কোনো পিস্তল থেকে কোনো গুলির কথা নেই। প্রবেশপথে পাহারাদারদের খতম করে দেয়াল টপকে বাড়ির চত্বরে ঢুকেছিল মেজর বিল্লালের পঞ্চাশ জন সৈন্য। তারপরই তারা গুলি করেছিল স্টেনগান দিয়ে—নানা দিক থেকে। দোতলায় উঠে মুজিবের শোবার ঘরের দরজায় গুলি করে দরজা খুলে সেই কক্ষে ঢুকেছিল তারা। মুজিব তৈরি ছিলেন আত্মসমর্পণের জন্য। (সালিক, ১৯৭৮)
আহমদ সালিমও লিখেছেন যে গ্রেপ্তারের আগে মুজিবের বাসভবনের ওপর নানা দিক থেকে অসংখ্য গুলি ছোড়া হয়েছিল। (সালিম, ১৯৯৭) তাঁকে মেগাফোনে বলা হয়েছিল নিচে নেমে আসার কথা। তিনি তখন কাপড়-চোপড়ের ছোট্টো একটি ব্যাগ হাতে করে আর মুখে পাইপ দিয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। জিপে ওঠার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর ওপর যে শারীরিক নির্যাতন শুরু করে, তার কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন, ডেভিড ফ্রস্টকে। তিনি বলেন,
‘তারা আমাকে ধরে নিয়ে টানাটানি করে। আমার মাথার পেছন দিকে বৃষ্টির মতো ঘুসি মারতে আরম্ভ করে। আমাকে আঘাত করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে। তা ছাড়া, তারা আমাকে এদিকে-ওদিকে ধাক্কা দিতে থাকে।’ (উদ্ধৃত, সালিম, ১৯৯৭)
নিজে ধরা দিলেও মুজিব আগে থেকে অন্য নেতাদের গা ঢাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাজউদ্দীনকে তিনি শহরতলিতে পালিয়ে থাকার কথা বলেছিলেন। (আমীরউল ইসলাম, ১৯৮৮) শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খানকেও তিনি পালিয়ে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যদেরও সম্ভবত বলে থাকবেন। কিন্তু অন্যরা পালালেও তাঁর নিজের পালানোর কোনো উপায় ছিল না। তাঁর মতো একজন নেতাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, পালানোর মতো মনোবৃত্তিই তাঁর ছিল না।
বদরুদ্দীন উমরের মতো কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, এভাবে ধরা দেওয়া তাঁর ঠিক হয়নি। এর ফলে তিনি বিপ্লবের নেতৃত্বে দিতে ব্যর্থ হন। (উমর, ২০০৬) কিন্তু এই সমালোচনাকে যথার্থ বলে মানা যায় না। কারণ, মুজিব চিরদিন সাংবিধানিক রাজনীতি করেছেন, বিপ্লবী রাজনীতি করেননি। তা ছাড়া তিনি সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি যে পাকিস্তানিরা অমন বর্বরোচিত হামলা করে লাখ লাখ লোককে হত্যা করতে পারে। আর ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সত্যিকার নির্ভীক এবং আপসহীন। এর আগে বহুবার গ্রেপ্তার বরণ করেছেন তিনি। কারা বাস করেছেন বহু বছর। কিন্তু গ্রেপ্তারের ভয়ে কোনো দিন তিনি আত্মগোপন করেননি। অথবা তাঁর দল নিয়ে তিনি কোনো দিন কমিউনিস্টদের মতো গোপন আন্দোলনও করেননি।
নিয়াজি ও রাও ফরমান আলী লিখেছেন, তাঁরা মনে করেছিলেন রাজনীতিকদের গ্রেপ্তার করেই স্বাধীনতা আন্দোলন বন্ধ করা যাবে। কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো তা মনে করেননি। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন এর ফৌজি সমাধান। ইয়াহিয়া আগে থেকে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। দু-একবার প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিলেন। যেমন—২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেলদের সভায় তিনি নাকি বলেছিলেন, দরকার হলে ৩০ লাখ লোককে খতম করে দেওয়া হবে। বাকিরা তখন অনুগত ভৃত্যের মতো আচরণ করবে। (রুডলফ রামেল, ১৯৯৬)
এ জন্যই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসেন টিক্কা খানকে। এর আগে টিক্কা খান কঠোর হাতে বেলুচিস্তানের জনগণকে দমন করেছিলেন। সে ‘খ্যাতি’র কারণেই তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল বাঙালিদের দমন ও নিধন করতে। অন্য জেনারেলদের নিয়ে টিক্কা খান ১৮ মার্চ পরিকল্পনা করেছিলেন, মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশকে তিনি ‘বিদ্রোহী’মুক্ত করবেন। ২০ মার্চ এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। (সালিক, ১৯৮৮)
ব্যাপক গণহত্যার মধ্য দিয়ে জনতাকে হতভম্ব ও চুপ করিয়ে দেওয়াই ছিল এই ঝটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্য।
তার জন্য অবশ্য সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিল না। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর (বিডিআর) ও পুলিশকেও দমন করারও দরকার ছিল। মার্চ মাসের গোড়া থেকেই তাই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি কর্মকর্তাদের জায়গায় বসানো হয়েছিল পশ্চিমাদের। বেশির ভাগ বাঙালি কম্যান্ডিং অফিসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল দায়িত্ব থেকে। যেমন—চট্টগ্রামের সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি অফিসার ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ২৪ তারিখে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে আনা হয় ঢাকায়। যেমন—খালেদ মোশাররফকে ২২ মার্চ ঢাকার ব্রিগেড মেজরের পদ থেকে সরিয়ে কুমিল্লায় বদলি করা হয়। যেমন—জয়দেবপুরে শফিউল্লাহর বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসার করে এক পশ্চিমা ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারকে পাঠানো হয় ২৫ মার্চের দু-তিন দিন আগে। যেমন—শাফায়েত জামিলকে কল্পিত ভারতীয় শত্রু দমন করার জন্য কমিল্লা থেকে পাঠানো হয় সিলেটের পথে। (জামিল, ২০০৯)
তা ছাড়া বাঙালি সৈন্য ও সেনাপতিদের রাখা হয়েছিল চোখে চোখে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র করা হয় বহু বাঙালি সেনা-কর্মকর্তাকে। এমনকি অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। নিহতও হন অনেকে।
২৫ মার্চ রাতে সৈন্য বাহিনী ঢাকায় যে হামলা চালায়, তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন সার্চ লাইট’। এ হামলা যেমন অতর্কিত ছিল, তেমনি ছিল বিদ্যুত্ গতির। রাস্তায় বেরিয়ে সৈন্যরা মধ্যরাতের পর থেকেই নির্বিচারে হাজার হাজার লোককে মারতে আরম্ভ করেছিল।
স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্ররা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। সে জন্য বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর ওপর হামলা চালায় সৈন্যরা। তখনকার ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহিরুল হক হল) ছিল ছাত্রলীগের ঘাঁটি—সেখানে সে রাতে অন্তত দু শ ছাত্র নিহত হন। ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং দুই দিন পরে এই হলে গিয়ে তখনো পোড়া কক্ষগুলোয় আধা-পচা লাশ দেখতে পান। দেখতে পান এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ। (ড্রিং, ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৩০. ৩. ১৯৭১) হিন্দু ছাত্রদের ওপর সৈন্যদের আক্রোশ ছিল আরও বেশি। তাদের ধারণা ছিল, জগন্নাথ হল কার্যত অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছে। (সালিক, ১৯৭৬)
রাও ফরমান আলী লিখেছেন, সামরিক অভিযান শুরু হলে এই হল থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। (ফরমান আলী তাঁর গ্রন্থে সত্য কথা কমই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর কথাকে সাক্ষ্য হিসেবে নেওয়ার কারণ নেই। তিনি এও লিখেছেন, ২৫ মার্চ রাতে কোনো ট্যাংক ব্যবহার করা হয়নি।) কিন্তু সে যা-ই হোক, এই হলে সৈন্যরা যাকে পায়, তাকেই হত্যা করে। কালীরঞ্জন শীলের মতো সেখান থেকে দু-চারজন ছাত্রই অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। (কালীরঞ্জন শীল, [রশীদ হায়দার, ১৯৯৬])
ছাত্র ও কর্মচারীদের মৃতদেহগুলো হলের সামনের মাঠে গণকবরে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই গণকরব খোঁড়ায় কালীরঞ্জনও অংশ নিয়েছিল। ক্লান্ত হয়ে সে শুয়ে পড়ায় সৈন্যরা তাঁকে মৃত বলে মনে করেছিল। এই হলে যে আগুন জ্বালানো হয় তা দুই দিন পরেও নিভে যায়নি বলে লিখেছেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা। (বাসন্তী, ১৯৯১)
জগন্নাথ হলের প্রোভেস্ট ছিলেন জি সি দেব (গোবিন্দচন্দ্র দেব)। চিরকুমার, আপন-ভোলা মানুষ। দর্শনের অধ্যাপক। সৈন্যরা তাঁকেও হত্যা করে। জগন্নাথ হলের কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর বাড়িতে থাকতেন অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান আর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। মুনিরুজ্জামানের বাড়িতে ঢুকে সৈন্যরা তাঁকে এবং অন্য তিনজনকে টেনে এনে সিঁড়ির ওপর গুলি করে হত্যা করে। নিচতলায় বাড়ি থেকে বের করে ঘাড়ের ওপর দুটি গুলি করে জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার। তিনি হাসপাতালে মারা যান ৩০ মার্চ। গুলি করার আগে তাঁর কাছে নাম ও ধর্ম কী—তা জিজ্ঞেস করেছিল সৈন্যরা। এমনিতে তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে দয়া হয়েছিল কি না, জানা যায় না। কিন্তু হিন্দু শুনে আর দয়া করতে পারেনি। (বাসন্তী, ১৯৯১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আট-নয়জন অধ্যাপক নিহত হন এই রাতে। এই অধ্যাপকদের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু।
আসলে হিন্দুরা পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ফলে কেবল এই রাতে নয়, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসই হিন্দুদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। (ম্যাসকারেনহ্যাস, ১৯৭১)
নির্মম নির্যাতন করতে পাকিস্তানি সেনারা অকুণ্ঠ ছিল। কিন্তু হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করা, শিশু-বৃদ্ধসহ হিন্দু পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা এবং তাঁদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনা এবং তাদের দোসর রাজাকারেরা একটু বেশি বিশেষ উত্সাহী ছিল। (সরকার, ২০০৬)
বিদেশি সাংবাদিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু-নিধনের কাজ চালানো হয়েছিল পদ্ধতিগতভাবে এবং নীতি হিসেবে। (ডেইলি টেলিগ্রাফে লোশাকের রিপোর্ট, সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইমস, ভারজিন আয়ল্যান্ডস ডেইলি নিউজ, সানডে টাইমস [১৩ জুন], টাইমস [৫ জুন], সানডে টাইমস [১৩ জুন] এবং নিউইয়র্ক টাইমস-এর বিভিন্ন সংখ্যা, অ্যান্টনি ম্যাকারেনহ্যাসের দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ [১৯৭১] গ্রন্থ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) আসলে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে দেশছাড়া করতে। যাতে পূর্ব পাকিস্তান পুরোপুরি মুসলমানদের দেশে পরিণত হয়।
২৫ মার্চ রাতে, কেবল সাধারণ মানুষদের ওপর নয়, প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় বাঙালি নিরাপত্তাকর্মীদের ওপরও। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য, ইপিআর ও পুলিশকে খতম করা ছিল পশ্চিমাদের একটা বড় লক্ষ্য। তাই তারা একযোগে আক্রমণ করে পিলখানার ইপিআর ছাউনি এবং রাজারবাগের পুলিশ লাইনের ওপর। রাত ১২টায় এ দুই জায়গায়ই সেনারা পৌঁছে যায়।
পিলখানায় বাঙালি জওয়ানেরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, কিন্তু বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। আগে থেকেই পশ্চিমা কর্মকর্তা ও জওয়ানদের নিয়ে এসে সেখানে বাঙালিদের দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল। জওয়ানেরা অনেকেই বুড়িগঙ্গার ওপারে গিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। নিহত হয়েছিলেন অনেকেই। রাজারবাগের পুলিশেরা অতি তুচ্ছ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবল যুদ্ধ করেন, কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাধা দিতে পারেননি। এখানে এগারো শ পুলিশ ছিল। তার মধ্যে খুব কমই রক্ষা পেয়েছিলেন। বাকি সবাই নিহত হন। পুলিশ লাইনের একজন মহিলা সুইপার পরে সাক্ষী দিয়েছেন, পরের দিন থেকেই রাজারবাগ পরিণত হয় ধর্ষণকেন্দ্রে। বিভিন্ন বয়সের বাঙালি নারীদের—এমনকি বালিকাদের এনে এখানে ধর্ষণ করে তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। এই মহিলাকেও উপর্যুপরি ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল। (তালুকদার, ১৯৯১)
প্রসঙ্গত বলা দরকার, ধর্ষণের ব্যাপারে পাকিস্তানি সৈন্যরা বিশেষ উত্সাহী ছিল। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে, এ হচ্ছে কাফের নিধনের জন্য ধর্মযুদ্ধ অর্থাত্ জেহাদ। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী জেহাদের মালামাল এবং নারীরা তাদের জন্য ‘হালাল’। কাজেই নয় মাস ধরে লাখ লাখ বাঙালি বালিকা, কিশোরী, যুবতী এবং মধ্যবয়সী নারীদের উপর্যুপরি ধর্ষণ করতে তারা বিবেকের কোনো দংশন অনুভব করেনি। জেনারেলরাও বাদ যাননি। নিয়াজি যেমন—সালিকের ভাষ্য অনুযায়ী, দায়িত্ব নেওয়ার সময়ে জেনারেল খাদিমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কখন তুমি তোমার রক্ষিতাদের আমার হাতে দিচ্ছ?’ সালিক এও স্বীকার করেছেন, ধর্ষণের বহু ঘটনা ঘটেছিল এবং এ জন্য নয়জন জওয়ানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। (সালিক, ১৯৮৮)
ঢাকায় কী ভয়ানক হামলা হয়েছিল তার বর্ণনা দেশি-বিদেশি অনেকেইে দিয়েছেন। এই হামলার ফলে কী ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, তারও। সরকারি হিসাবে বলা হয়েছিল ৪০ জন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতে, এক শ। (সালিক, ১৯৭৬) সায়মন ড্রিং ব্যাংকক থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলেন, ঢাকায় সাত হাজার, দেশের অন্যান্য জায়গায় ১৫ হাজার। (ডেইলি টেলিগ্রাফ, ৩০ মার্চ) ২৭ মার্চের ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড-এর মতে ১০ হাজার। ২৮ মার্চের নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে ১০ হাজার; এ দিনের ডেইলি এক্সপ্রেস-এর মতে ৪০ হাজার। ২৯ তারিখের সিডনি হেরাল্ড-এ লেখা হয়, ১০ হাজার থেকে এক লাখ। নিউইয়র্ক টাইস-এর ১ এপ্রিলের সংখ্যা প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এর সময়ে নিহতদের সংখ্যা ৩৫ হাজার। বাঙালিরা লিখেছেন, হাজার হাজার। কিন্তু সত্যিকারভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি। তবে সব মিলে ঢাকায় যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তার সবচেয়ে ভালো বর্ণনা দিয়েছেন লে. জে. নিয়াজি। তিনি লিখেছেন:
“২৫ মার্চের সেই সামরিক অভিযানের নৃশংসতা বুখারায় চেঙ্গিস খান, বাগদাদে হালাকু খান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যায়।...মেজর জেনারেল রাও ফরমান তাঁর টেবিল ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল মাটি লাল করে দেওয়া হবে।’ বাঙালির রক্ত দিয়ে মাটি লাল করে দেওয়া হয়েছিল।” (নিয়াজি, ২০০৮)
সেনাদের এই ঝটিকা আক্রমণ ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা দেশের বড় শহরগুলোতে একই সঙ্গে তারা আক্রমণ শুরু করে। বিশেষ করে প্রবল যুদ্ধ শুরু হয় চট্টগ্রামে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রসদ আসার এটাই ছিল একমাত্র পথ। সে পথ খোলা রাখাটা ছিল তাদের অগ্রাধিকার। অন্যান্য শহরে সেনাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন ছাত্র-শিক্ষক এবং হিন্দুরা।
বাঙালিরা পঁচিশের রাতে অতর্কিত হামলার কোনো জবাব দিতে না পারলেও পরের দিন থেকে পাকিস্তানি সেনারা কিছু বাধার মুখোমুখি হয়। বাঙালি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় এই হত্যাযজ্ঞে বাধা দেন। তাঁদের বেশি অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; লড়াই করার জন্যে তাঁদের কেউ আদেশও দেননি; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা যুদ্ধ শুরু করেন, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে যাঁরা ছিলেন—জেলা শহরগুলোতে ও সীমান্তে। ‘যার যা কিছু ছিল’ তা নিয়ে ইপিআরের জওয়ান, পুলিশ, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষেরা বাধা দিতে থাকেন পাকিস্তানি বাহিনীকে।