| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
 রেজাউল করিম ফকির
রেজাউল করিম ফকির
অধ্যাপক, কোবে গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়
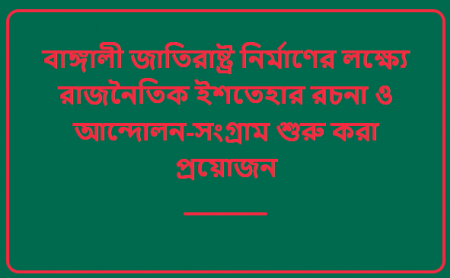
এক. ইতিহাস-বিস্মৃতির রাজনৈতিক কাঠামো
১. বাঙ্গালী জাতির প্রচলিত ইতিহাসের একটি মৌল সমস্যা হলো—এই ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির গর্ব, ঐশ্বর্য ও রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যের দীর্ঘ ধারাটি সম্যকভাবে লিপিবদ্ধায়িত হয়নি। প্রাথমিক কারণটি সুপরিচিত: ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাঙ্গালা সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের পর বাঙ্গালী জাতির কোনো পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
২. আরও দুশ্চিন্তার বিষয়, ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ—এই দীর্ঘ প্রায় চার শতাব্দীকাল মুঘল, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসনের অধীনে বাঙ্গালীরা পরাধীন ছিল। এই তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নিজেদের ক্ষমতাবান বয়ান নির্মাণের স্বার্থে বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসকে আড়াল, অপদস্থ বা বিকৃত করার দিকে প্রবল মনোযোগ দিয়েছে।
৩. ফলে বাঙ্গালার অগণিত শিলালিপি, দলিলপত্র, ইতিহাসগ্রন্থ ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনের অবক্ষয় বা বিলোপ ঘটেছে। বহু স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে, রাজধানী গৌড়-লখনৌটির অবক্ষয় ঘটেছে, নগর ও বন্দরগুলোর নাম-ইতিহাস মুছে দেওয়া হয়েছে কিংবা ভিন্ন বয়ানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
দুই. বৈধতা-রাজনীতি এবং ইতিহাস-বিস্মৃতির তত্ত্ব
৪. ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক শক্তি যে প্রায়শই পূর্ববর্তী রাজত্বের ঐশ্বর্যকে গোপন করতে বা মুছে ফেলতে সচেষ্ট থাকে—এটি ইতিহাসের অভিজ্ঞ সত্য। এই প্রবণতাকে "বৈধতা-রাজনীতি" (politics of legitimacy) বলা যায়, যেখানে নতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বসূরিদের কৃতিত্বকে ম্লান করে তোলে।
৫. উদাহরণস্বরূপ, জাপানে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত মেইজি বিপ্লবের পর নতুন শাসকগোষ্ঠী পূর্বতন তোকুগাওয়া রাজত্বের নানা অর্জন ও রাজনৈতিক স্মারককে চাপা দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছিল। এমনকি সেই শাসনযুগকে "এদো যুগ" নামে পুনর্নামকরণ করা হয়—এদো ছিল তোকুগাওয়া রাজবংশের রাজধানী শহর।
৬. অথচ তোকুগাওয়া রাজবংশ প্রায় আড়াইশ বছর (১৬০৩–১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) জাপানকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তর, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক বিকাশে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল।
৭. বাঙ্গালী জাতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ "ইতিহাস-বিস্মৃতি" কাজ করেছে—যার উৎস বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী শাসন, উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব, এবং নতুন রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব রাজনৈতিক প্রয়োজন। বাঙ্গালীরা প্রায় চার শতাব্দী মুঘল শাসনের (আনুমানিক ১৫৭৩/১৫৭০-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দুই শতাব্দীর কম-বেশি ব্রিটিশ শাসনের (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) অধীন ছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসনের (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ) দমন-পীড়নও সহ্য করতে হয়েছে।
তিন. উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য
৮. এই তিন পর্বেই বাঙ্গালীর স্বকীয় সভ্যতা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় চিন্তার ধারাকে হয়তো উপেক্ষিত, নয়তো চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করার প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে। রাজধানী গৌড়-লখনৌটির অবক্ষয়, প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর নীরব বিলোপ, স্থান-নাম পরিবর্তন—এসব ছিল সেই বিস্তৃত প্রকল্পের অংশ।
৯. অধিকন্তু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পরও স্বাধীন ভারতবর্ষ নিজস্ব জাতীয় বয়ান গঠনে প্রবৃত্ত হয়ে অনেক সময় বাঙ্গালার বিশেষ ইতিহাসকে কেন্দ্র-প্রধান বয়ানে মিশিয়ে দিয়েছে। পূর্ব বাংলার একটি অংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হলেও, পর্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, দলিল সংগ্রহ, প্রত্নস্মৃতি সংরক্ষণ ও জ্ঞান-রাষ্ট্রের (knowledge state) নির্মাণ তৎপরতায় দ্রুত ও সুসংগঠিত অগ্রগতি হয়নি।
চার. বিশ্ব ইতিহাসে জাতীয় পুনর্জাগরণের নজির
১০. তবে মুক্তির পথও ইতিহাসেই বিদ্যমান। চীনের হান জাতি বহু শতাব্দী মঙ্গোল (ইউয়ান, ১২৭১-১৩৬৮) ও মাঞ্চু (ছিং, ১৬৪৪-১৯১২) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে ১৯১২ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পর তারা নিজেদের জাতীয় ইতিহাসকে সুদূর খ্রিষ্টপূর্বকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে।
১১. এই প্রক্রিয়ায় তারা কনফুসিয়াস, লাওৎসে, সান ইয়াৎ-সেন প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবন ও কর্ম থেকে শুরু করে হান, তাং, সং, মিং প্রভৃতি রাজবংশের গৌরবময় অধ্যায়গুলো পুনরুদ্ধার করে।
১২. এই নজির দেখায়—রাজনৈতিক মুক্তির পর সাংস্কৃতিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে একটি জাতির দীর্ঘ ধারার ইতিহাস নতুন করে রচিত হওয়া সম্ভব। হানদের এই উদাহরণ সামনে রেখে বাঙ্গালী জাতির ক্ষেত্রেও—পরাধীনতার ধুলা ঝেড়ে—সর্বাঙ্গীন ইতিহাস পুনর্লিখন আজ সময়ের দাবি।
পাঁচ. পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস নির্মাণের তাত্ত্বিক কাঠামো
১৩. পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস নির্মাণের জন্য কিছু নীতিগত দিক স্থির করে নেওয়া জরুরি। প্রথমত, ইতিহাস শুধু রাজবংশ বা সামরিক লড়াইয়ের তালিকা নয়; বরং একটি জাতির অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-প্রযুক্তি, সমুদ্র-ব্যবসা ও নগর-উন্নয়ন—সবকিছুর কালানুক্রমিক সন্নিবেশ।
১৪. দ্বিতীয়ত, জাতীয় ইতিহাসের বয়ান শুরু হবে প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুদয় থেকে—কারণ রাষ্ট্রিক কাঠামোই একটি জাতির রাজনৈতিক আত্মসত্তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এই প্রেক্ষিতে, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বছরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে ধরে পুনর্লিখন উপযোগী।
১৫. তৃতীয়ত, এই ইতিহাস নির্মাণে প্রত্নতত্ত্ব–শিলালিপি–মানচিত্র–দলিল–ভাষাবিজ্ঞান–লোকসংস্কৃতি–জলপথ–বন্দর–বাণিজ্য–রন্ধন–বস্ত্র–সঙ্গীত—সবকিছুকে এক সূত্রে গেঁথে জাতীয় ইতিহাসের বয়ান পুনর্গঠন করতে হবে। এটিই "দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী তরঙ্গে ইতিহাস দেখা"র পদ্ধতি।
ছয়. প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা: পাল সাম্রাজ্য (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)
১৬. চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমগ্র উত্তর ভারতজুড়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে বরেন্দ্রভূমির ভূমিপুত্র গোপাল গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
১৭. পালদের মাধ্যমে বাঙ্গালা এক নতুন রাজনৈতিক সংহতি, বাণিজ্যপথের পুনরুজ্জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল (নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর বিশ্ববিদ্যালয়সদৃশ প্রতিষ্ঠান), মুদ্রা-প্রশাসন—সব মিলিয়ে স্থিতিশীল রাষ্ট্র-পরিসর পায়।
১৮. উত্তর-পশ্চিমে গুর্জর-প্রতিহার (৭৩০-১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট (৭৫৩-৯৮২), পশ্চিমে চালুক্য (৯৭৫-১১৮ৄ) এবং পূর্বে বাগান (৮৪৯-১২৯৭) সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাল শাসকরা ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করেন।
১৯. এই সময়েই নদীনির্ভর বাণিজ্য, মৃৎশিল্প-ধাতুশিল্প, স্থাপত্যকলা, উপাসনা-সংস্কৃতি ও লোকজ জ্ঞানভান্ডার বাঙ্গালার সভ্যতার মজ্জায় গেঁথে যায়। ধর্মপাল, দেবপাল, মহিপাল প্রমুখের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্য শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও একটি উন্নত সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে ।
সাত. দ্বিতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা: স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত (১৩৫২-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)
২০. পালের পর সেন যুগ (আনুমানিক ১০৭০-১২৩০) ও আন্তঃরাজ্য পর্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে চড়াই-উতরাই এলেও, বাঙ্গালার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়নি। এদিকে মধ্য এশিয়া থেকে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও নানা ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের আবির্ভাব ভারতবর্ষব্যাপী নতুন রাজনৈতিক-ধর্মীয় বয়ান গড়ে তোলে।
২১. বাঙ্গালায় এর ফলশ্রুতি—শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাতের প্রতিষ্ঠা। দিল্লি সালতানাত, দাক্ষিণাত্য ও আরাকান-বার্মার প্রভাববলয় অতিক্রম করে এই সালতানাত প্রায় দুই শতাব্দী বাঙ্গালার স্বাধীনতা রক্ষা করে।
২২. এখানেই "বাঙ্গালা" নামের ভূখণ্ড-পরিচয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়; রাষ্ট্রের নামে দেশের নাম, দেশের নামে জাতির নাম, জাতির নামে ভাষার নাম—এই ধারাবাহিকতায় "বাঙ্গালা দেশ", "বাঙ্গালী জাতি" ও "বাঙ্গালা/বাংলা ভাষা" অভিধাগুলির সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতি দৃঢ় হয়।
২৩. সালতানাত-পর্বে নগর-বন্দর গড়ে ওঠে, সেচ-নৌবহর-করব্যবস্থা সুসংহত হয়, ফার্সি-আরবি-তুর্কি প্রশাসনিক পরিভাষা ও স্থানীয় প্রাক-ইন্দো-আর্য-দেশজ ঐতিহ্যের মিশ্রণে বাঙ্গালার এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-সংস্কৃতি বিকশিত হয়।
২৪. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ প্রমুখ সুলতানদের শাসনামলে বাঙ্গালা সালতানাত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছে। এই সময়ে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় ঘটে যা পরবর্তী কালে বাঙ্গালী জাতিসত্তার মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।
আট. সাম্রাজ্যবাদী পর্ব এবং প্রতিরোধ-সংগ্রামের ধারা
২৫. ১৫৭৩/১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী গৌড় পতনের পর বাঙ্গালা প্রথমে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে এবং ১৭৫৭ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনে নিপতিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালী জনগণ কখনোই এই পরাধীনতাকে মেনে নেয়নি।
২৬. মুঘল আমলের অন্তিম পর্বে বারো ভূঁইয়ার জোট ও ঈশা খাঁর (১৫৩৬-১৫৯৯) নেতৃত্বে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। তার নেতৃত্বে বাঙ্গালার জমিদার ও কৃষকরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।
২৭. ব্রিটিশ পর্বে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন (প্রায় ১৭৬০-১৮০০), সাঁতাল হুল (১৮৫৫), সিপাহি বিপ্লব (১৮৫৭), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯), তেভাগা আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন এবং নানা স্থানীয় প্রতিরোধ—সবই বাঙ্গালার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করে।
২৮. বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু, ড. কিরণ শংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনাধীন ব্রিটিশ বেঙ্গল প্রদেশ থেকে একটি একক ও অখণ্ড স্বাধীন বাঙ্গালা রাষ্ট্র গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।
নয়. তৃতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা: আধুনিক বাংলাদেশ (১৯৭১-বর্তমান)
২৯. দেশভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে এসেও বাঙ্গালী জাতি তাদের স্বাধিকারের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব বাঙ্গালার জনগণ স্বাধীনতার জন্য পর্যায়ক্রমে ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন (১৯৫৪), ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬), গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯) ও অসহযোগ আন্দোলনের (১৯৭১) মাধ্যমে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে।
৩০. অবশেষে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ রাত্রিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙ্গালী জাতির ওপর নির্মম গণহত্যা শুরু করলে, বাঙ্গালী জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাঙ্গালী জাতি বাংলাদেশ নামে স্বাধীনতা লাভ করে।
দশ. চতুর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্বগত ভিত্তি
৩১. এই ধারাবাহিক আলোচনায় তিনটি রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্দিষ্ট স্বরূপ স্পষ্ট হয়: প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা—পাল সাম্রাজ্য (৭৫০-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ), দ্বিতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা—স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত (১৩৫২-১৫৭৩/১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ), তৃতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা—বাংলাদেশ (১৯৭১-বর্তমান)। প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্বও নন্দিত: মহামতি গোপাল, শাহ-ই-বাঙ্গালা সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৩২. কিন্তু সমস্যা হলো—রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৭১-এ অর্জিত সাফল্যকে ইতিহাসের একমাত্র মাইলফলক করে দেখলে—বহুযুগের সঞ্চিত রাষ্ট্র-অভিজ্ঞতা, সমুদ্র-বাণিজ্য, কৃষি-প্রযুক্তি, নগরায়ণ, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা-সাহিত্য-দর্শন—এসবের ধারাবাহিকতা আড়ালে পড়ে যায়।
৩৩. তাই এখানেই "জাতিরাষ্ট্র" নির্মাণের ভাবনাটি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাঙ্গালীদের জন্য ১৯৭১ সালে একটি নাগরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বাঙ্গালী সমসত্ত্ব জাতি হিসেবে স্বীকৃত ও সুগঠিত। সুতরাং ইতিহাস, ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, ভাষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা—সব মিলিয়ে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান।
এগার. চতুর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থার পাঁচটি কর্মধারা
৩৪. "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ" যদি ইতিহাস-অনুগত ও ভবিষ্যৎমুখী নকশায় বিন্যস্ত হয়, তবে চতুর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পাঁচটি কর্মধারা অনুসরণ করা যেতে পারে:
ক. ইতিহাস-নবায়ন ও জ্ঞান-পুনর্গঠন
৩৫. জাতীয় আর্কাইভ ও ডিজিটাল হেরিটেজ প্ল্যাটফর্মে শিলালিপি-দলিল-মানচিত্র-লোককাহিনি-নৃতত্ত্বীয় তথ্যসমগ্র সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে হবে। উপকূল-নদী-বন্দর-বাণিজ্যপথের ঐতিহাসিক ভূগোল মানচিত্রায়ণ করা প্রয়োজন। গৌড়, সোনারগাঁও, পুণ্ড্রনগর, মহাস্থান, মৈনামতি, পাহাড়পুর ইত্যাদি প্রত্নকেন্দ্রগুলোতে সমন্বিত প্রত্ন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই কাজ কেবল অতীতপ্রেম নয়—এটি ভবিষ্যৎনীতি নির্মাণের জ্ঞানভিত্তি।
খ. ভাষা ও জ্ঞাননীতির পুনর্বিন্যাস
৩৬. বাঙ্গালা/বাংলা ভাষার রাষ্ট্রিক-প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাডেমিয়া-শিল্প-প্রযুক্তিতে মাতৃভাষাভিত্তিক জ্ঞান-উৎপাদনের প্রসার ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে বহুভাষিক দক্ষতা (ইংরেজি-আরবি-হিন্দি-চীনা-জাপানি ইত্যাদি) অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করতে হবে। ভাষা-পরিকল্পনায় এই যুগপৎ কৌশল—জাতিসত্তার শিকড় ও বৈশ্বিকতার ডানা—দুটোকেই শক্ত করবে।
গ. অর্থনীতি-প্রযুক্তি-সমুদ্রনীতির পুনর্গঠন
৩৭. পাল-সালতানাত-মুঘল-ব্রিটিশ—সকল পর্বেই বাঙ্গালার জলপথ-নির্ভর অর্থনীতি ছিল কেন্দ্রীয়। আধুনিক বন্দর-নদী-শাসন-কোস্টাল ইকোনমি-উৎপাদনশিল্প-কৃষি-প্রযুক্তি-বস্ত্র ও আইটি-জ্ঞানসেবা—এই খাতগুলোতে দীর্ঘকালীন comparative advantage চিহ্নিত করে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বুঝলে অর্থনীতির ভবিষ্যৎপথও পরিষ্কার হয়।
ঘ. নাগরিকত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র
৩৮. বাঙ্গালী পরিচয়কে কেন্দ্র করে নাগরিকত্বের আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে—যেখানে নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল—সব পার্থক্য সম্মানিত হয়; কিন্তু নাগরিক-স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, পরিবেশ-নিরাপত্তা—এসব মৌল অধিকারে সবার সমভাবে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন—জাতিরাষ্ট্রের স্থিতি আসে অন্তর্ভুক্তি থেকে, সংকীর্ণতার থেকে নয়।
ঙ. স্মৃতি-উৎসব-পাবলিক হিস্ট্রির নির্মাণ
৩৯. পাল প্রতিষ্ঠা-দিবস, স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাতের অভ্যুদয়, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ—এই নোঙর-তারিখগুলোকে রাষ্ট্রীয় ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে শেখানো, উদযাপন ও অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত করতে হবে। জাদুঘর-ঐতিহ্যপথ-নগর দেয়ালচিত্র-ডিজিটাল আর্কাইভ—এসব মাধ্যম তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দেবে।
বারো. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বাস্তবায়ন কৌশল
এই মহান কর্মযজ্ঞে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জ্ঞান-পরিকাঠামো, দলিল-সংরক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ। রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি, মিডিয়া—সবাই মিলে যদি পরিকল্পিত কর্মসূচি নেয়, তবে অদূর ভবিষ্যতেই বাঙ্গালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-গ্রন্থনা, নীতিগত পুনর্জাগরণ এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতিরাষ্ট্রের রূপরেখা বাস্তবের জমিনে রূপ পেতে পারে।
চতুর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকত্বের মর্যাদা, আইনের শাসন, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, জ্ঞান-অর্থনীতির বিকাশ, এবং নিরাপত্তা-কল্যাণ-ন্যায়—এই ত্রিত্ব নীতির বাস্তবায়ন মিলিতভাবে বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে বিশ্বমঞ্চে স্থায়ী ও মর্যাদাবান করে তুলবে।
তের. উপসংহার: দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী তরঙ্গের ইতিহাস পুনরুদ্ধার
৪৩. বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হাজার বছরেরও পূর্বে; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি-রাজনীতির কারণে দীর্ঘ দিন জাতীয় ইতিহাসের উৎসকে সংকুচিত করে কেবলমাত্র সাম্প্রতিক একটি মহান মুক্তিযুদ্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ এই ইতিহাসের শিখর; কিন্তু শিখরের নীচে আছে পাহাড়—পাল, সেন, সালতানাত, উপনিবেশ-প্রতিরোধ, ভাষা-আন্দোলন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
৪৪. এই দীর্ঘ জাতীয়তাবাদী তরঙ্গকে ফিরিয়ে আনাই আজকের কাজ। ইতিহাস পুনর্লিখন তাই শুধু পাণ্ডিত্য নয়—রাষ্ট্রনির্মাণের অবিচ্ছেদ্য ধাপ। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আদর্শকে আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বিত করে, জ্ঞান-অর্থনীতি-প্রযুক্তি-পরিবেশ-সামাজিক ন্যায়ের সমাহারে, "চতুর্থ রাষ্ট্রব্যবস্থা"র দিগন্ত উন্মোচন করা সম্ভব।
৪৫. সেই পথই বাঙ্গালী জাতিকে তার প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে আধুনিক মর্যাদায়, নিজের শক্তিতে, বিশ্বের সঙ্গে সমমর্যাদায় দাঁড় করাবে। ইতিহাস তখন আর কারও বয়ানে ধার করা থাকবে না; নিজের কণ্ঠে নিজের কথাই উচ্চারিত হবে—দলিল-প্রমাণ-দর্শনে সমৃদ্ধ, সংহত ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল।
©somewhere in net ltd.