| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
 র ম পারভেজ
র ম পারভেজ
স্বপ্নময় পথিক। দেখা, শোনা ও জানাগুলিকে ব্লগের পাতায় রেখে যেতে চাই।
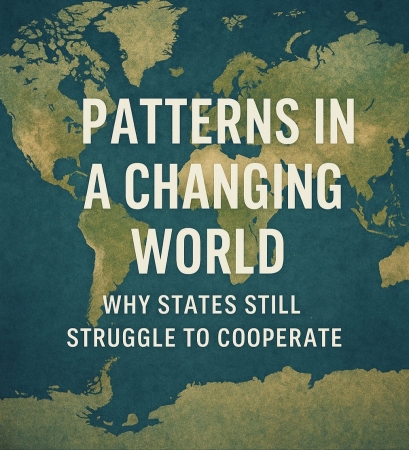
আজকের পৃথিবীটা যেন আগের চেয়ে অনেক ছোট। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যেতে পারেন। মুহূর্তেই টাকা পাঠাতে পারেন যেকোনো দেশে। আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কী ঘটছে, তা আপনি এখনই জানতে পারেন। এমন এক আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে আমরা বাস করছি। তবুও, যুদ্ধ কেন হয়? কেন রাষ্ট্রগুলো এখনও একে অপরকে ভয় করে? কেন প্রতিযোগিতাই সহযোগিতার উপর বিজয়ী হয়ে থাকে?
এই প্রশ্নগুলোই প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—জোসেফ নাই এবং ডেভিড ওয়েলচ (Joseph Nye and David Welch) রচিত Understanding Global Conflict and Cooperation বইয়ে। এই অধ্যায়ের নাম—“Are There Enduring Logics of Cooperation in World Politics?”—তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি আমাদের নিয়ে যায় ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, তত্ত্বের জগতে, আর রাষ্ট্রের মনস্তত্ত্বের গভীরে।
অধ্যায়টি শুরু হয় একটি দারুণ বৈপরীত্য দিয়ে। একদিকে, আমরা ভাবি এখনকার পৃথিবীতে সব কিছু সহজ হয়েছে—বাণিজ্য, যোগাযোগ, প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান। তবুও, যুদ্ধ হয়। সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, শাসনের লড়াই, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি—এসব কিছু চলছেই। নাই এবং ওয়েলচ বলেন—বিশ্ব বদলেছে ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রের আচরণের মূল যুক্তি—ভয়, অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা—অদৃশ্য হয়নি।
ইতিহাসের পেছনে ফিরে দেখা
জোসেফ নাই এবং ডেভিড ওয়েলচ আমাদের তিনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকাতে বলেন:
• সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা, যেখানে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বাকিদের শাসন করে
• সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে আনুগত্য বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত থাকে
• গণতান্ত্রিক-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা, আজকের মতো, যেখানে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নেই
আমরা এখন যে "ওয়েস্টফালিয়ান" রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাস করি, সেটি হলো এক আত্মনির্ভর ব্যবস্থার প্রতীক—যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেই নিজের নিরাপত্তার দায়িত্বে।
বাস্তববাদ বনাম উদারবাদ: দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব
লেখকদ্বয় দুইটি প্রধান তত্ত্ব তুলে ধরেন:
• বাস্তববাদ বলে, রাষ্ট্রগুলো সর্বপ্রথম নিজের অস্তিত্ব ও শক্তিকে রক্ষা করতে চায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এক ধরনের চিরন্তন প্রতিযোগিতা।
• উদারবাদ আশাবাদী। তারা বলে, বাণিজ্য, সংলাপ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিশ্বে শান্তি আনা সম্ভব।
এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব কেবল তাত্ত্বিক নয়—এটি প্রতিদিনের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলে।
চিন্তা বদলে দেয় দুনিয়া: কনস্ট্রাক্টিভিজমের পাঠ
সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল তৃতীয় তত্ত্ব—কনস্ট্রাক্টিভিজম। এটি বলে, রাষ্ট্রের পরিচয়, চিন্তা ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রের আচরণকে গঠন করে।একটি দেশকে কেন হুমকি হিসেবে দেখা হয়, অন্যটিকে মিত্র বলা হয়—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় চিন্তাধারার ভিতরে। এই তত্ত্ব মনে করিয়ে দেয়—ধারণা বদলালে নীতিও বদলায়।
শান্তি সম্ভব, কিন্তু সহজ নয়
অধ্যায়টি কোনো সহজ সমাধান দেয় না। এটি আমাদের চিন্তা করতে শেখায়। বুঝতে শেখায়—শান্তি অর্জন করতে হয়, সহযোগিতা গড়ে তুলতে হয়, এবং সেই আস্থাকে রক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ না আমরা বিশ্ব রাজনীতির এই অদৃশ্য কিন্তু প্রভাবশালী ধারাগুলো বুঝি, ততক্ষণ আমরা সত্যিকারের শান্তির স্বপ্ন দেখতে পারব না।
![]() ৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ১০:১৮
৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ১০:১৮
র ম পারভেজ বলেছেন: ধন্যবাদ! ইনশাআল্লাহ, চেষ্টা করবো আর লেখার!
২| ![]() ৩০ শে জুলাই, ২০২৫ রাত ১২:৩৪
৩০ শে জুলাই, ২০২৫ রাত ১২:৩৪
কামাল১৮ বলেছেন: চিন্তা কর্মকে নিয়ন্ত্রন করে,কর্ম চিন্তা কে পথ দেখায়।
![]() ৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:৫৬
৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:৫৬
র ম পারভেজ বলেছেন: ভালো কথা বলেছেন।
৩| ![]() ৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:২১
৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:২১
রাজীব নুর বলেছেন: সৎ চিন্তা মানুষকে এগিয়ে নেয়। পথ দেখায়।
![]() ৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:৫৭
৩০ শে জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:৫৭
র ম পারভেজ বলেছেন: সততাই উত্তম পন্থা।
©somewhere in net ltd.
১| ২৯ শে জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৩:১০
২৯ শে জুলাই, ২০২৫ বিকাল ৩:১০
সৈয়দ মশিউর রহমান বলেছেন: আপনার লেখাগুলো বরাবরই চমৎকার।