| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
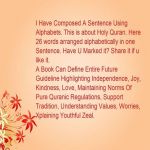 এস এম ইসমাঈল
এস এম ইসমাঈল
মুক্তমনা, সকল রকমের সংস্কার মুক্ত, আমি ধর্মভীরু হলেও ধর্মান্ধতা আমাকে কখনো গ্রাস করে নিতে পারেনি।আমি সুস্থ্য চিন্তা আর মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আমার শক্তি আমার আবেগ আবার সে আবেগ-ই আমার বিশেষ দুর্বলতা। নেহায়েত সখের বশে এক আধটু কাব্য চর্চা করি, এই আর কি। প্রিয় বিষয় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, সংগীত, দর্শন, দেশ ভ্রমন আর গোয়েন্দা সিরিজের বই পড়া।ভীষণ ভোজন রসিক আমি। জন্ম যদিও চট্টগ্রামে কিন্তু ঢাকা শহরেই লেখা পড়া আর বেড়ে উঠা। আমার জীবনের গল্প তাই আর দশ জনের মতো খুবই সাদামাটা।
বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবসমুহঃ
এদেশে রাজনৈতিকভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগে থেকেই বাংলার সাধারণ মানুষ ধর্ম প্রচারক আরবদেশীয় বনিক শ্রেণী ও পীর-দরবেশগণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল। পীর-দরবেশগণের অতি সাধারণ জীবন যাপন পদ্ধতি, নিষ্কলুষ সচ্চরিত্র, মধুর ব্যবহার, মানব সেবা এবং সর্বোপরি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাত্বত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকে। যা মুসলিম বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছিল। এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত পুস্তক সমুহে ঐতিহাসকগণ অনেক সময় সমগ্র মুসলমান সমাজের সার্বিক অবস্হার বিবরণও দিয়েছেন। এছাড়া পর্যটকগন তাঁদের ভ্রমন কাহিনীতে এবং কবি-সাহিত্যকগণ তাঁদের রচনাদিতে সমসাময়িককালের মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্হানের বর্ণনা রেখে গিয়েছেন।ঐসব রচনাদিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে আমরা সুলতানী, মোগল ও নবাবী যুগের বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবসমুহ নিয়ে আলোচনা করবো।
বাংলার সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য-
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ এম. এ. রহিম তাঁর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে 'বাঙ্গালি মুসলমানদের সামাজিক জীবন' অধ্যায়ের দ্বিত্বীয় পর্বে ''উৎসবাদি,অনুষ্ঠানাদি ও রীতিনীতি'' সমুহের বর্ণনা প্রসংগে (২৪২-২৭২) ৩০ পৃষ্টা জুড়ে এগুলির সুবিস্তৃত বিবরন দিয়েছেন।
মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুসলমানদের জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে ৩৪৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন,'' তারা (মুসলমানেরা) প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে, এবং লাল পাটি (মাদুর) বিছিয়ে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়ে। সোলেমানি মালা গুণে তারা পীর-পয়গমৃরের ধ্যান করে এবং পীরের মোকামে প্রদীপ জ্বালায়। তাদের দশিবশজন একত্রে বসে বিচার-আচার করে। মুসলমানগণ সদা সর্বদা কোরআন-কিতাব পাঠ করে। তারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ ব্যতিত তারা আর কাউকে ভয় করে না। প্রাণ গেলেও এরা রোজা ত্যাগ করে না।''
এছাড়া, বাংলা সাহিত্যের অপরাপর মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের কবিগণ যেমন- বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল', বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল', ষষ্ঠিবরের 'মনসামঙ্গল', দ্বিজ বংশী দাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্য এবং কৃষ্ণ কবিরাজের কাব্যগ্রন্থে মধ্যযুগীয় মুসলমান সমাজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমুহ সবিস্তারে স্হান পেয়েছে।
নবাবী আমলের ঢাকার সমাজ জীবনঃ
''ঢাকার সামাজিক জীবনও গড়ে উঠতে থাকে নানা জাতি-ধর্মের সংমিশ্রনে, তখনকার জীবন যাত্রা পাঠ করে জানা যায়- সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদির অধিকাংশ উপকরণই ছিল ধর্মভিত্তিক। খুব সমারোহের সঙ্গেই তখন এই সব উৎসব পালিত হ'তো, এবং সকল ধর্মের লোকেরাই একে অপরের উৎসবে যোগ দিতো। ধর্মীয় আচাররীতি আলাদা হলেও উৎসব পালা-পার্বণ পালনে একত্রিত হতো সকলে। মোহররম পর্ব সকল সম্প্রদায় নিয়ে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হতো''।
''মসজিদ তৈরি হলে উৎসব হতো। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মুঘল আমলে ঢকায় 'বেগম বাজারের করতলব খানের মসজিদ' স্হাপনের সময়েও বেশ সমারোহ হয়েছিল''।
''তখনকার ঢকার গৃহজীবনের ও কিছু কিছু পরিচয় ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যায়, প্রায় গৃহেই বৈঠকখানা কিংবা মজলিশ ঘর থাকতো। বড় লেকের বৈঠকখানা পানদান, আতরদানে সাজানো থাকতে. নানা রকম উপাদানে বাড়ীর মেয়েরা পান সাজাতো। ........................চীন দেশ থেকে আমদানী করা মাটির পাত্রে অতিথিদের খাবার সাজিয়ে দেয়া হতো। ঢাকার কারিগরদের তৈরী পানদান, আতরদানের সুক্ষ্ম কারুকাজ দেখে বিদেশীরাও মুগ্দ্ধ হতেন। ................................................... মিলাদ ও মুশায়েরার আয়োজনেও সামাজিক মেলামেশার ব্যবস্হা ছিল''।
''মুসলমানদের মধ্যে তখনও ছিল তখনো ছিল আরবি ফারসির প্রচলন। সামাজিক মেলামেশার আর একটি সুযোগ ছিল তখন মিলাদের আসরে। ঢাকা শহর জুড়েই তখন মিলাদের চর্চা ছিল। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সুর করে দোয়া দরুদ শিক্ষায় উৎসাহিত করা হতো। ভাল মিলাদকারীদের কদর ছিল সে সময়ে। সুর করে বাড়িতে সালাম দেয়ার সময়ে সুরে সুরে ভরে যেতো বাড়ি। মিলাদের পর সকলকে ঘন দুধে পাক করা চিকন চালের ফিরনী, কিংবা জাফরানী জরদা বিতরণ করা হতো ছোট ছোট তস্তরী করে। এখনকার মতো ঠোঙ্গা হাতে অতিথিদের বিদায় করা হতো না। মিলাদের পর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীদের মধ্যে আলাপ জমে উঠতো জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে''। (তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার-উল-আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং-৫৮৭-৯০।)
মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবসমুহে ঢাকার নবাব পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা-
ঢাকার নবাব পরিবার এ দেশের ইতিহাসে স্বনামধন্য ও প্রভাবশালী পরিবারগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। শুধু দেশীয় রাজনীতিই নয়, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কার্যাদিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সংগঠন-অনুষ্ঠান সমুহে আর্থিক সহায়তা-অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ঢাকার নবাব পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মাত্রা ছিল প্রবাদসম।
ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্যগন সুন্নী মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং সুফী ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। তাঁদের পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ঢাকা শহরের নামীদামী পীর হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। এ প্রসংগে 'আহসান মন্জিল ও ঢাকার নওয়াব- ঐতিহাসিক রুপরেখা' (প্রকাশনা-২০০৮ইং) গ্রন্থে বিশিষ্ট গবেষক ও আহসান মঞ্জিলের কীপার ডঃ মোহাম্মদ আলমগীর লিখেছেন,"খাজা আবদুল্লাহ একজন সফলকাম পীরের ভূমিকা পালন করেন, তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এতদাঞ্চলে আলেম উলামসহ এক বিরাট সংখ্যক জনগন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। তদানীন্তন ঢাকার মগবাজার দায়রার প্রখ্যাত আলেম ও পীর শাহ নুরী (মৃত্যু-১৭৮৫খৃঃ) পর্যন্ত তাঁর মুরীদ হতে পেরে গর্ব বোধ করতেন''। নবাব পরিবারের পূবপুরুষ নবাব পরিবারের আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারে এ পুস্তকের ৫৩-৫৫ নং পৃষ্টায় বিশদ বিবরন দেয়া হয়েছে।
পঞ্চায়েতের ভূমিকাঃ
ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা মোহাম্মদ আযম থাকতেন দিলকুশায়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১খৃঃ-১৯১৫খৃঃ) তাঁকে ঢাকার পঞ্চায়েতসমুহের জন্য তত্তাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দেন। খাজা আযম ছিলেন ঢাকার সকল পঞ্চায়েতসমুহের জন্য নিয়োজিত প্রথম তত্তাবধায়ক। ফলে এটা খুবই স্পষ্ট যে, নবাব পরিবারের প্রধানকে ঢাকার মুসলমানদের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকার। আসলে পঞ্চায়েত প্রথাটিকে সক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের পিছনে ঢাকার নবাব নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলামীকরণের মাধ্যমে ঢাকার মুসলমান সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করা'। এছাড়া তাঁর মান-সম্মানের বিষয়টিতো এর সাথে জড়িত ছিলই। বস্তুতঃ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ ভঙ্গ ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার (১৯০৬ খৃঃ) প্রেক্ষিতে নবাব পরিবারের দ্বারা ঢাকার পঞ্চায়েত ব্যবস্হার পুনরুজ্জীবন ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ঘটনাটি ছিল বিংশ শতাব্দীর বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও মুসলিম নবজাগরণের প্রতীক।
''খাজা আযমের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ১৯০৭ সালের দিকে ঢাকা শহরের পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল ১৩৩ টি। ঢাকা শহরের প্রতিটি মহল্লায় ছিল একটি করে পঞ্চায়েত। এর সদস্য ছিলেন মহল্লার সমস্ত মুসলমান বাসিন্দাগণ। ঢাকার নবাব পরিবারের বিভিন্ন মহল্লার পঞ্চায়েত প্রধানদিগকে পাগড়ী পরিধান করাতেন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হতো মিলাদ মাহফিলের। পঞ্চায়েত সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়াদি দেখবাল করার জন্য একজন তত্তাবধায়কের পদ সৃষ্টি করা হয়। মহল্লার প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠান, অন্যান্য কার্যাবলী, এক কথায়, মহল্লার মুসলমানদের জীবন নিয়নত্রন করতো এই পঞ্চায়েত। মহল্লার বিবাদ-বিসম্বাদ সবকিছুর মীমাংসা হতো এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। মহল্লার অধিবাসী কারো পক্ষ্যেই পঞ্চায়েতের দেয়া সিদ্ধান্ত অমান্য করা সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত পঞ্চায়েত সমুহ 'দায়রা-ই-মুতিয়ুল ইসলাম' নামে পরিচিত ছিল''.''মহল্লার সকল বৈষয়িক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির তত্তাবধান ছাড়াও পঞ্চায়েতের একটা প্রধান কাজ ছিল মুসলমানদের সকল ধর্মীয় উৎসবগুলোতে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেবের 'পঞ্চায়েতকে ইসলামীকরণের' সাথে এটি যুক্ত ছিল। ঢাকার মুসলমান সমাজের যে দু'টি ধর্মীয় উৎসব পালনে পঞ্চায়েতকে বিশেষভাবে সহায়তা করতে হতো সেগুলো হলো- 'মুহররম' ও 'ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহম'। তথ্য সূত্রঃ স্মৃতিময় ঢাকা- মুনতাসীর মামুন, ঢাকা-১৯৯২ খৃষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা নং-৩০-৩৮।
১। আশুরা -মুসলমান শাসনামলে বাংলাদেশে শিয়া সম্প্রদায় ছিল। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে শিয়াদের ইমামবাড়ার বহু উল্লেখ আছে। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চন্ডী মঙ্গল কাব্যের ৩৪৪ নং পৃষ্ঠায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত ইমাম বাড়ার বর্ণনা করেছেন।
''বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা 'মোহররম' পর্বকে কারবালায় (ঈমাম) হোসেনের শাহাদাতের বাৎসরিক স্মরণিকা হিসেবে পালন করতো। 'ফাদার মনসেরাত' মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬খৃঃ-১৬০৭খৃঃ) সময়কার 'মোহররম' উদযাপনের বর্ণনা দিয়ে বলেন,''মোহররমে'র সময় মুসলমানরা মাসের প্রথম নয় দিনে কেবল নিরামিশ খেয়ে রোজা রাখতো এবং একটি উঁচু মঞ্চ থেকে জনসভায় হাসান হোসেনের দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতো। এতে সমস্ত সভাগৃহ শোকে অভিভূত হয়ে যেত.........................। তারা হাসান-হোসেন ধ্বনি দিয়ে ক্রন্দন করতো''।
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ এম. এ. রহিম তাঁর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে 'বাঙ্গালি মুসলমানদের সামাজিক জীবন' অধ্যায়ের দ্বিত্বীয় পর্বের ২৪৫ পৃষ্টায় 'মনডেলসলো' কতৃক বর্ণিত আগ্রাতে মোগল সম্রাট শাহ্জাহানের (১৬২৮খৃঃ-১৬৬০খৃঃ) সময়কার মোহররম মিছিলের উল্লেখ করেছেন। অতঃপর লেখক বলেছেন,''সুন্নী মুসলমানগণ 'মোহররম' একটা নীরব শোকের পর্ব হিসেবে পালন করতো এবং সাধারণতঃ শিয়াদের আবেগময় খেলা ও মিছিলে অংশগ্রহন করতো না। সুন্নীদের মধ্যে কেবলমাত্র সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা এ-সব ব্যাপারে অংশগ্রহন করতো। মুসলমানরা মোহররমের প্রথম দিনটি নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে পালন করতো''।
'বাহারিস্তান' থেকে জানা যায় যে, 'মুসলমানগণ উৎসব ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের দ্বারা মোহররমের চাঁদকে স্বাগত জানাতো'।
নবাবী আমলে ঢাকা শহরে মুহররমের এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত হোসেনী দালানে, শহরের বিভিন্ন পঞ্চায়েত কত্বক রাতে মাতমের আয়োজন করা হতো। এ মাতম 'ভাটিয়ালী মর্সীয়া' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ১০ ই মহররম তাজিয়া মিছিল আয়েজিত হতো। বিশেষতঃ শিয়া মুসলমানেরা এতে অংশ নিতো। এছাড়া অনেক হিন্দু মহিলাগন পুত্র সন্তান লাভের আশায় তাজিয়া মিছিলে অংশ নিতো। বৃটিশ সরকারের আমলে আশুরা উপলক্ষ্যে মুহররমের এক তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত সরকারী ছুটি থাকত।
''মুসলমানদের ঈদ ও মোহররমে মেলা বসতো, মিছিল বের হতো,.............................. মেলা-মিছিলে সব ধর্মের লোকেরাই যোগ দিতে পারতো।" (তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার-উল- আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং-৫৮৮)।
২। আখেরী চাহার সাম্বা - সফর মাসের শেষ বুধবার আখেরী চাহার সাম্বা হিসেবে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে বিশষভাবে প্রতিপালিত হতো। হযরত রাসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দিনে সামান্য সুস্থ্য বোধ করে গোসল করেছিলেন বলে হাদীস শরীফের কিতাবাদিতে উল্লেখিত আছে। সে কারণে এ দিনটিতে এদেশের মুসলমানরা রোগ মুক্তির আশায় বিশেষ দোয়া-তাবিজ লিখিত পানি পান ও তদ্বারা গোসল করতো এবং ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করতো। বৃটিশ সরকার এ দিনটিতে ও সরকারী ছুটি ঘোষনা করেছিল।
৩। হযরত রাসুলে কারীমের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র জন্ম উৎসবঃ -
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও গবেষক ডঃ এম. এ. রহিম তাঁর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড) গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্টায় বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খান কতৃক নুর নবীজীর জন্ম উৎসব পালনের এক চিত্তাকর্যক বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন যে, ''বাঙ্গালী মুসলমানগণ রসুলের জন্মবাষর্কীও আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতেন। জানা যায় যে, নবাব মুর্শীদকুলী খান এই পর্বকে এক বিরাট উৎসবে পরিনত করেন। রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম বারো দিন তিনি লোকদেরকে আপ্যায়িত করেন। ভাগীরথীর তীরভূমিসহ সমগ্র মুর্শিদাবাদ তিনি আলোকমালায় সজ্জিত করতেন। একটি বিশেষ মুহুর্তে মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে খুশীর সময় ঘোষণা করে তোপধ্বনি করা হতো।'' তিনি আরো লিখেছেন,'' এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রবর্তকের জন্মদিন স্মরণীয় করে রাখার জন্য মহানবীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা শাসনকর্তা ও অবস্হাপন্ন ব্যক্তিদের একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছিল। এ সময় ধর্মভীরু ও বিদ্বানদেরকে উপহার প্রদান করার এবং মুসলমানদের মধ্যে ভোজ ও শোকরানা আদায়ের এক বিশেষ সুযোগ ছিল।''
বৃটিশ সরকারের শাসনামলে নুর নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মদিন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানী পর্ব বিবেচনায় সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষিত ছিল। 'আহসান মন্জিল-ও ঢাকার নওয়াব- ঐতিহাসিক রুপরেখা' গ্রন্থে বিশিষ্ট গবেষক ও আহসান মঞ্জিলের কীপার ডঃ মোহাম্মদ আলমগীর লিখেছেন, ''নওয়াব সলিমুল্লাহর উৎসাহ উদ্দীপনায় ফাতিহা-ই-দোয়াজ দাহামের সময় ঢাকা শহর সরগরম হয়ে উঠতো। নওয়াবের আর্থিক সহায়তায় প্রতি বছর এ উপলক্ষে ঢাকার পঞ্চায়েত সমিতিগুলো পাড়ায় পাড়ায় জাঁকালোভাবে আলোকসজ্জা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতো''। পৃঃ ৩৮
হাকিম হাবীবুর রহমান (১৮৮১ খৃঃ -১৯৪৭খৃঃ ) বলেন, ''শাহ্ বুরহানুল্লাহ কাদেরী আমার প্রতি খুব সদয় ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রফুল্ল চিত্ত ও খোশালাপী। ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জে (ঢাকা জেলা) তাঁর অনেক মুরীদ ছিল। তিনি জাঁকালোভাবে ঈদ-এ-মিলাদুন-নবী পালন করতেন''। মালয় উপদ্বীপে জন্মগ্রহনকারী, ঢাকার ভাট মসজিদ এলাকায় বসবাসকারী এই পীরের পূর্ব-পুরুষগন ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তাঁর প্রপিতামহ বহু পূর্বেই বাগদাদ থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্হাপন করেন। ১৩৩৩ হিজরী/১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তথ্যসূত্রঃ চাছালাছা -পৃষ্টা নং-১১০। ছ
ছ
চাআ৪। ফাতেহা-এ-এয়াজ দহম -
প্রতি বছর ১১ ই রবিউস সানি তারিখে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র (রহঃ) (১০৭৭ খৃঃ -১১৬৬খৃঃ) ওফাত দিবস সারা দেশের ধর্মপ্রান মুসলমান সমাজ ফাতেহা-এ-এয়াজ দহম হিসেবে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করতেন। এদেশে এটির সর্বপ্রথম প্রচলন করেন বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ) সিপাহীপাড়ায় সমাহিত হযরত বাবা আদম (রহঃ)। তাঁর নির্দেশে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দের ১১ ই রবিউস সানি তারিখে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র (রহঃ) ৮ম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তদীয় খলীফা আবদুল্লাহপুর খানকা'র প্রধান হযরত মুয়াবিন আল বসরী (রহঃ) একটা গরু জবাই করে ওরস পালন করেছিলেন বলে জানা যায়। হিন্দু রাজ্যে গরু জবেহ করার অপরাধে আবদুল্লাহপুর খানকা'র প্রধান হযরত মুয়াবিন আল বসরীকে (রহঃ) সামন্ত রাজা বল্লাল সেন অন্ধ কুপে নিক্ষেপ করে শহীদ করে। এতে কাদেরিয়া তরীকার আনুসারী হযরত বাবা আদম শহীদের (রহঃ) সাথে বল্লাল সেনের সংঘর্ষ আনিবার্য হয়ে পড়ে। ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু সামন্ত রাজা বল্লাল সেনের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাতবরণ করেন হযরত বাবা আদম (রহঃ)।
মধ্যযুগের অন্যতম মুসলিম মহাকবি আলাওল (১৬০৭ খৃঃ -১৬৮০খৃঃ) ছিলেন কাদেরিয়া তরীকার আনুসারী। তাঁর পীর হযরত মসউদ শাহ্ কাদেরী (রহঃ) ছিলেন রোসাঙ্গের কাজী। হযরত বড়পীর সাহেবের (রহঃ) প্রতি কবি আলাওলের প্রচন্ড ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে তিনি কবিকে কাদেরীয়া তরীকার খিলাফত প্রদান করেছিলেন বলে কবি তাঁর 'সিকান্দরনামা' (১৬৭৩খৃঃ) গ্রন্হের এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন।
এছাড়া অতি আধুনিককালের মহাকবি কায়কোবাদও (১৮৫৭ খৃঃ-১৯৫১খৃঃ) কাদেরিয়া তরীকার আনুসারী ছিলেন। কলকাতার হযরত এরশাদ আলী আল কাদেরী (রহঃ) ছিলেন তাঁর পীর। প্রতি বছর ১১ ই রবিউস সানি তারিখে সেগুনবাগিচাস্হ নিজ বসত বাড়ীতে কবি বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র (রহঃ) ওরসের আয়োজন করতেন। তাঁর মৃত্যর পরও যাতে এটা অব্যাহত থাকে সে মর্মে কবি তাঁর সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। পীরের নির্দেশে কবি শেষ ব্য়সে 'গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ' নামক হযরত বড়পীর সাহেবের (রহঃ) জীবনী বিষয়ক একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যা কবির মৃত্যর পর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর কন্যা জাহানারা বেগম কতৃক প্রকাশিত হয়।
আগেই বলেছি, পঞ্চায়েতের একটা প্রধান কাজ ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিলো- 'ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহম'। "ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব বিংশ শতকের শেষ দশকে মুসলমানদের আরেকটি প্রধান উৎসব হিসাবে 'ফাতেহা-ই-ইয়াজ দহম' কে তুলে ধরেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই জাঁক-জমকের সাথে ঢাকা শহরের প্রতিটি মহল্লায় ফাতেহা-এ- এয়াজ দহম উৎযাপিত হতো। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের প্রতিটি পঞ্চায়েতকে তিনি টাকা দিতেন। এই টাকা প্রধানতঃ দু'টি খাতে ব্যবহার করা হতো - মহল্লা সাজানো এবং মিলাদ পড়ানো। এ মিলাদের ও বিশেষ বৈশষ্ট্য ছিল। এটি পরিচিত ছিল 'ভাটিয়ালী মৌলুদা' নামে। জনাব নাসির আহমদ, নবাব সলিমুল্লাহ্'র সময়কার অনুষ্ঠিত এক 'স্পেশাল মিলাদের' কথা উল্লেখ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা এই স্পেশাল মিলাদ-ই ছিল 'ভাটিয়ালী মৌলুদা' বা 'মিলাদ'। হয়তো ভাটিয়ালীর সুরে পড়ানো হতো বলেই এটির এরকম নামকরণ। তিনি আরো জানিয়েছেন, ''নবাব সলিমুল্লাহ্ নিজে বিভিন্ন মহল্লায় এই মিলাদ পড়াতেন। মিলাদ পড়ানোর সাথে সাথে তিনি মহল্লার মুসলমানদের সংগঠিত করার কাজটা সেরে নিতেন এবং নিজ অনুসারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতেন। ফাতেহা -এ- এয়াজ দহমের সময় পঞ্চায়েতসমুহ চকের মসজিদ খানা সুন্দরভাবে সজ্জিত করতেন এবং সেখানে উচ্চস্বরে মিলাদ পড়াবার বন্দোবস্ত করতেন।" (তথ্য সূত্রঃ স্মৃতিময় ঢাকা-মুনতাসীর মামুন,পৃষ্ঠা নং-৩৮-৩৯)। বৃটিশ সরকারের শাসনকালে এ দিনটি ও সরকারী ছুটি হিসেবে ঘোষিত ছিল।
৫। শবে মেরাজ বা মিরাজুন্নবীঃ মক্কা জীবনে নুর নবীজী (দঃ) এর পবিত্র মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। রজব মাসের ২৬ তারিখ মধ্য রাত্রে তিনি স্বশরীরে মহান আল্লাহ্ পাকের সাথে উর্ধকাশে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এ পবিত্র রজনীর স্মৃতিকে স্মরণ করে প্রতি বছর মুসলামনেরা শবে মেরাজ বা মিরাজুন্নবী পালন করে থাকেন। এ উপলক্ষ্যে প্রতিটি মহল্লায় বাড়ীতে বাড়ীতে মিলাদের আয়োজন করা হতো। এ সকল অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা অংশগ্রহন করতো। মসজিদেও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।
৬। শবে বরাতঃ শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাতকে এ দেশের মুসলমান সমাজ সৌভাগ্যের রজনী হিসেবে পালন করে থাকে। এ পবিত্র রজনীকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মুসলামনেরা শবে বরাত বা লায়লাতুল বরাত উৎযাপন করে থাকেন। এ উপলক্ষ্যে মহল্লার প্রতিটা বাড়ীতে হালুয়া-রুটি তৈরি করে পাড়া-প্রতিবেশী ও ফকীর মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা হতো। সারা রাত নফল নামাজ, দোয়া-দুরুদ পাঠ, মৃত স্বজনদের কবর জিয়ারত, ফকীর-মিসকীনদেরকে দান খয়রাতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হতো। মসজিদসমুহে ও পাড়ায় পাড়ায় মিলাদের আয়োজন করা হতো। এ সকল অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনেরা অংশগ্রহন করতো।
শামস সিরাজ আফিফের প্রমানাদি থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক চারদিনব্যাপী এ উৎসব পালন করতেন। এবং এ পরিমান আতশবাজীর আয়োজন করতেন যে, রাত্রিকাল প্রশস্ত দিবালোকের আকার ধারণ করতো।
'তারিখ-ই দাউদী'তে আবদুল্লাহ্ লিখেছেন যে, ''শেরশাহের খ্যাতনামা সভাসদ ও তদীয় পুত্র আদিল খানের সমর্থক খাস খান ফতেহপুর সিক্রিতে শেখ সেলিম চিশতির খানকায় শব-ই-বরাতের সারা রাত্রি নামাজ আদায় করেন''।
সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বাংলার নবাবগণ বিশেষ মযার্দার সঙ্গে এ পর্ব পালন করতেন। আলোকমালায় গৃহসমুহ সজ্জিত করা হতো এবং স্ত্রী-পুরুষ কতৃক প্রতিটি গৃহে এবং মসজিদে সারা রাতব্যাপী নামাজ পড়া হতো। তারপর ভোজের অনুষ্ঠান হতো এবং গরীবদের মধ্যে দান খয়রাত বিতরণ করা হতো। আতশবাজী প্রদর্শনীর ব্যবস্হা ছিল। বাংলার নবাবগণ এ দেশের মুসলমানদের বহুকাল প্রচলিত রীতি অব্যাহত রেখেছিলেন।
বস্তুতঃ শব-ই-বরাত ছিল মুসলমানদের একটি জনপ্রিয় পর্ব এবং এটি ছিল আরাধনা, খানা-পিনা ও আনন্দ-উৎসবের একটা বিশেষ দিন। প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাস এই যে, 'শব-ই-বরাত' খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাত এবং এ রাতে আল্লাহ্ মানুষের জন্য রুজি বন্টন করেন। এরুপ বিশ্বাস করা হয় যে, প্রার্থনা, পবিত্র কোরআন পাঠ ও পূণ্য কার্যের মাধ্যমে এ রাত্রি যাপনের জন্য মহানবী (দঃ) মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলামনরা এ পর্বটিকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসভিসেবে পালন করে থাকেন। তারা এ শব-ই-বরাতকে খাওয়া-দাওয়া, আলোক সজ্জা ও আতশবাজীর দ্বারা আনন্দ উৎসব করার ও একটি বিশেষ পরিণত করেছেন।
৭। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা- ইসলাম একটি সহজ ধর্ম এবং এর অনুষ্ঠানাদি সামান্য ও আড়ম্বরহীন। বাংলার মুসলমানরা এ উৎসবগুলোকে বিরাট আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। তাবাকাৎ-ই-নাসিরী থেকে জানা যায় যে, সুলতানগণ রমজান মাসে দৈনন্দিন ধর্মীয় অলোচনার ব্যবস্হা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক নিয়োগ করেন। তাঁরা 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'র নামাজ পড়ার জন্য ইমামও নিযুক্ত করেন। শহরের বাইরে বিরাট উম্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতো। এবং এসব স্হানকে 'ঈদগাহ্' বলা হতো।
'বাহরিস্তানে গায়েবী'র লেখক মীর্যা নাথান বণর্না রমজান ও অন্যান্য উৎসবাদি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি বলেন,''রমজান মাসের সূচনা থেকে এর শেষ দিন পর্যন্ত ছোটবড় সকলে প্রত্যহ নিজ নিজ বন্ধুর তাঁবুতে যেতেন। এটা একটা সাধারণ রীতি হয়ে দাড়ায় যে, প্রত্যহ সকলে এক একজন বন্ধুর তাঁবুতে তাদের সময় কাটাতে। সেই অনুসারে, শেষের দিন মুবারিজ খানের সান্ধ্য ভোজ ছিল। সমস্ত লোক সেদিন তার সেখানে সময় কাটাতো।''। এ থেকে বুঝা যায় যে, রমজান মাস কেবল সংযম ও নামাজের মাসই ছিল না, 'এ মাসে প্রতি রাত্রে অবস্হাপন্ন মুসলমানদের গৃহে সাক্ষাত করা ও খানাপিনার আয়োজন করা হতো।'
'ঈদুল ফিতর'র নতুন চাঁদ দর্শনে মুসলমানদের আনন্দ-উৎসবের ঈঙ্গিত ও মীর্যা নাথান বণর্নায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন,''দিনের শেষে যখন মোমবাতির আলোকে নতুন চাঁদ দেখা গেল, তখন শিবিরে রাজকীয় বাজনা বেজে উঠলো এবং আগ্নেয়াস্ত্র ক্রমাগত অগ্নি উদ্গীরণ করে চললো। রাত্রির শেষভাগে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ থেমে গেল। এর স্হলে ভারী কামানের অগ্নি উদ্গীরণ শুরু হলো। এ ছিল যেন ভূমিকম্প''। বাংলাদেশে মোগল সৈন্যদের ছাউনী থেকে ঈদের আনন্দ বার্তা ঘোষনা করা হতো।
ঈদের দিন মুসলমান নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা সুন্দর কাপড় পরতো।
গোলাম হোসেন ঈদ উল আজহাকে আনন্দ স্ফুর্তি ও সকল মানুষের জন্য নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ পরার দিন বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানরা সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে ঈদগাহে যেতো। অবস্হাপন্ন ব্যক্তিরা এ উৎসবের সময়ে মুক্ত হস্তে অর্থ ও উপহারাদি চলার পথে ছড়িয়ে দিতেন। আর সাধারণ মুসলমানেরা গরীবদেরকে দন-খয়রাত করতেন। ঢাকার নায়েব সুবাদার মুর্শীদকুলী খান ঈদের দিনে ঢাকার দুর্গ থেকে ঈদগা'র ময়দান পর্যন্ত এক ক্রোশ পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন। মুসলমানেরা ঈদগা'র বিরাট জমায়েত ঈদের নামাজ পড়তেন ও আমোদ-প্রমোদ চলতো এবং সর্বত্র অভিনন্দনের আনন্দে মুখরিত হতো। এ সমস্ত বড় উৎসবের দিনে সৌজন্যমুলক সাক্ষাত ও একত্রে আনন্দ-উৎসব করার জন্য তারা বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গমনাগমন করতেন। ঈদের দিন মুসলমান নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা সুন্দর কাপড় পরতো। এতে প্রকাশ পায়, কিভাবে মুসলমানরা ঈদ উৎসবকে স্বাগতঃ জানাতো এবং এই আনন্দ উৎসবে আমোদ-প্রমোদ করতো ও এর জন্য শুকরিয়া আদায় করতো।
''ঈদের সময় মেলা বসতো.............................. মেলায় সব ধর্মের লোকেরাই যোগ দিতে পারতো। নানা কারুকাজ নিয়ে নানা জাতির কারিগররা দোকান বসাতো এই সব মেলায়। কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, নানা রকমের বয়ন শিল্পের প্রদর্শনী হতো মেলায়। শাঁখারী বাজারের শাঁখের গহনা এবং হাতির দাঁতের কারুকাজ দেখেও মুগ্ধ হতো বিদেশী ব্যবসায়ীরা। মুঘল যুগে ঢাকার কারিগরী ব্যবসায়ে হিন্দুদের আধিপত্য ছিল বেশী, বয়ন শিল্প এবং সোনা-রুপার কাজে হিন্দু কারিগরদের দক্ষতা বেশী পরিলক্ষিত হলেও, পোষাকে জরি-বুটিকের কাজে, কাটা পোষাক তৈরিতে এবং হাতির দাঁতের শিল্পকর্মে মুসলমান কারিগরই নিয়োজিত ছিল বেশী। দালান কোঠা তৈরির কাজেও নিয়োজিত মুসলমান ওস্তাদরা।'' (তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার -উল - আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং-৫৮৮)।
৮। ওরসঃ ''পীর ফকীরের মাজারে 'ছিন্নী' দিতো সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলেই, ক্রমে ঢাকার অলিতে গলিতে অসংখ্য পীর-ফকীরের মাজার গড়ে ওঠে এবং এক শ্রেণীর লোকের আয়ের ব্যবস্হা হয় মাজার থেকে।'' এছাড়া বিভিন্ন মাজার ও পীরের খানকাসমুহে ওরস উপলক্ষ্যে মাসিক বা বার্ষিক মিলাদের আয়োজন করা ছিল খুবই সাধারণ বিষয়। এ সকল অনুষ্ঠানে সকল শ্রেনীর নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহন করতো ।
(তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার -উল - আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং-৫৮৯)।
বাংলার মুসলমানদের সামাজিক উৎসবসমুহঃ
১। সন্তানের জন্ম উৎসবঃ ধনবান ব্যক্তিরা পুত্র সন্তানের সালগিরা এবং খাৎনাতেও উৎসব করতেন খানা-পিনার ব্যবস্হা করে।
(তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার -উল - আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং-৫৮৭।
এর সাথে সংযুক্ত ছিল আরো বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিকতা। যেমন-
আকীকা- সন্তানের ৪০ দিন বয়সে, বিসমিল্লাহ খানী - (লেখাপড়ায় হাতে খড়ি) সন্তানের ৪বছর চার দিন বয়েসে, খাতনা- সন্তানের সাত বছর বয়সে,
বিয়ে-শাদীঃ সন্তান উপযুক্ত হলে।
২ ক) নতুন আবাস গৃহ বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মিলাদঃ-
মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সাফল্যকে উপলক্ষ্য করে মিলাদের আয়োজন করা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যপার। এ সকল মিলাদানুষ্ঠানে সকল পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়্ন করা হতো। তখনও পর্যন্ত দেশীয় শহরবাসী নাগরিকদের জন্য নিয়মিত মেলামেশার জন্য কোন সুব্যবস্হা গড়ে না উঠার ফলে এ সকল মিলাদানুষ্ঠান সামাজিক আলাপ-পরিচয় ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের একটা উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে পরিনত হয়েছিল।
২ খ) সাফল্য লাভ বা রোগ/বিপদ মুক্তির জন্য মিলাদ মাহফিল
যে কোন রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে আক্রান্ত হলে মিলাদের আয়োজন করা হতো। বাড়িতে স্হান সংকুলান না হলে সেক্ষেত্রে পাড়ার মসজিদে মিলাদের ব্যবস্হা করা হতো। মিলাদ শেষে উপস্হিত অভ্যাগতদেরকে ফিরনি বা ক্ষীর দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। আর অপেক্ষাকৃত গরীব পরিবারের লোকেরা জিলাপী বা বাতাসা দিয়ে আতিথিদরকে মিষ্টিমুখ করাতো।
৩। প্রিয়জনের মৃত্যুতে কুলখানী, চেহলাম ও ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠানঃ ''জন্ম-মৃত্যুতে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার আলাদাভাবে পালিত হতো। ................................ মুসলমানদের চল্লিশা যাপন করা হতো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়ে।''
মৃত স্বজনদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনায়
(তথ্য সূত্রঃ ঐতিহাসিক ঢাকা মহা নগরীঃ বির্বতন ও সম্ভাবনা- সম্পদানা-ইফতিখার -উল - আউয়াল, প্রকাশনায়- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৪খৃঃ, পৃষ্ঠা নং- ৫৮৯।)
ইংরেজ আমলে সরকারী ছুটির তালিকাঃ
১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় রেগুলেশন আনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের জন্য ছুটি বরাদ্দ ছিল মাত্র ২২ দিন। এর মধ্যে
মহররমের ছুটি - ১৫ দিন
আখেরী চাহার সাম্বা - ১ দিন
নবীজীর জন্ম উৎসব - ১ দিন
১ লা শাবান - ১ দিন
ঈদুল ফিতর - ২ দিন
ঈদুল আযহা - ২ দিন
সর্ব মোট - ২২ দিন
(তথ্য সূত্রঃ ইতিহাসের খেরো খাতা-১ম খন্ড, মুনতাসীর মামুন, ঢাকা-১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ,পৃষ্ঠা নং-৫৭।)
বাংলার লোক উৎসবঃ বেড়া ভাসান
১। বেড়া ভাসান ও বদর আউলিয়া_
সারা আরব জাহানও ভারতবর্ষ জুড়ে হযরত খিজির (আঃ) কে নিয়ে প্রবল ঔৎসুক্য বিদ্যমান। এমনকি বাংলাদেশেও হযরত খিজির (আঃ) বহুল আলোচিত এক নাম। তাঁকে অনেক মুসলমান আজো একজন নবী হিসেবে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম এ রহিম সাহেব তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থের ২৪৬ নং পৃষ্টায় লিখেছেন - " বাংঙ্গালী মুসলমানগণ 'বেড়া' উৎসব পালন করতো বলে জানা যায়। এই উৎসব পয়গম্বর খোয়াজ খিজিরের সম্মানার্থে পালন করা হতো। খোয়াজ খিজিরকে সকল জলরাশির অভিভাবক বলে বিশ্বাস করা হতো। নবাব মুশির্দকুলী খান বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে এই উৎসব পালন করতেন। কলাগাছ এবং বাঁশের তৈরী নৌকা সাজান এবং তদুপরি কাগজ নির্মিত গৃহ ও মসজিদ ইত্যাদি ছিল 'বেড়া' উৎসবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। মুশির্দকুলী খান ৩০০ ঘন ফুট আকারের একটি নৌকা নির্মাণ করেন এবং এর উপরে তিনি ঘর ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে জাহাজটি আলোকসজ্জিত করে নদীতে ভাসান। জাহাজের আলোক-মালা বহুদুর থেকে দেখা যেতো। এই উপলক্ষে আতশবাজীর প্রদশর্নীও থাকতো। 'বেড়া' উৎসবটি বাংলা ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার দিনে উদযাপিত হতো। বহু মুসলমান এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতো। নবাব মুকাররম খান কতৃক ঢাকায় এ উৎসবটি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল " । কে পি সেন, বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল) গ্রন্থের ৭১ নং পৃষ্ঠায় একই রকম তথ্য দিয়েছেন।
এছাড়া পীর বদর আউলিয়া ও এদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমানভাবে পূজিত। ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কতৃক ২০০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত - ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরীঃ বিবর্তন ও সম্ভাবনা শীর্ষক গ্রন্হের ৮৩ নং পৃষ্ঠায় বিষয়টি এভাবে এসেছে, ''ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত হিন্দু-মুসলিম সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ব্যতিত কতক লৌকিক দেবদেবীর পূজা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত, যা দানীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহায়ক ছিল। এ রকম একজন দেবতা হচ্ছেন "বদর", যাকে নদীর অধিষ্ঠাত্রী তথা রক্ষক দেবতা হিসেবে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক দিন পূজা করত। তবে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নিম্ন স্তরের (যারা নদীভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ) মানুষের মধ্যে এটির প্রচলন ছিল বেশী''। দানী- পৃষ্টা নং-৬৩।"
©somewhere in net ltd.