| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
ফকির লালন ও কবিয়াল কুবির গোঁসাই : বাংলার জনপথের গান
আবদুল্লাহ আল আমিন
অখ- নীলাকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ শ্যামল ফসলের মাঠ। মাঠের পূর্বে মেহেরপুরের ইছাখালি এবং পশ্চিমে নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নফরচন্দ্রপুর। ইংরেজ আমলে গ্রাম দুটি একটি অখ- গ্রাম ছিল। ১৯৪৭ সালে এই অখ- গ্রামটি অবিভক্ত বাংলার মতই বিভক্ত হয়ে গেছে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এ বর্ধিষ্ণু গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এক সাধক মহাজন যার নাম আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮)। তিনি ছিলেন একাধারে অধ্যাত্মসাধক, পদকর্তা,অগ্রগামী গায়ক এবং নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাংলাদেশের বৃহত্তর পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর জেলায় ছিল তার অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী। লালন সাঁই, কুবির গোসাঁই এর মতো তিনিও ছিলেন মানুষ সত্যের উপাসক। বিরুদ্ধ প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ‘মানুষ বিনে আর কিছু নাই’। এই মহাজন সাধকের বাণী ও সঙ্গীত সম্পর্কে দু’বাংলার মরমী ভাবুকরা বিশেষ ভাবে জানেন যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরজান শাহের জন্মস্থান অবিভক্ত নদীয়ার মেহেরপুর মহকুমার তেহট্ট থানার ইছাখালি-নফরচন্দ্রপুর গ্রামের পূর্ব অংশ ইছাখালির অবস্থান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় আর খাল সংলগ্ন নফরচন্দ্রপুর অংশটি পশ্চিমবঙ্গে। অনতিদূরে আরজান শাহের গুরুপাট শরডাঙ্গা গ্রামটিও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে লালন উত্তর মরমি ভাবুকতার অন্যতম প্রধান পুরুষের জন্ম, মৃত্যু, মাজার ও গুরুপাট আর অবিভক্ত বাংলার নিয়তি বুঝি একই সরলরেখার অনুগামী। কিন্তু নিগূঢ় সত্য এই যে, রাজনৈতিক কারণে বাংলা দিখ-িত হলেও বাঙালির ভাবসত্তা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায়নি। অসম্ভবের মধ্যেও পথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে মিলনের আহবান। মানচিত্রে খ-িত হলেও রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-লালনের চিন্তা ও ভাবুকতায় ¯œাত বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূগোলকে বিভক্ত করা যায়নি। মহাজন সাধক আরজান শাহের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত সীমান্তবর্তী ইছাখালি-নফরচন্দ্রপুর পীঠস্থানও সহজিয়া মরমীদের সহজ মিলনের বাতাবরণ তৈরী করে দিয়েছে। প্রতিবছর দোল পূর্ণিমায় আরজান শাহের মাজার প্রাঙ্গণে বসে দু’বাংলার সাধক দরবেশদের মিলনোৎসব। ২৪ ফাল্গুন ১৪১৮ বৃহস্পতিবার আরজান স্মরণ দিবস উপলক্ষে দোল পূর্ণিমার ধবল জ্যোৎ¯œায় ¯œাত মাজার প্রাঙ্গণে মেহেরপুর সিংহাটি গ্রামের হারুন বাউল নামের এক গায়ক গাইছেন :
‘সাঁই সাহেবের মসজিদ খানা/মাধবপুরে তার ঠিকানা/রহিমশাহ করিম শাহ দুজনা/আলাবেড়ের পতিতপাবন ॥ /ভিটেপাড়ায় মদন শাহ’র আসন/ ডোমপুকুরে বিশ্বাসে বদন/ ঘোষপাড়ায় সতীমার আসন/হুদোপাড়ায় পাল চরণ ॥/ কেরামত উল্লাহ হুজুর মিয়া/শরিয়তে দুজনা দিয়া/পাঞ্জু খোন্দকার ময়নুদ্দি শাহ/এদের দিয়ে হয় পঞ্চজন ॥/যাদুবিন্দু এরাই দুজনা/পাচলাখি গাঁয় তার ঠিকানা/ শেওড়াতলায় আহাদ সোনা/আরও আছে কত জনা॥/ ঘোলদড়িয়ায় পাঁচু শাহ’র আসন/কুবির গোসাঁই, নারায়ন চেতন/উদয় চাঁদ কোদাই শাহ দু’জন/আনন্দ মোহিনী আর মদন॥/কামার পাড়ায় ভোলাই শাহ রয় ছেঁউড়িয়াতে দরবেশ লালন ॥’
গ্রাম্য এই সাধকের গানের কথা একেবারেই সহজ-সরল এবং আটপৌর। কিন্তু তাঁর আহরণে রয়েছে গভীরতা ও মানবিক ঔদার্য। অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তিনি তঁাঁর এই গানে অবিভক্ত নদীয়া, বর্ধমান এবং যশোরের বিস্তৃত ভূখ-ের অসংখ্য সাধু দরবেশ, ফকিরদের নাম-ঠিকানা দিয়ে গেঁথেছেন তার গানের মালা। তাঁর গানের কথায় রাজনৈতিক ভূগোলের পরিসীমা নেই, জাতি ধর্মের বেড়ি নেই, স্থানগত বিভাজন কিংবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই। লোকধর্মের দিগন্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ধর্মের নামে ভেদাভেদ থাকে না, থাকে না কাঁটা তারের বেড়া। কারণ তাদের আরাধ্যের নাম কেবল মানুষ। তাদের শাস্ত্র কিতাব নেই; নেই মন্ত্র কিংবা গঙ্গা জলের মহিমা। তারা স্মৃতি শাস্ত্রের পুরোহিত কিংবা আলেম মওলানাদের নিকট থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা কাছে টানেন মানুষকে, যে মানুষ ভাবের মানুষ এবং রসের মানুষ। সম্প্রদায়গত ভাবে এরা হিন্দু-মুসলমান হলেও তারা মসজিদ-মন্দিরের চার দেয়ালের বাইরে গান গেয়ে সাঁই নিরঞ্জন বা পরমারাধ্যকে তালাস করেন। মন-মননে, চিন্তায় কর্মে, জীবন চর্চায় তারা সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। আখড়া, আশ্রম, সাধুসঙ্গ, মেলায় গান গাওয়ার সময় তারা মুলতঃ মানুষ ও মানবতার জয় ঘোষণা করেন। এদের গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,
‘...... এই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমান মিশেছে, কোরান-পুরানে ঝগড়া বাঁধেনি।’ (মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ১ম খন্ড, আশীর্বাদ, রবীন্দ্রনাথ।)
লোকধর্ম তার স্বাভাবিক উদারতা দিয়ে জগতের সকল শ্রেয়োচেতনা ধারণ করতে পারে। সেকারণে নদীয়ার বৃত্তিপাড়া গ্রামের তিনকড়ি নামের লোকধর্মের এক অখ্যাত, নিরক্ষর সাধক সহজ সরল ভাষায় এই উঁচুমানের গানটি বাঁধতে পেরেছিলেন। উদ্ধৃত গানের কথায় যেমন করে ঘোষপাড়ার সতীমা, বৃত্তিহুদার চরণ পাল, চুয়াডাঙ্গার ঘোলদাঁড়িয়ার পাঁচু শাহ, পাঁচ লাখির যাদুবিন্দু, চাপড়ার কুবির গোসাঁই, ছেঁউড়িয়ার লালন সাঁইজির প্রসঙ্গ এসেছে, তেমনি মাধবপুরের মসজিদ এবং শরিয়তপন্থী মওলানা কেরামতউল্লাহ ও হুজুর মিয়ার নামও বাদ যায়নি। এমন ঔদার্য, মনের প্রসারতা সম্ভবত লোকধর্মের বিস্তৃত প্রাঙ্গণেই মেলে, যদিও তারা তত্ত্বগতভাবে শরিয়ত বিরোধী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও শাস্ত্র- কেতাব বিরোধী।
আঠার ও ঊনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলার নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের বিস্তৃত জনপদের বিভিন্ন অখ্যাত অজপাড়া গ্রামে যে সব লোকধর্মের উদ্ভব ঘটে তাদের মধ্যে সাহেবধনী ও বাউল অন্যতম। অর্থনেতিকভাবে বিপন্ন ও প্রান্তিক মানুষ যারা বড় ধর্মে আশ্রয় পায়নি, তারাই বাউল,কর্তভজা ও সাহেবধনীর মত লৌকিক গৌণধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব নদীয়া জেলার শালিগ্রাম অঞ্চলের আঠার শতকের গোড়ার দিকে চরণ পাল নামের এক সাধকের নেতৃত্বে। চরণ পালের জন্ম ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে। শাস্ত্র-মূর্তি-মন্ত্র ও বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে দ্রোহী ধর্ম হিসেবে সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এ সম্প্রদায় এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবুও দোগাছিয়া গ্রামের প্রান্তবর্তী জলাঙ্গী নদীর পূর্ব পারে বৃত্তিহুদা গ্রামে আজও তাঁর ভিটে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সাহেবধনীদের আরাধ্য দীন দয়ালের সাধনগৃহ রয়েছে। সাহেবধনীদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি দু বাংলার লোকসমাজে নেই বললেই চলে। তবে এদের গান বেঁচে আছে, আজও এ গান সাধু দরবেশরা ভুলে যায়নি। এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গান বেঁধেছেন কুবির গোঁসাই। তিনিই এ সম্প্রদায়ের প্রধান ভাষ্যকার, বিশ্লেষক ও গীতিকার। হয়তো একদিন সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কথা মানুষ ভুলে যাবে, কিন্তু কুবির এর বিশাল গানের জগৎ বেঁচে থাকবে। তিনি কেবল সাহেবধনী সম্প্রদায়ের জন্য গান রচনা করেননি। বাংলার লৌকিক গানের ভা-ারকেও উৎকর্ষম-িত করেছেন। শ্যামা সঙ্গীত বা শাক্ত গানে রামপ্রসাদ, বাউল গানে লালন শাহ, কবিগানে ভোলা ময়রা, কীর্তনে মধুকান, মারফতিগানে হাসন রাজা, ফকিরি গানে পাঞ্জুশাহ, কঠিন দেহতত্ত্বের গানে হাউড়ে গোঁসাই, কর্তাভজাদের গানে লালশশী এককভাবে ভাবুক রসিকদের অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়েছেন যেভাবে, ঐ একইভাবে সাহেবধনীদের গানে অবশ্য উচ্চার্য নাম কুবির গোঁসাই।
সাহেবধনীদের সমসাময়িক বাউল বা ফকিরি সম্প্রদায় বাংলার লোকধর্মগুলির অন্যতম প্রধান ও লোকপ্রিয় ধারা। বাংলার বাউলরা মূলত পাঁচ ঘরানায় বিভক্ত। এরা কেউ সতীমা ঘরানার, কেউ লালন ঘরানার আবার অন্যরা উজল চৌধুরী, দেলবার সাঁইজি এবং পাঞ্জু শাহর ঘরানার। পোশাক আশাক অবয়ব,সাধন ভজনের পদ্ধতিতে এদের মধ্যে খানিকটা অমিল থাকলেও ভাব-ভাবুকতায় মিল খুঁজে পাওয়া যায় বেশি। তবে বাউল মতবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে লালন সাঁইজিকে ঘিরে। বাউল মতবাদের যে শিখরস্পর্শী লোকপ্রিয়তা তার মূলেও রয়েছেন বাউল সাধক লালন সাঁই ও তাঁর গান। তাঁর বাণী, গান, সাধনা, দর্শন এখন এত জনপ্রিয় যে তা লৌকিক জীবনের গ-ি পেরিয়ে নাগরিক জীবনকে স্পর্শ করেছে। তিনি তাঁর জীবৎকালেই বাংলার বিদ্বৎ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহিত্য সাধক, গ্রামবার্তা সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, সরলাদেবী চৌধুরানী লালনের গান সংগ্রহ করেছেন। তাঁর লোকপ্রিয়তা এমন তুঙ্গে উঠেছিল যে লালনের জীবতকালের লালন গীতি ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। একালেও তাঁর বর্ণিল জীবন ও সঙ্গীত সাধনা নিয়ে দু বাংলার বিদ্বদ সমাজ থেকে শুরু করে রাজনীতিকদের মধ্যে পর্যন্ত রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতুহল। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে এক বিশেষ সমাবেশে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, ‘লালন শাহ একজন উঁচু দরের সুফি সাধক ছিলেন এবং পবিত্র কোরানের ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন।’ (সাপ্তাহিক ইস্পাত। কুষ্টিয়া, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮)।
তাঁকে নিয়ে নাটক, যাত্রাপালা রচিত হয়েছে, ফিচার, ফিল্ম ও ডকুমেন্টারিও নির্মিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে রচনা করেন কালজয়ী উপন্যাস ‘মনের মানুষ’ এবং এই উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ নির্মাণ করেন আন্তর্জাতিকমানের শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র। প্রতিবছর চৈত্রের দোলপূর্ণিমায় তার সমাধি প্রাঙ্গণে নামে লাখো মানুষের ঢল। চৈত্র মাসের দোল পূর্ণিমায় লালন প্রবর্তিত সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা এখন বিশাল লোকমেলার রূপ নিয়েছে। এই মেলা ইতোমধ্যেই দেশি বিদেশি গবেষক, প-িত, রাজনীতিক, আমলা মন্ত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আর ব্রাত্য লালন নন, তিনি এখন বিবিসির শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত সেরা কুড়ি বাঙালির একজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ রায়, অমর্ত্য সেনের নাম যে তালিকায় রয়েছেন সেখানে লালন সাঁইজির নামও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকার ১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ সংখ্যায় ‘হারামণি’ শিরোনাম লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে যে লালনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সারস্বত সমাজে, তিনি দেশের গ-ি অতিক্রম করে বিশ্বের নানা দেশে পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, যা বলাই বাহুল্য। অথচ তাঁর সমসাময়িক অনেক সাধক গীতিকার সেই পরিচিতি পাননি। যেমন, আমরা চিনি না কবির গোঁসাইকে। লালনের সমসাময়িক এই সাধক ছিলেন একাধারে পদরচায়িতা, গায়ক, অধ্যাত্মক সাধক এবং সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শের বিশ্লেষক ও ভাষ্যকার। তাঁর শিষ্য যাদুবিন্দু (১৮২১-১৯১৯) পদকর্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গানের ভা-ার সমৃদ্ধ করছেন কুবির গোঁসাই (১৭৮৭-১৮৭৯) এবং তার শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই। কুবির অনন্য প্রতিভার অধিকারী এক বিরলপ্রজ সাধক কবি ছিলেন তথাপি মরমীদের গানের ভুবনে তার গান কম গীত হয়। সম্ভবতঃ কুবিরের গান ছিল তত্ত্ব সমৃদ্ধ, জটিল ও দুর্বোধ্য। এছাড়াও তার সাধনক্ষেত্র ও আবাস দুর্গম পল্লী অঞ্চলে হওয়ায় তার গান কারো চোখে পড়েনি। উৎপন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো সংগ্রাহকও কুবিরের গান সংগ্রহ করতে কোন রকম কৌতুহল দেখাননি। যদিও তিনি তাঁর সুবৃহৎ গীতি সংকলনে কুবিরের ভণিতা যুক্ত যাদুবিন্দুর চারখানি গান সংগ্রহ করেছেন। এভাবেই ফোকলোরবিদ ও সংগ্রাহকদের উপেক্ষার কারণে কুবির লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। লালন সাঁইজিকে হয়তো ওই একই ভাগ্য বরণ করতে হতো যদি না রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে কুষ্টিয়া অঞ্চলে যেতেন। কুবিরের গানের সাথে দু’বাংলার বিদ্বদ সমাজের পরিচয় না থাকলেও সহজিয়া সাধকদের তার গানের সাথে রয়েছে ঘনিষ্ঠতা। অনেক সাধক বাউলই তাঁর নাম জানে এবং তার গানের মর্ম বোঝে।
কুবির গোঁসাই বাসস্থান ও জন্মস্থান নিয়েও বির্তক রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মধুপুর গ্রামের সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাধক শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (১৯৩৮-২০০৫) এর মতে, তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তার আসল নাম কুবের সরকার। তাঁর পিতা-মাতার নাম জানা যায়নি। প্রথম যৌবনে চরণ পালের নাম ডাক শুনে তিনি চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে চলে আসেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। কুবিরের ভিটে ও সমাধি বৃত্তিহুদা গ্রামে রয়েছে। কুবিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য বৃত্তিহুদা গ্রামের রামলাল ঘোষের খাতা থেকে জানা যায়, কুবিরের জন্ম ১১৯৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন পূর্ণিমায়, মৃত্যু ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত চারদ-ে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথির মধ্যে।’ (সুধীর চক্রবর্তী, ‘সাহেবধনী সম্প্রদায়ের তাদের গান’, রচনা সমগ্র। কলকাতা ২০১০, পৃ: ২৪)।
রামলাল ঘোষের খাতা থেকে কুবিরের জন্ম মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেলেও তার জন্মস্থান কিংবা পৈতৃক নিবাস সম্পর্কে হদিস মেলে না। রামলালের খাতা থেকে আরও জানা যায় কুবিরের স্ত্রীর নাম ছিল ভগবতী (মৃত্যু: ১২৯৭) এবং সাধন সঙ্গীনির নাম কৃষ্ণমোহিনী (মৃত্যু: ১২৯৮)। বৃত্তিহদার পালবাড়ির খুব কাছে কুবিরের সমাধি মন্দিরের পাশেই তার স্ত্রী ও সাধন সঙ্গীনিকে সমাহিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চরণপালের জন্ম ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে, কুবিরের জন্ম ১৭৮৭ আর মৃত্যু ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে, দুলাল চাঁদের জন্ম ১৭৮৭ আর মৃত্যু ১৮৩৩, সতীমার মৃত্যু ১৮৪৩ খ্রি. এবং ফকির লালন সাঁই এর জন্ম ১৭৭৪ আর মৃত্যু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় কর্তাভজা, সাহেবধনী ও বাউল, এই তিন লৌকিক সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল অভ্যুদয় আঠার শতকের শেষপাদে এবং তিনটি ধর্মের প্রসার ক্ষেত্র অবিভক্ত নদীয়া জুড়ে। এছাড়াও বলরামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম হাড়ির জন্ম ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৮৫০ খ্রি.।
এখন প্রশ্ন হলো যে, আঠার শতকের শেষ দিকে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশে এতগুলো লৌকিক ধর্মমত উদ্ভবের কারণ কী? আর কেনইবা কালের আবর্তে অধিকাংশ লৌকিক ধর্মগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেল? আরও একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, এসব লোকধর্মের প্রাঙ্গণে উচ্চবর্ণের মানুষের ঠাঁই মেলেনি, কারণ এদের প্রবর্তক কিংবা প্রধান গুরুরা ছিলেন অন্ত্যজ. অস্পৃশ্য কিংবা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক। সাহেবধনীদের চরণ পাল ছিলেন গোয়ালা, বলরামিদের বলরাম জাতে হাড়ি, লালন সাঁই জাতিচ্যুত বাউল,খুশি বিশ্বাস দরিদ্র আতরাফ মুসলমান। প্রশ্ন জাগে, একদা একদল দ্রোহী জীবনরসিক মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রবল আধিপত্যের বিরুদ্ধে নির্মাণ করেছিলেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, আবার কেনইবা তাদের উত্তরপুরুষরা মাথানত করল রাষ্ট্র সমর্থিত প্রথাগত ধর্মের প্রবল প্রতাপের কাছে?
আজকাল ছেঁউড়িয়ায় লালনকে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা এবং এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা মাতামাতি করছেন, অথচ লালন অনুসারীরা গ্রামে গঞ্জে ক্রমাগত ভাবেই প্রান্তিক অবস্থানে চলে যাচ্ছে। কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনার বিস্তৃত জনপদে এক সময় গড়ে উঠেছিল অসংখ্য আখড়া আশ্রম যেগুলি অধিকাংশই নিষ্প্রভ বা বন্ধ হতে চলেছে। পরাক্রান্ত সমাজের প্রতিকূলতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে লালন একদিন ভোগবাদ আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে চেতনা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন সেই চেতনাকে আমাদের সমাজের গভীরে তেমন প্রোথিত করা যায়নি। তার দর্শনের নিগূঢ়তা আর জীবন প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা বাউল সমাজ কিংবা আমাদের সারস্বত সমাজ বা রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে খুব সামান্যই। তাহলে এই লুম্পেন নিয়ন্ত্রিত, দুর্বৃত্ত কবলিত, ভোগসর্বস্ব বাংলাদেশ ও তার সমাজ কোন লালনকে নিয়ে মাতামাতি করছে? আর কেনই বা করছে? এই মাতামাতি কি কেবলই ভাঁড়ামি ? কেবলই কী মুদ্রানিয়ন্ত্রিত সমাজের কর্পোরেট-দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার জন্য? তাদের কাছে তো ধান, গান, ভোরের শিশির, মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারানো মায়ের অশ্রু, গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা কিংবা লালন-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সবই পণ্য। দীর্ঘকাল ধরে লালন নানাভাবেই আমাদের শিক্ষিত নাগরিক সমাজের কাছে ব্রাত্য হয়ে ছিলেন। এখন তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আসল লালনকে আমরা কখনই খোঁজ করতে চাইনি। আজ যে লালনকে নিয়ে মাতামাতি করা হচ্ছে তিনি আসলে তথাকথিত গবেষক ও ফেরেব্বাজদের বানানো নকল লালন। এই বানানো নকল লালনের আধিপত্যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে কুবির গোঁসাই এর মতো অনেক সাধকের নাম, ধাম ও পরিচয়। লালনের সমসাময়িক এই সাধক মহাজন তার প্রয়াণের শতবর্ষ পার হতে না হতেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। এই মহান সাধক বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেন কার দোষে? নিশ্চয় তাঁর নিজের দোষ নয়। তাহলে কার দোষে? উন্নাসিক প-িতের? দেশভাগের কারণে? সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা কারণে? যার দোষেই হোক কুবির গোসাঁইকে আবিস্কার করতে হবে। কারণ তিনিও লালনের মত যুগন্ধর সাধক ও মানবহিতাকাক্সক্ষী মরমিয়া ছিলেন । তিনিও বলেছেন: ‘মানুষ হয়ে মানুষ মানো/মানুষ হয়ে মানুষ জানো/ মানুষ হয়ে মানুষ চেনো/মানুষ রতন ধন/করো সেই মানুষের অন্বেষণ’।
বেদ ব্রাহ্মণ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী সহজিয়া ও লৌকিক ধর্মের এই সাধক আরও বলেন:
‘হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল/মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষী গোপাল/বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মরো?/মানুষে করোনা ভেদাভেদ/করো ধর্মযাজন মানুষ ভজন/ ছেড়ে দাওরে বেদ/মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে/মানুষের উদ্দেশ্যে ফের।’
অর্থাৎ মানুষে মানুষে ভেদ নেই, মানুষ অমৃতের সন্তান। মাটির ঢিবি, মূর্তির মধ্যে ঈশ্বর নেই। বৈদিক শাস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে। হরিষষ্ঠী মনসা মাখাল নয় মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করতে হবে।
লালনও একই কথা বলেছেন তার এক গানে :
‘মানুষ তত্ত্ব সত্য হয় যার মনে
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে?
লালন ‘মাটির ঢিবি কাঠের ছবি’, দেব দেবতার পূজা অর্চনার বিরোধীতা করেছেন। তিনি মানুষকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন।
লালন ও কুবিরের জীবনদর্শনের মধ্যে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন. ‘লালনের সাধন ভূমি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া থেকে কুবিরের বৃত্তিহুদা সোজা স্থলপথেই যুক্ত ছিল। কাজেই লালনের গান যে বাউলদের সংলগ্ন থেকে কুবিরের কাছে একেবারে আসা অসম্ভব তাতো নয়।’ (সুধীর চক্রবর্তী, রচনাসমগ্র- ১০২)
আসলে লালন ও কবির দুজনেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানতাবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী। ধর্মের লোকচারকে প্রত্যাখ্যান করে লালন বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন:
‘ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে
হিন্দু-মুসলমান দুইজন দুই ভাগে।
আছে বেহেস্তের আশায় মোমিনগণ
হিন্দু দিগের স্বর্গেতে মন।’
মরমিরা মানবতাবাদী হলেও কোন ভাবেই তারা নিরীশ্বরবাদী নন। উদার সমন্বয়বাদী অধ্যাত্মচিন্তা আয়ত্ত করে আত্মিক মুক্তি ও জগৎ জীবনের রহস্য খুঁজতে চেয়েছেন তাঁরা। লালন ও কুবির দুইজনই ছিলেন একই পথেরযাত্রী। চমকে দেওয়ার মত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন কুবির এক চমকপ্রদ অনুভবে :
একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহবায় থাকেন আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
লালন ও কুবির দুজনেই তাদের গানে ও জীবনচর্যায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন। ষোড়শ শতকে নদীয়ার পথে পথে চৈতন্যদেব যে মহামিলনের বাণী উচ্চারণ করে ছিলেন, লালন ও কুবির সেই বাণীকে আরও লোকপ্রিয় করে তোলেন। তারা দুজনেই মুক্তকণ্ঠে চৈতন্যদেবের প্রচারিত মতবাদকে উদার চিত্তে স্বীকার করে জাত পাত, জপতপ, তুলসিমালা প্রত্যাখ্যান করেছেন। চৈতন্য যেমন বেদ পুরাণ অগ্রাহ্য করেছিলেন, উত্তরকালে লালন-কুবির একই পথ অনুসরণ করেন। তাদের বিশ্বাস:
১. এনেছে এক নবীর আইন নদীয়াতে
বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে। (লালন)
২. দয়াল গৌর হে তোমা বই কেহ নাই।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ
আমার মরণ কালে চরণ দিও
আর কিছুই না চাই। (কুবির)
৩. সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়। (লালন)
লালন মনে করেন, সনাতন ধর্মমতে যে চারযুগের কথা বলা হয়েছে তার মাঝখানে চৈতন্যদেব এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। এ যুগেই জাতগোত্রহীন মানব সমাজের উথান যা বোঝা কঠিন নয়। আর কুবির গোসাঁই তার সমন্বয়বাদী ধর্মচেতনা ও দার্শনিক ভাবনা দিয়ে চৈতন্যকে যীশু খ্রিস্টের সাথে একাকার করে ফেলেন। লালন ও কুবিরের গানের ভাব, প্রকরণ, প্রতীক, প্রতিমা বিশ্লেষণ করলে বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পলাশী যুদ্ধোত্তর সামূহিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনের সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয় আমাদের বিস্মিত করে এবং বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। কারণ দুজনেই একই কালপর্ব ও ভৌগোলিক পরিম-লে জন্ম গ্রহণ করেন।
লালন ফকির ছিলেন বাংলার লোকায়ত সাধনা ও গানের পরম্পরায় এক নিঃসঙ্গ পুরুষ, এ বিষয়ে কেউ আপত্তি তুলবে না। কিন্তু এখন তিনি দু বাংলার সাধক-গায়ক, রসিক ও গবেষকদের প্রাণের মানুষ, নন্দিত লোকনায়ক। তার বাণী, সাধনা ও গান নিয়ে ব্যাপক চর্চা চলছে। অথচ কুবির গোঁসাই এর গান জানা তো দূরে থাক, তার নাম পর্যন্ত বড় বড় প-িত-গবেষক জানেন না। বিস্মিত হতে হয়, লালনের গানের টেক্সট এবং তার অর্ধশিক্ষিত মুরিদদের হস্তাক্ষরে লিখিত গানের খাতা, শোনা গান ও পড়া গানের প্রভেদ নিরূপণ নিয়ে লালন অনুসারী ও গবেষকদের মধ্যে যখন তুমুল তর্ক- বিতর্ক ও বাকবিত-া চলছে, তখন কুবিরের গান নিয়ে কিন্তু সে ধরনের তেমন কোন সমস্যা নেই। কারণ কুবিরের গানের খাতা আজও চাপড়া থানার বৃত্তিহুদার ভক্তদের কাছে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। ১২০৯টি গানের মূল না হলেও মূলানুগ অনুলিখন তার সমাধি সংলগ্ন ভিটের পার্শ্ববর্তী এলাকার অনুসারীদের কাছে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। তাহলে কেন এই সাধক-কবিয়াল জাতে উঠতে পারলেন না; ব্রাত্য, উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত থেকে গেলেন ? তাহলে কী তার গান কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, না-কী শিল্পমানসম্মত ছিল না ?
‘ লক্ষী আর দুর্গা কালী, ফাতেমা তারেই বলি / যার পুত্র হোসেন আলি মদিনায় করেখেলা।’
অথবা, ‘ সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন/ হিন্দু যবন জাত নিরূপণ দুই কিসের কারণ।/ পুরুষের লক্ষণ প্রকৃতি আশ্রয়/ হল যুগেতে জন্ম সবার মর্ম বোঝে মহাশয়।’
এসব গানের ভিতর ভাবৈশ্বর্য, ধ্বনিমাধুর্য বা শিল্পগুণ সব আছে- কী নেই? তাহলে উপেক্ষার কারণ কী হতে পারে ?
ফকির লালন ছিলেন বাউল মতাবলম্বী ভাবুক, চিন্তক ও দর্শন বিশ্লেষক এবং কুবির গোঁসাই সহজিয়া সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক-গায়ক। কিন্তু কোথায় যেন দুজনের ভাবুকতা ও দর্শনে, সাধনা ও জীবন চর্যায় আশ্চর্য রকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুই জীবন রসিক সাধক দুঃখ সমুদ্র মন্থন করে আমাদের অমৃত দান করে গেছেন দুঃখ জাগানিয়া গান গেয়ে।
লালন বলেছেন:
‘কারে বলব আমার মনের বেদনা
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলেনা।’
আর কুবির বলেছেন :
‘দুঃখের দুখী পেলাম কই
দুটো মনের কথা কই।’
দুঃখজনক হলে সত্য যে, কুবির গোঁসাই ফকির লালনের মত গবেষক ও প-িতমহলে তেমন পরিচিত নন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, মীর মশাররফ হোসেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের মত মানুষরা তাঁর গানের খোঁজ পাননি। অথচ এই সাধকের গান, বহু বর্ণিল জীবন নিয়ে গবেষণা হতে পারতো কিংবা উপন্যাস রচনা করা যেতো। কেবল বিখ্যাতদের মধ্যে কেবল রামকৃষ্ণ দেবের নিকট কুবিরের ‘ডুবডুব রূপসাগরে আমার মন’ গানটি পৌঁছেছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এটি পাওয়া যায়।
লালনের মত ১১৬ বছরের দীর্ঘ জীবন না পেলেও কুবির বেঁচেছিলেন দীর্ঘ ৯২ বছর। এই সুদীর্ঘ জীবনে জীবিকার তাগিদে নানা কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। প্রথম জীবনে যুগী এবং পরবর্তীতে কবিয়াল হিসেবে আসরে আসরে গান গেয়ে বেড়াতেন। ভোলা ময়রা, এ্যাটনি ফিরিঙ্গির মত পেশাদার কবিয়াল হিসেবেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি একটি গানে বলেছেন :
‘আমার নাম কুবির কবিদার। /এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছি করে রোজগার।’
বৃত্তিহুদার চরণ পালের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁকে কবিগান করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। কিন্তু এই ‘সন্ন্যাসী উদাসীন’ কবিদার সংসারে থেকেও সংসারী হতে পারেননি। তিনি জাত কূলত্যাগ করে সারা জীবন ‘সাধুর দ্বারে পাতড়া চাটা’ হয়ে থেকেছেন গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রেখে। কুবির উচ্চ বংশজাত, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত এলেমদার কেউ ছিলেন না। কিন্তু নানা ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার গভীরজ্ঞান ছিল এবং মুসলমানদের সাথে সখ্য সম্পর্ক ছিল। সাহেবধনী ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে গিয়ে ইসলামী তত্ত্ব ভালভাবে জেনেছিলেন। এসব কারণে স্বসমাজ কর্তৃক শূদ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। গভীর ক্ষোভ নিয়ে তিনি একটি গানে বলেছেন:
‘মরি হায়রে আমি বুদ্ধি বিদ্যেহীন/তাই ভেবে মরি রাত্রি দিন/এই মুসলমানদের শাস্ত্র জেনে/আমি শূদ্র হইলাম কি কারণে।’
কুবিরের গানের ভুবনে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মর্মদর্শন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা তাকে পৌঁছে দিয়েছিল উদার, সমন্বয়বাদী মানবিকতার উন্মুক্ত প্রান্তরে।এ কথা অকপটে বলা যায় যে, তিনি তার বিরানব্বই বছরের জীবন পরিক্রমায় যা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তা অনেক সাধক মহাজন পারেননি।
দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুম-িত জীবন রসিক মানুষটি বাস করতেন স্ত্রী ভগবতী আর সাধন সঙ্গীনি কৃষ্ণমোহিনীকে নিয়ে। সহজিয়া কায়া সাধনে তার আগ্রহ ছিল সবিশেষ। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন বহুদর্শী, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ, জীবন রসিক, স্বকালের বিশ্লেষক ও রূপকার। জাতে যুগী, পেশায় তাঁতী, জীবিকায় কবিয়াল আর ধর্মে সাহেবধনী দীক্ষিত কুবির গোঁসাই ছিলেন অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী এক সাধক- গীতিকার। তিনি যেমন পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে গান বেঁধেছেন, তেমনি দেশকাল, সমাজ, শাসন-শোষণ নিয়েও গান রচনা করেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি, অভাব অনটন, দুঃখ দারিদ্রের বাস্তব চিত্র তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক কিংবা প-িতদের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য নয় চারপাশের পরিচিত জীবনকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য গান বাঁধতে ও গাইতে হয়েছে তাকে। আলকাপ গম্ভীরা তে সমকালীন জীবন বাস্তবতার ছবি যেমন ধরা থাকে, কুবিরের গানেও এমন অনেক কিছু পাওয়া যায়। মরমী সাধক লালনও জীবৎকালে অনেক বিতর্কিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন গানে গানে। ‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে’ গানটির মাধ্যমে লালন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।কুবিরও সমকালের ধর্ম, দর্শন, মানুষের দুঃখ-আনন্দ, প্রেম-বিরহ তথা যাপিত জীবনকে ব্যাখ্যা করে গেছেন গানে গানে। তিনি ছিলেন সাহেবধনী মতবাদের বলিষ্ঠ অনুগামী ও ভাষ্যকার। কিন্তু এই মতবাদ তাকে উগ্র সাম্প্রদায়িক করে তোলেনি বরং করেছে সমন্বয়বাদী। বাউলরা প্রতিবাদী হলেও তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। লালন ও দুদ্দুশাহ ছিলেন প্রতিবাদী আর কুবির ছিলেন ভিক্ষাজীবী দরিদ্র নিঃসঙ্গ সাহেবধনী। মননে, উপলব্ধিতে এবং জীবনচর্যায় তারা সবাই ছিলেন মানবিক অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ‘মানুষ সত্যের উপাসক’। প্রবৃত্তি সম্পন্ন পশু জীবনের চেয়ে মানব জীবন যে মহৎ তা কুবির প্রসন্ন চিত্তে বারবার বলেছেন। তিনি গেঁয়েছেন: মানুষ বৈ আর কিছু নাই’।
গীতিকার হিসেবে কুবির গোঁসাই ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী এবং মানুষ হিসেবে বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ। লালন সাঁই, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, হাউড়ে গোঁসাই প্রমুখ সাধক গীতিকবিদের গানে উল্লেখ করার মত বৈচিত্র্য নেই। তারা কেবল ভাবরস, দেহাত্মবাদ আর মানবিক আধ্যাত্মিকতার মহিমা বয়ান করে গেছেন। কিন্তু কুবিরের গানে তাঁত বোনা, চাষ করা, নৌকা বানানো, গ্রামীণ অর্থনীতি, আখমাড়াই, গুড় তৈরি প্রভৃতির বিবরণ রয়েছে নানা রূপকে। যেমন, নৌকা তৈরির ক্রমিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গেয়েছেন :
‘ আগে তলা গড়ে শেষে তক্তা জোড়ে/ আড়ে আরফোঁড়ে তাই না জানি? আরো গুড়ায় বসায় বাঁক তাতে মেরেছে পেরাক? গলুই জলুই আঁটা দুই কিনারায় মুক্তা মানিক।’
বাংলা ১২৭২ সালে নদীয়া জেলা জুড়ে বিধ্বংসী খরায় যে আকাল হয় , তাও এই মর্মজ্ঞ সাধক গেঁথে রাখেন তার মর্মস্পর্শী গানের পদাবলিতে:
‘ভুট করেছে গত সনের ঝড়ে- / আবার এই বাহাত্তর সালে ঘোর আকালে/ লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।/ বলে অন্ন বিনে ছন্নছাড়া ধান্য গেছে পুড়ে।।’
এসব গান বিশ্লেষণ করলে সাধক, কবিয়াল, গীতিকার কুবির গোঁসাই-এর যে প্রতিমূর্তি প্রবলভাবে ফুটে ওঠে তা মানবিক। বিশেষ এক লোকধর্মের অনুসারী হয়েও তিনি ছিলেন সমকাললগ্ন ও যুগন্ধর পুরুষ। এজন্য বাংলা লৌকিক গানের ইতিহাসে তাঁর আসনটি আজও স্থায়ী হয়ে আছে। ‘তিনি যে লালশশীর চেয়ে বড় কবি এবং লালন ফকিরের চেয়ে বড় দ্রষ্টা ছিলেন তাতে বির্তক নেই। তাঁর বিরানব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবন সংকীর্ণ গ্রামজীবনেই কেটেছে। সম্মান, খ্যাতি, সাধনাসিদ্ধি ও গান রচনা, সবদিক থেকেই সফল ছিলেন কুবির।’ (রচনা সমগ্র: পৃ: ৬৭)। মধ্যযুগে এক নিস্তরঙ্গ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেও কুবির যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেনদের মত মানুষের সান্নিধ্য না পেয়েও এই গ্রাম্য সাধক ছিলেন সত্যিকারের স্বনির্মিত মানুষ। তার গানের ভেতর আমরা যত প্রবেশ করি ততই বিস্ময়াবিষ্ট হই মানুষটির ভাবুকতায় ও সৃজন নৈপুণ্যে। কিন্ত প্রশ্ন থেকে যায়, কেন কুবিরের নাম প্রায় অবজ্ঞাত থেকে গেল ? লালন ও কুবির দুজনেই মহাভাব-সাধক, তারপরও কেন কুবির ব্রাত্য ও অপাঙক্তেয় থেকে গেলেন ? হয়তোবা দেশভাগ অথবা কুবিরের জীবনে লালনের মতো ধর্মান্তরিত হওয়ার চমক ছিল না, তাই। কিন্তু কুবির তো হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে আল্লাহকে সেজদা করেছিলেন। লালনের মত তিনিও বুকের ভিতর জাপটে ধরেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের জগাই-মাধাই দুজনকেই, নদীয়ার সমন্বয়ী ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে।
‘ রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা/ হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা/ এক চাঁদে জগৎ উজলা।’
অবশ্য লালনের গানেও ওই একই ভাব মেশানো, তিনিও গেয়েছেন: এক চাঁদে হয় জগৎ আলো/ এক বীজে সব জন্ম হইল/ লালন বলে মিছে কল/ কেন শুনতে পাই ?’
বৃত্তিহদার অনতিদূরে ১৮৩৮ সালে ক্যাথলিক চার্চ এবং ১৮৪০ সালে চাপড়ায় প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টম-লী গড়ে ওঠার পর থেকে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ভক্ত , অনুরাগী ও দীক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে থাকে ধর্মান্তকরণের কারণে। একদিন হয়তো বিলীন হয়ে যাবে সাহেবধনী সম্প্রদায়। সাথে সাথে মাটিতে মিশে যাবে কুবিরের সমাধি মন্দির। কিন্তু কুবির ও এই সম্প্রদায়ের গান বেঁচে থাকবে নদীয়া, ২৪-পরগণা, যশোর, বর্ধমান, পাবনা অঞ্চলের অজপাড়া গ্রামের সাধক ও গায়কদের কণ্ঠে। কারণ কুবিরের গানের বাণী ও সুরে লুকিয়ে আছে, বাংলার জনজীবন , একটি কালপর্ব ও লৌকিক গৌণ সম্প্রদায়ের সাধন ভজন, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ ও কান্না-হাসির মর্মকথা।
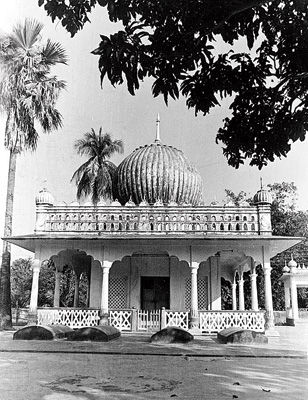
©somewhere in net ltd.
১| ০২ রা ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১২:৩৮
০২ রা ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ১২:৩৮
রক্তিম দিগন্ত বলেছেন: চমৎকার একটি পোষ্ট। +