| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চার ও বিকাশের প্রথম ও মধ্যযুগ হিসাবে সুলতানী আমলকেই ধরা হয়। তবে সে চর্চা পুথি, অনুবাদ ও নানা রকম লোকসাহিত্যের মাধ্যমে অব্যাহত থাকলেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আগে ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে বাংলার বিকাশ প্রায় রূদ্ধই ছিল। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা তার পূর্ববর্তী গঠন পরিবর্তন করে নতুন ভাবে গঠিত হতে শুরু করে এবং ভাষার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য ও নব নব শাখায় বিকাশিত হয়। এক কথায় ঊনিশ শতকে সাহিত্যের এক স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। তবে তার আগে গঠিত হয় সেই সাহিত্যের উপযোগী ভাষা নির্মান। এই নির্মানের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর,দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র,কালী প্রসন্ন সিংহ থেকে নিয়ে তত্কালীন আরো অনেকে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
ভাষা নির্মানে প্রধান ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজেরাও সৃষ্টি করেছেন উন্নত মানের সাহিত্য এবং এর ভিত্তি রচিত হয় মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার আধুনিকরনের মাধ্যমে।
এই আধুনিকরন বা উন্নয়ন না হলে ঊনিশ শতকের যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তা ছিল প্রায় অসম্ভব।
আধুনিক যুগের প্রথম পর্বের শেষে বাংলা সাহিত্যে আগমন ঘটে আরো নতুন নতুন কবি সাহিত্যিকের, যারা তাদের নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে।সৌন্দার্য মন্ডিত করতে কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন বিদেশী শব্দের। তবে পাকিস্তানী আমল থেকেই বাংলা ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতির করার অনেক চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। বাংলাকে নিষ্কিয় করতে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল অন্য ভাষা। যদিও কোনভাবেই তা তারা সফল করতে পারেনি। আমরা আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্যকে রক্ষা করতে রাজপথে ঢেলে দিয়েছিলাম বুকের তাজা রক্ত। বাংলাকে শুধু রাষ্ট্রভাষা নয় শিক্ষা সংস্কৃতির মাধ্যম করাও ছিল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
এজন্য ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর আমরা চ্যালেন্জ নিয়ে ছিলাম, ৭১ সালের পর থেকেই আমাদের উচিত ছিল এই চ্যালেন্জ মোকাবেলা করার। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ৬২ বছর পার করলেও আমরা আমাদের চ্যালেন্জ মোকাবেলায় ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা আমাদের স্বীকার করতে হবে। শুধু ফেব্রুয়ারী মাস এলেই ভাষা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়ে যায় । চেতনার বহ্নিশিখা চতুর্দিক ছড়িয়ে পরে। মিছিল মিটিং সেমিনার বক্তৃতা থিয়েটার মঞ্চে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার তুড়ি ছোটে। আবার ফেব্রুয়ারী মাস গেলেই বাংলা ভাষার চেতনা হারায়। বলা যায় বর্তমান আধুনিক ছেলেমেয়ের কাছে অনেক ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা নিয়ে বলা, বাংলা ভাষা নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া আত্মপ্রসারী ফ্যাশনের অংশ হয়ে দাড়িয়েছে।
আবস্হানগত সুযোগ সুবিধার জন্যই ভাষার ঢোল গলায় ঝুলিয়ে বেড়ায় কয়েক দিন। তারপর আবার যেই সেই !
প্রতিবছর বাংলা একাডেমি একুশের চেতনায় বই মেলার আয়োজন করে। বইয়ের মান বিচার না করেই বিনা বাধায় প্রতি বছরই প্রকাশিত হয় হাজার হাজার বই, বিক্রয় হয় স্টল গুলোতে। এখানেও চোখে পড়ে নানা রকম অসংঙ্গতি। বেশির ভাগ বইয়ের নামকরণ, বানান, শব্দ চয়ন, বাগভঙ্গি ও বিষয় বস্তুর মধ্যে মারাত্মক ভুল দেখা যায়। অন্যদের কথা বাদ দিলাম প্রকাশকদের অনেকের কাছ থেকেই শোনা যায় এসব বইয়ের বেশির ভাগই অপাঠ্য ও মুদ্রিত আবর্জনা। যেগুলো তারা ছাপছে লেখকদের টাকায়, বানিজ্যিক কারনে মুনাফা অর্জনের জন্য।
এছাড়া স্কুল কলেজের পাঠ্য বইতেও প্রতি বছরই দেখা যায় ভুলের ছড়াছড়ি। ভুলের পরিমান এত গুরুতর, যা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।
আর সাধু ভাষা চলিত ভাষার মিশ্রন তো আছেই।
ছোট বেলা দেখেছি সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রন দূষণীয় এই কথাটা বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নের উপরিভাগে লেখা থাকতো কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োগ দেখিনি।
বরং এই ব্যাপারে আজ সবাই উদাসীন চিন্তা পর্যন্ত করার সময় নেই।
একটা জগা খিচুড়ি মার্কা ভাষায় আমারা আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দীক্ষিত হচ্ছে। যেখানে নীরব বিপদ হিসাবে প্রয়াত, মহোদয়, চাচা, মহাত্মের বদলে হাই, হ্যালো, হ্যান্ডশেক, আংকেল ইত্যাদি হাজার হাজার শব্দ শুধু বলাতে নয় সাহিত্যে এসে জবরদখল স্বত্ব জারি করেছে।
এসবের দায় কে নিবে ?
অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষকেই তা বহন করতে হবে এবং জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
বর্তমান সময় অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে মুহুর্তের মধ্যে সব খবরাখবর সম্পর্কে জানা যায়।
আবার এর মাধ্যমে সম্ভব শিক্ষাদীক্ষা ভাষা ব্যবহারসহ অনেক কিছু শেখার। কিন্তু দেখা যায় শেখানেও মারাত্মক ভুল ভাবে, ভুল শব্দ চয়নে উপস্হাপিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সমাজের প্রতিনিধিস্হানীয় ব্যক্তিদের অহরহ ভুল উচ্চারন ভঙ্গিমা তো লেগেই আছে।
তাছাড়া বর্তমান টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল গুলো যেন বিকৃত বাংলা প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বাংলা সিনেমার বাংলার নাম করে অদ্ভূত সংলাপ ব্যবহ্নত হচ্ছে যা বাংলার মত শুনতে মনে হলেও প্রকৃতিতে হিন্দি ইংরেজীর এক মিশ্র সংস্করন।
সব জায়গাতেই প্রমিত মাতৃভাষার অস্তিত্ব প্রায় নির্বাসিত । আঞ্চলিকতার ছড়াছড়িতে সর্বত্র একটা হযবরল অবস্হা।
তবে এক মহাসত্য স্বীকার করতেই হবে যে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা অবহেলিত হওয়ার মুল কারণ, যে শ্রেনী ১৯৭১ সালের পর ক্ষমতাসীন হলো তাদের চরিত্র ও কার্যকালাপের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। কারণ রাষ্ট ও সরকার যদি বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচলন চাইত এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করত তাহলে বাংলা ভাষার অবস্হা আজ এমন হতো না।
ইংরেজ আমলের আগে মুঘল যুগে ফার্সি ছিল আইন আদালতের ভাষা। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহনের পর রাতারাতি ফার্সী বদলে ইংরেজী চালু করেনি। রাষ্টভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী করতে প্রয়োজনীয় সময় নিয়েছিল। ১৮৩৭ সালে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষিত হলেও আরো কয়েক বছর লেগেছিল সব জায়গাতে ইংরেজী চালু করতে। কিন্তু ১৯৭২ সালে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ক্ষমতাসীন রাতারাতি ইংরেজীকে উঠিয়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে, যার বিষময় ফল এখন শিক্ষা সংস্কৃতির সবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।
যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে মাদ্রাসা নিতান্তই করুনা নিয়ে বেচে আছে।
অনেক ক্ষেত্রে কিছু ইংরেজী মাধ্যম প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষাকে বিদ্রুপ পরিহাস কটাক্ষ করতেও দেখা যায়।
এ পরিবেশ পরিস্হিতিতে ভাষা সাহিত্য ও বিদ্যা চর্চার যে পরিনতি স্বাভাবিক ভাবে তাই হয়!
ভাষা ও বিদ্যা চর্চার বর্তমান অবস্হা তুলে ধরার নিমিত্তে এতক্ষন এত কথা ব্যাখ্যা কর লাম।
ভাষাকে একটা সমাজের দর্পন বলা যায়। কারণ ভাষার আর সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় সমাজের নানা দিক। আর এ কারনে মাতৃভাষার জন্য আমরা প্রান দিতে কুন্ঠা বোধ করিনি।বাংলাকে শুধু রাষ্টভাষা নয় বরং শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যের মাধ্যম করাও ছিল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্ষোভ হয় যখন দেখি ভাষা আন্দোলনের এই দেশে কিছু মানুষ বাংলার থেকে অন্য ভাষায় কথা বলতে বেশী স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।মনে হয় সেদিনের ভাষা শহীদরা আজকের দিনে বেঁচে থাকলে মনের দুঃখে না জানি কি করতেন।
তবে এটা বোঝা যায় পাকিস্তানীদের বুদ্ধি অনেক কম ছিল।কারন তারা যদি জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে কৌশলে ডোরেমন টাইপ কিংবা চোখ ধাধানো উর্দু সিরিয়াল বানাতো তাহলে আমরা এমনিতেই উর্দুতে কথা বলতাম। যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে আজ হিন্দিতে বলছি।আমাদের সংস্কৃতিতে হিন্দির অনুপ্রবেশে কোমলমতি শিশুরা শুধু হিন্দি বলাই শিখছে না বরং হিন্দি সংস্কৃতির ভিতর যে বিকৃতি আছে তাও শিখছে।যখন আমাদের উপর উর্দু চাপানোর কথা হলো তখন আমরা বিরোধীতা করলাম কিন্তু কৌশলে আজ হিন্দির প্রবেশকে মেনে নিচ্ছি।এটা আমাদের জন্য লজ্জানয়,বিপদও বটে। কারণ এরকম সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটে গেলে বেরিয়ে আসা কষ্ট কর হবে।
বর্তমান সময় আরেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে তাহলো দেশের সবক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা চলছে।বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।দেশের কোথাও আজ সুশাসন আইনের যথার্থ প্রয়োগ নেই।তাই কেউ আইন মানতেও চায় না, বেআইনি কাজের ভিতর মজা খুজে পায়। অনেকে মনে করে আইন না মানার ভিতর এক ধরনের বাহাদুরী আছে।সেই বেআইনি বাহাদুরী ভাষার ক্ষেত্রেও দেখাচ্ছে।যে যার মত ভাষার আইন ভঙ্গ করে ব্যবহার করছে।আমরা ইংরেজী অশুদ্ধ বললে লজ্জা পাই কিন্তু বাংলার বেলায় গুরুত্ব দিচ্ছি না।গুরুত্ব না দেওয়ার কারন হচ্ছে বেআইনি কাজ করায় আমাদের আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হয়নি।এজন্য এটাও বুঝতে চাইনা নিজের ভাষাকে ছোট করে বিপরীত সংস্কৃতির অন্য কারো ভাষাকে টেনে আনার মধ্যে কোন বীরত্ব নেই।এতে বরং ক্ষতির আশংকাই প্রবল। কিন্তু তারপরও আমরা ভিন্ন ভাষাকেই গ্রহন করছি।আমরা বাংলা ভাষায় কথা বললেও তার সাথে ঘাটাছি ভিন্ন ভাষার মিশ্রন নিজ ভাষাকে গ্রহন করতে পারিনি হ্নদয় থেকে,পারিনি সর্বস্তরে আজও বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে। উচ্চতর আদলতের ভাষা এখন ও বাংলা হয়নি। যদিও বিচারক বাঙ্গালী, বাংলা ভাষায় কথা বলে,বাদী বিবাদী বাংলা ভাষায় কথা বলে।উকিলরাও বাংলা ভাষায় কথা বলছেন। তারপরও উচ্চ আদলতের ভাষা বাংলা হয়নি। যেখানে রায় দেয়া হয় সকল কিছু বাংলা করতে হবে কিন্তু রায়টা লেখা হয় ইংরেজীতে।
এর কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সাধারন ব্যাখ্যায় বলা যায় দীর্ঘ দিনের অভ্যাস!
আবার উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার না হওয়াটাও আমাদের ব্যর্থতা, লজ্জা জনকও বটে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আমরা ইংরেজী ও অন্য ভাষা শিখবো তবে তা মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। উচ্চতর শিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রচলন যে সম্ভব এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি করা সম্ভব তা প্রমানের দায়িত্বও রাষ্টের নেয়া উচিত ছিল। তা না করে নীরব ভূমিকায় আবর্তীর্ন হয়েছে।
ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলা বাংলা করে,
সবকিছু তে ইংরেজী রেখে ভাষা প্রেম কি মানায়?
সবকিছুর মত বর্তমানের ভাষাবিদ সংস্কৃতিককর্মী সাহিত্যিকরাও দলীয় করন হয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তবে সবাই যে এমন তা নয় ভিন্ন মতাদর্শেরও আছে যদিও সংখ্যাটা খুবই কম এবং বিছিন্ন। যারা বিক্রিত তারাই সংখ্যায় ভারী এবং সংঘবদ্ধ।যে যার দল নিয়ে ব্যস্ত এবং দলীয় ঘরকোনা সাহিত্য রচনার কারনে ভাষা গঠন,প্রমিতকরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় গবেষনা বা বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখন তাদের নেই। তারা এখন বিভিন্ন পুরস্কার ও দলীয় সুযোগ সুবিধার পিছনে ছুটছে। এবং এগুলো পাওয়ার জন্য নানা প্রকার তত্পরতা ও ধান্দাবাজিও করা হয় অনেকের পক্ষ থেকে। এটা এক রকমের অশ্লীল ব্যাপর তো বটেই দুর্নীতিরও দৃষ্টান্ত।
সমাজে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বীপের মত কোন বিছিন্ন জিনিস নয় বরং সবই সমাজের অবিচ্ছেদ অংশ।কাজেই সমাজের পরিবর্তন ছাড়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে এখন যে পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে তাতে পরিবর্তন ঘটানো সহজ নয়। এগুলোর জন্য দরকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেখানে থাকবে মেধার মূল্যায়ন, থাকবে দায়বদ্ধতা জবাবদিহিতার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্হাপনের নিদর্শন। যেখানে এ প্লাস না পাওয়ার দুঃখে কেউ আত্মহত্যা করবে না। কারণ ফলাফল দিয়ে মেধা যাচাই কখনও সম্ভব নয়। ফিরিয়ে আনতে হবে সত্,নিষ্ঠাবান,সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্প কাব্যসাহিত্য সেবী ও জ্ঞানান্বেষনকারীর উপস্হিতি।
ভাষা প্রমিতকরন,বানান,শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তু সঠিক ভাবে প্রয়োগের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আগমন নিশ্চিত। তাছাড়া বই প্রকাশনার ক্ষেত্রেও একটা বাছাই কমিটি গঠন করা দরকার।যাতে ত্রুটি বিচ্যুতির পরিমান রোধ করা অনেকটাই সম্ভব হয়। বই প্রকাশকম হোক তবে যেটা হবে সেটা যেন অবশ্যই মানসম্মত হয়।
বংশপরম্পরায় মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে ভাষার উন্নায়নে কাজ করতে হবে। তাহলেই সম্ভব পর হবে বর্তমান ভাষার বিকৃতি ব্যবহার রোধ,সাহিত্য স্হান পাবে উপযুক্ত ব্যবহার।
তাহলে সম্ভব হবে একুশের চেতনাসহ জাতিসত্তার সকল অর্জনকে বাঁচানোর জন্য একবিংশ শতাব্দীর ভয়ানক চ্যালেন্জ কে গ্রহন করার।
তাহলে যেমন ঐতিহ্যের সোনালী অতীতকে রক্ষা করা যাবে তেমনই ভবিষ্যতেও মাথা উচু করে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে, আপন ভাষাকে আকড়ে ধরে। 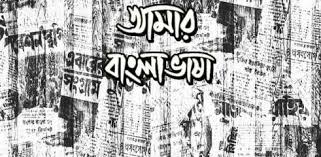
©somewhere in net ltd.