| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
 দীপক ৭৪ রায়
দীপক ৭৪ রায়
Dipak Ray, Kalirhat, Krishnagar, Nadia, WB, India, Ph. 9775179985 Mail. [email protected]আমি লিখি, লেখার চেষ্টা করি। যা বিশ্বাস করি না, তা লিখি না। শিক্ষকতা আমার পেশা, লেখালেখি-সাংবাদিকতা নেশা। আমার লেখার সমালোচনা হলে, আমি সমৃদ্ধ হই।
'মরিচঝাপি' পর্ব-২
(সংক্ষিপ্ত বিবরন)
দীপক রায় (২৪-১১-১৭)
# মরিচঝাঁপি একটি দ্বীপের নাম। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবস্থিত মোটামুটি দেড়শো বর্গকিমির একটি ছোট্ট নির্জন দ্বীপ। দক্ষিন ২৪ পরগনার আর পাঁচটা দ্বীপের মতো মরিচঝাপি কিন্তু সমুদ্রের অভ্যন্তরে নয়। সংরক্ষিত সুন্দরবনের ভিতরে কতগুলি নদী, উপনদী বেষ্টিত একটা দ্বীপ। উত্তরদিকে নদীর ওপারে রয়েছে কুমিরমারি ও ছোট মোল্লাখালি, আর পূর্বে সাতজেলিয়া ও সাধুপুর। পূর্বে কিছুটা গেলেই নদীর ওপারে বাংলাদেশের সুন্দরবন।
# মরিচঝাপি যেহেতু সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সেই কারনে সেখানে মানুষের বসবাস আইনসিদ্ধভাবেই নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ সরকারের সময় থেকেই ভারত সরকার এই ধরনের বনাঞ্চলে কোন ধরনের মানুষের স্থায়ী বসবাস করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। ফলে এই ধরনের বনাঞ্চল রক্ষা করতে সংস্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিও আইনানুগভাবেই বাধ্য।
# ১৯৭৭ সাল। বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হল। কেন্দ্রে জনতা দলের সরকার। বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত তখনও আসা বন্ধ হয়নি। মধ্যপ্রদেশের মানা ক্যাম্প, উড়িষ্যার দন্ডকারন্য ক্যাম্পেও ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা। আর বাংলাভাষী মানুষ বাংলারই কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে অন্য রাজ্যের ক্যাম্প থেকে বাংলায় এসে বসবাস করার একটা তাগিদ উদ্বাস্তুদের ছিলই। তাঁর উপরে উদ্বাস্তু আন্দোলনে সফল বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে, সুতরাং একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে, এমন ধারনাও উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে ছিল। পাশাপাশি কিছু অবিবেচক নেতা গোছের মানুষ, যারা নিজেরাই অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছিলেন, পরবর্তী পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা না করেই। বামফ্রন্টের নেতানেত্রীদের ক্ষমতায় আসার আগে উদ্বাস্তু বিষয়ক কিছু বক্তব্যও এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এমন কিছু মানুষ, যারা পরে মরিচঝাপি আন্দোলনের মধ্যমনি ছিলেন, তাদের প্রশ্রয়ে, বক্তব্যে, সাহায্যে দলে দলে প্রথমে বর্ধমান ও পরে কাকদ্বীপ ষ্টেশানে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে তারা কুমিরমারী ও সাতজেলিয়া দিয়ে পৌঁছে যান মরিচঝাপি।
# মনে রাখতে হবে সময়টা ১৯৭৮ সাল। ফলে দ্রুত খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যাবে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দেরিতে হলেও খবর গিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে উপরেও খবর গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কত মানুষ দ্বীপে গিয়েছে, সেই তথ্য প্রশাসনের কাছে ছিল না। তাঁর কারন, প্রথম থেকেই প্রশাসন ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই গিয়েছে। ১৪ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার নানা মুনির নানা মতের লেখা বেরিয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা জানা প্রশাসনেরও সম্ভব হয়নি। সেই সময়ের খবরের কাগজগুলি, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, প্রশাসনের বক্তব্য, সংসদীয় দলের রিপোর্ট, স্থানীয় মানুষের বক্তব্যে তাই সংখ্যা নিয়ে ভুতুড়ে হিসেব আজও রয়ে গিয়েছে। তবে বেশ কয়েক হাজার উদ্বাস্তু মানুষ সেখানে গিয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এত মানুষ একসাথে একটা দ্বীপে আশ্রয় নিলে পাশের গ্রামগুলির ব্যবসার আর্থিক চেহারা বদলাবে এটা স্বাভাবিক। আর হয়েছিলও তাই। কারন মরিচঝাপিতে কিছুই ছিল না। এত মানুষের থাকা খাওয়ার জন্য সাতজেলিয়া আর কুমীরমারীর ব্যবসায়ীরা তাই ফুলে ফেপে উঠেছিল। রাজ্য সরকারের নির্দেশ পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েত তখন পাশের গ্রামগুলিতে উদ্বাস্তুদের জন্য পানীয় জল, চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। নইলে মহামারী দেখা দেবার সম্ভবনা ছিল। কিন্তু যেহেতু মরিচঝাপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, ফলে দ্বীপের ভিতরে সরকার বা প্রশাসন কোন কিছু করেনি।
# রাজ্য সরকার রিপোর্ট পাঠায় কেন্দ্রীয় সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানায়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কোন বসতি গড়তে দেওয়া যাবে না। বেশ কয়েকবার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনার পরে বিষয়টিকে মেটাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রচার চালানো হয়, মরিচঝাপি ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য। রাজনৈতিকভাবেও আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। জ্যোতি বসু ও তাঁর সরকারের কঠোর নির্দেশ ছিল, বলপ্রয়োগ করে কাউকে ফেরত নিয়ে আসা হবে না। বুঝিয়েই ফেরত আনতে হবে। কিন্তু ততদিনে একদিকে মরিচঝাপিতে, আরেকদিকে মূল ভুখন্ডে রাজনৈতিক প্রভুরা ময়দানে নেমে পড়েছেন। সংগঠন তৈরি হয়েছে। কুমিরমারী, সাতজেলিয়ার ব্যবসায়ীরাও সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কারন এত মানুষ দ্বীপে থাকা মানেই তাদের বানিজ্যিক সুবিধা। সেটা তারা নষ্ট হতে দেবেন কেন? আর দ্বীপের অসহায় মানুষের মাধ্যমে নদীপথে সরকারী গাছ কেটে নতুন ব্যবসাও ফেদে বসেছেন অনেকেই। নদীর ওপারে বাংলাদেশ। ফলে চোরাপথের লাভজনক বানিজ্যের সুবিধাই বা তারা নষ্ট হতে দেবেন কেন? ফলে সরকারী বা শাসক দলের যত প্রচার হয়েছে মরিচঝাপি ছেড়ে বেরিয়ে আসার, ততই জোটবদ্ধ হয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী আর সেখানকার উদ্বাস্তুদের নেতারা। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন মরিচঝাপিতে প্রবেশ না করে, নানাভাবে আলাপ আলোচনা ও মরিচঝাপি থেকে বেরিয়ে আসার প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল।
# ১৯৭৮ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীর শেষ অবধি মরিচঝাপির বাসিন্দারা বিনা বাধায় বসবাস করেছিল। প্রশাসন বলপ্রয়োগ করেনি। জানুয়ারীর শেষে যখন ১৪৪ ধারা জারি করা হয়, তখন মরিচঝাপিতে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মরিচঝাপি নিয়ে যতই হইচই করা হোক, বাস্তবে সেটা যে বসবাসের অযোগ্য, সেটা বুঝে অনেক উদ্বাস্তুই মরিচঝাপি থেকে চলে যান। ফলে খুব বেশি পরিবার শেষ অবধি সেখানে ছিল না।
# পুলিশের গুলিচালনার ঘটনা ঘটেছিল কুমিরমারীতে। আর তাতে যে দুজন মারা গিয়েছিল, তারা কুমীরমারীরই বাসিন্দা। মরিচঝাপির নয়। এর পরে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠলে রাজ্য সরকার মরিচঝাপি ফাঁকা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৬-৩১ জানুয়ারী ৩০ টি লঞ্চ মরিচঝাপিতে পৌছায়। ক্রমাগত মাইকে প্রচার চলতে থাকে। সেখানকার বাসিন্দারা শেষ অবধি সেই লঞ্চেই ফিরে আসেন। প্রশ্ন ওঠে এত মানুষ কোথায় গেল? তাহলে কি সব মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে? উঠে আসে নানা তথ্য। বহু প্রত্যক্ষদর্শী নানা কাগজে নানা রকমের বিবৃতি দেন। অধিকাংশ নেতাই পালিয়ে যান দন্ডকারন্যে, মানা ক্যাম্পে, কেউ বা বাংলাদেশে। তারা হয়ে যান সব বড় বড় ব্যবসায়ী। অসহায় মানুষদের ফেলে চলে যাওয়া সেও এক ইতিহাস।
# কিন্তু যে প্রশ্ন নিয়ে এত আলোচনা সে হল গনহত্যা। গনহত্যা কবে হল? এই নিয়ে বহু বই, চলচ্চিত্র, নিউজ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা বারো থেকে ছত্রিশ, দেড়শো থেকে তিনশো ছাড়িয়ে হাজার হাজারও লেখা হয়েছে। এক বিদেশী গবেষক তো রীতিমতো থিসিস লিখে গবেষণালব্ধ বই বের করে ফেলেন। যার মোদ্দা কথা, সুন্দরবনের বাঘেরা মানুষখেকো হয়েছে, মরিচঝাপিতে পুলিশের গুলিতে মরা লোকের মাংস খেয়ে!
# আন্দোলনকারীদের যে সব ডকুমেন্ট পরবর্তীতে পাওয়া গিয়েছে বা তারা মৃত্যুর যে খতিয়ান দিয়েছে, তার সংখ্যা কত? হাজার হাজার বা শত শত মৃত্যুর তথ্য কিন্তু তাদের ডকুমেন্ট বা বিবৃতিতে নেই। ঘটনার পরে আসা সংসদীয় দলের মারফৎ যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়েছিল্ সেই রিপোর্টেও মৃত্যুর সংখ্যা দেখলে বর্তমান মরিচঝাপিপ্রেমীরা নিরাশই হবেন।
তাহলে কোন তথ্যকে মান্যতা দেওয়া হবে? পুলিশের তথ্য? রাজ্য সরকারের তথ্য? কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য? সংসদীয় দলের তথ্য? সংবাদ পত্রের তথ্য? আন্দোলনকারীদের তথ্য? কোন আন্দোলনকারীর তথ্য? সেখানে তাদের তথ্যে তো আকাশপাতাল তফাৎ! পরবর্তীকালে প্রকাশিত বইপত্র বা ইন্টারনেটের তথ্য? কোনটা বিশ্বাস করব?
# সত্যি সবসময় সত্যিই হয়। পুলিশের গুলিচালনায় কুমীরমারীর দুইজন নিহত হবার ঘটনা বাস্তব। কিন্তু মরিচঝাপিতে তাহলে কি কোন মৃত্যু হয়নি? সত্যিটা বেরিয়ে পড়েছে এই বিষয়ে 'গনহত্যার কাহিনী' লেখা নানা নিবন্ধে। সেখানে একটা কথাকে তারাও মান্যতা দিয়েছে। একটি লেখায় আছে, ''সরকার তাদের সরাসরি গুলি করে হয়তো সবাইকে মারেনি, কিন্তু ১৪৪ ধারা জারি করে তাদের ভাতে মারা হয়েছে্ পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। সেভাবে পালাতে গিয়েও বহু মানুষ মারা গিয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে।''
# আসল সত্যিটা এখানেই। এগারো মাস ধরে সরকার তাদের মরিচঝাপি ছাড়তে ধারাবাহিক প্রচার করেছিল। বেশিরভাগ মানুষ সেখানে যে নিদারুন কষ্টে ছিল, সেই অভিজ্ঞতায় তারা মরিচঝাপি ছেড়েছিল। আন্দোলনকারীদের চাপে অনেকে ছিলেন, স্বেচ্ছায়ও অনেকে ছিলেন। বাস্তবে শেষ অবধি অল্প সংখ্যাই ছিল। তাই মাত্র ৩০ টি লঞ্চে তাদের ফেরত আনা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধাহীন একটা বিচ্ছিন্ন এলাকায়, বসবাসের অযোগ্য এলাকায় থাকায় অবশ্যই কিছু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। যতই লবনের কারখানা, উন্নত চাষ, ইস্কুলের কথা বলা হোক না কেন- আদপে মরিচঝাপি একটা মানুষের বসবাসের অযোগ্য জায়গাই ছিল।
# এই বর্ণনা একটা সাধারন লেখা মাত্র। এখানে কোন অকাট্য তথ্য নেই। তথ্য ছাড়া কোন বক্তব্যই মান্যতা দেওয়া যায় না। তাই পরে আসব তথ্য নিয়ে। তথ্য গুলো ফাসিয়ে দেবে মরিচঝাপির গল্পের বেলুন! তাঁর জন্য একটু অপেক্ষা করুন। সবুরে মেওয়া ফলে।
(চলবে...পরের পর্ব...কারা কি কি বলেছেন...) 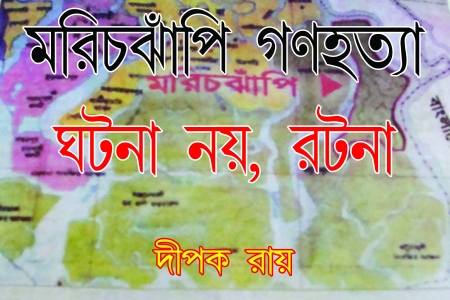
২| ![]() ০৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ রাত ১১:০৩
০৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ রাত ১১:০৩
রসায়ন বলেছেন: হুম
©somewhere in net ltd.
১| ০৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ রাত ১০:৩০
০৩ রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ রাত ১০:৩০
রাজীব নুর বলেছেন: ঠিক আছে তথ্যের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।