| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
 ক্ষয়রোগ
ক্ষয়রোগ
আমি এখন ভিন্ন মানুষ অন্যভাবে কথা বলি কথার ভেতর অনেক কথা লুকিয়ে ফেলি, কথার সাথে আমার এখন তুমুল খেলা...
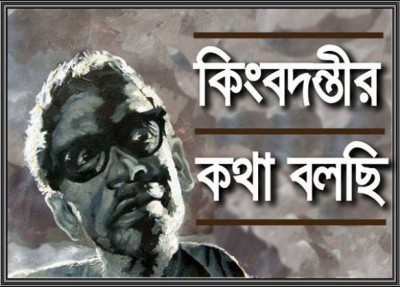
বাংলা চলচ্চিত্রের এক ধ্রবতারা ঋত্বিক ঘটক। তার নির্মাণ করা চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে কিংবদন্তী। বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। পাশাপাশি ছিলেন গল্পকার, নাট্যকার এবং অভিনেতা। পুরান ঢাকার আদি বাসিন্দা এই মনীষি মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।
উল্কার মতোই জ্বলে ওঠে ধুপ করে নিভে যাওয়া এক খ্যাপা শিল্পস্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক। তাঁর সৃজনশীলতার সূচনা করেন কবি এবং গল্প লেখক হিসেবেই। এরপর তিনি মঞ্চের সাথে যুক্ত হোন আর ধীরে ধীরে গণনাট্যসংঘের সাথে জড়িয়ে পড়েন। সেখানই সেলুলয়েডের হাতছানি তাকে পেয়ে বসে। মাত্র ৫১ বছরের জীবদ্দশায় ঋত্বিক কুমার ঘটক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পেরেছিলেন ৮টি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন সবমিলিয়ে ১০টি। আরও অনেকগুলো কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্রের কাজে হাত দিয়েও শেষ করতে পারেননি। এই হাতে গোনা কয়েকটি চলচ্চিত্র দিয়েই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারদের কাতারে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি।
১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার জিন্দাবাজারের জন্ম গ্রহণ করেছিলেন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক। ঋষিকেশ দাশ লেনে ঐতিহ্যময় ঘটক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঋত্বিক ঘটকের বংশের আদি পুরুষ পণ্ডিত কবি ভট্টনারায়ণ। ঋত্বিকের বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি কবিতা ও নাটক লিখতেন। তার বদলীর চাকুরীর কারণে তারা ঘুরেছেন দেশের নানা প্রান্তে। তাঁর বাবা অবসরের পর রাজশাহীতে গিয়ে বাড়ি করেন; উল্লেখ্য যে তাদের রাজশাহীর বাড়িটাকে এখন হোমিওপ্যাথিক কলেজ করা হয়েছে এবং তার নাম ঋত্বিক ঘটক হোমিওপ্যাথিক কলেজ।
ঋত্বিক ঘটকের শৈশবের একটা বড় সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। তিনি রাজশাহীর কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৪৬ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের প্রচুর লোক কলকাতায় আশ্রয় নেয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর পরিবারও কলকাতায় চলে যায়। তবে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে শরনার্থী হবার মর্মবেদনা ঋত্বিক কোনোদিন ভুলতে পারেননি এবং তাঁর জীবন-দর্শন নির্মাণে এই ঘটনা ছিল সবচেয়ে বড় প্রভাবক যা পরবর্তীকালে তার সৃষ্টির মধ্যে বারংবার ফুটে ওঠে। কলকাতায় ঋত্বিক ঘটক ১৯৪৮ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম এ কোর্সে ভর্তি হন। এরই মাঝে নাটকের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে নাটকের নেশাতেই এম.এ কোর্স শেষ করেও পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন তিনি।
ছাত্র অবস্থাতেই লেখালেখির সাথে যুক্ত ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৮ সালে ঋত্বিক ঘটক লেখেন তাঁর প্রথম নাটক কালো সায়র। একই বছর তিনি নবান্ন নামক পুণর্জাগরণমূলক নাটকে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে (আইপিটিএ) যোগদান করেন। এসময় তিনি নাটক লেখেন, পরিচালনা করেন ও অভিনয় করেন এবং বের্টোল্ট ব্রেশ্ট ও নিকোলাই গোগোল-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করেন।
ঋত্বিক ঘটক ১৯৫১ সালে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' সিনেমার মধ্য দিয়ে; তিনি এই ছবিতে একই সাথে অভিনয় এবং বিমল রায়ের সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। এর দু'বছর পর ১৯৫৩ সালেতাঁর একক পরিচালনায় প্রথম ছবি 'নাগরিক'। দু'টি চলচ্চিত্রই ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারাকে জোর ঝাঁকুনি দিতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের পরে শরণার্থীদের অস্তিত্বের সংকট তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর চলচ্চিত্রে এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অযান্ত্রিক মুক্তির সাথে সাথেই তিনি শক্তিশালী চলচ্চিত্রকার, হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এরপর একে একে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র- 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণ রেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'।
ঋত্বিক ঘটক নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে 'মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)', 'কোমল গান্ধার (১৯৬১)' এবং 'সুবর্ণরেখা (১৯৬২)' আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়। এই তিনটি চলচ্চিত্রকে ট্রিলজি বা ত্রয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন অবস্থা এবং উদ্বাস্তু জীবনের রুঢ় বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে। তবে 'কোমল গান্ধার 'এবং 'সুবর্ণরেখা'র ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে ষাটের দশকে আর কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
মানবতাবাদী শিল্পী ঋত্বিক ঘটক সবসময় স্বপ্ন দেখতেন ও দেখাতেন এমন এক সমাজ ব্যবস্থার যেখানে শোষক ও শোষিত সম্পর্ক থাকবে না, শ্রেণী বিভাজন থাকবে না, সাম্প্রদায়িকতা, কাড়াকাড়ি, সাংস্কৃতিহীনতা থাকবে না। তাইতো মানবতার টানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাকে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়।
প্রায় এক যুগ বিরতির পর চলচ্চিত্রে ১৯৭২ সালে ফের আবির্ভাব হয় ঋত্বিক ঘটকের। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করেন তিনি। ১৯৭৩ সালে সালে ছবিটি মুক্তি পায়। এ ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের কারণে আলোচিত হন বাংলাদেশের শক্তিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র। ছবিটিতে কবরীও অভিনয় করেছিলেন।

এরপর ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তিতক্ক আর গপ্পো'। কাহিনীর ছলে তিনি নিজের কথা বলে গেছেন এ ছবিতে। ছবিটিতে নিজের রাজনৈতিক মতবাদকেও দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। কে জানতো এটাই এই ক্ষণজন্মা নির্মাতার শেষ ছবি!
ওই সময় থেকেই খারাপ স্বাস্থ্য এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়া ঋত্বিক ঘটকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর সমালোচকরা বলে থাকেন ঋত্বিক সিনেমার নেশায় কি পড়বে? বাংলা মদ আর বিড়ির ধোঁয়ার নেশায়ই তো বুঁদ হয়ে আছে। তবে তার সিনেমাকে বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন সমালোচকরা। চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৫ সালে যুক্তি তক্কো আর গপ্পো চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্য ভারতের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।
শিল্পের প্রতি সততা বজায় রাখতে গিয়েই হতাশার চোরবালিতে পা ডোবান ঋত্বিক ঘটক। সুবর্ণরেখা সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন তার হাতে কোনো ছবি ছিলো না। নিজের প্রতি অত্যাচারের জেদ ঐ সময় থেকেই। মদ তখন তার ব্যর্থতা ভোলার অনুষঙ্গ।
আগেও একাধিকবার স্বল্প সময়ের জন্য মানসিক ভারসাম্যও হারানো ঋত্বিক ঘটক পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন শেষ ছবি 'যুক্তিতক্ক আর গপ্পো'র পর। চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয় মানসিক হাসপাতালে। স্মৃতি হারানো ঋত্বিক পরিবার-পরিজন আর শুভাকাঙ্খিদের চিনতে পারতেন। জটিল সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়াই মাঝেমধ্যেই মারমুখি হয়ে উঠতে থাকনে। জীবনের শেষ দিনগুলো তাকে কাটাতে হয়েছে হাসপাতালের নির্জন প্রকোষ্ঠে। সীমাহীন অসহায়ত্বের মাঝে ১৯৭৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫০ বছর বয়সে মেধাবী এ নির্মাতা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।
ঋত্বিক যে মানের নির্মাতা ছিল তাঁর যোগ্য সন্মান সে সময় তিনি পায়নি,তাই তো তাঁর সময়ের অনেক বাজে নির্মাতাও তাঁর থেকে বেশি পদক পেয়ছে।কিন্তু ঋত্বিকরা যুগে যুগে একবারই জন্মায় এবং তাঁরা পদক পাবার জন্য কাজ করে না,তাঁরা নিজের মনের তাগিদে,সমাজের তাগিদে কাজ করে যায়। কাজের মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের প্রমান করেন এবং মৃত্যুর পরেও কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকেন।
ঋত্বিক ঘটক নির্মিত চলচ্চিত্র
নাগরিক (১৯৫২) (মুক্তিঃ ১৯৭৭, ২০শে সেপ্টেম্বর)
অযান্ত্রিক (১৯৫৭)
বাড়ি থেকে পালিয়ে (১৯৫৮)
মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০)
কোমল গান্ধার (১৯৬১)
সুবর্ণরেখা (১৯৬১)
তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩)
যুক্তি তক্কো গপ্পো (১৯৭৪)
ঋত্বিকের চিত্রনাট্য:
মুসাফির (১৯৫৭)
মধুমতী (১৯৫৮)
স্বরলিপি (১৯৬০)
কুমারী মন (১৯৬২)
দ্বিপের নাম টিয়া রঙ (১৯৬৩)
রাজকন্যা (১৯৬৫)
অভিনেতা হিসেবে কাজ করা চলচ্চিত্র সমূহ:
তথাপি (১৯৫০)
ছিন্নমূল (১৯৫১)
কুমারী মন (১৯৬২)
সুবর্ন-রেখা (১৯৬২)
তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩)
যুক্তি,তক্কো,আর গপ্পো (১৯৭৪)
ডকুমেন্টারি:
আদিবাসীওন কা জীবন স্রোত (১৯৫৫) (হিন্দি)
বিহার কে দর্শনীয়া স্থান (১৯৫৫) (হিন্দি)
সায়েন্টিস অফ টুমরো (১৯৬৭)
ইয়ে কৌন (১৯৭০) (হিন্দি)
আমার লেলিন (১৯৭০)
পুরুলিয়ার ছাউ (১০৭০)
শর্ট ফিল্ম:
ফিয়ার (১৯৬৫) (হিন্দি)
রেন্ডিজভোয়াস (১৯৬৫) (হিন্দি)
সিভিল ডিফেন্স (১৯৬৫)
দুর্বার গতি পদ্মা (১৯৭১)
মঞ্চ নাটক:
চন্দ্রগুপ্ত (অভিনেতা)
অচলায়তন (নির্দেশক ও অভিনেতা)
কালো সায়র (নির্দেশক ও অভিনেতা)
কলঙ্ক (অভিনেতা)
দলিল (নির্দেশক ও অভিনেতা)
কত ধানে কত চাল (নির্দেশক ও অভিনেতা)
অফিসার (অভিনেতা)
ইস্পাত (মঞ্চে প্রদর্শিত হয়নি)
গ্যালিলিও চরিত
জাগরণ (অভিনেতা)
জলন্ত (রচনা)
জ্বালা (রচনা)
ডাকঘর (নির্দেশনা)
ঢেউ (নির্দেশনা)
ডেকি সর্গে গেলেও ধান বানে (রচনা)
নবান্ন (নির্দেশনা)
নিলদর্পন (অভিনেতা)
নিচের মহল (মঞ্চে প্রদর্শিত হয়নি)
পরিত্রাণ (অভিনয়)
ফাল্গুনি (অভিনয়)
বিদ্যাসাগর (নির্দেশনা)
বিসর্জন (নির্দেশনা)
ম্যাকবেথ (অভিনেতা)
রাজা (নির্দেশনা)
সাঁকো (অভিনেতা)
সেই মেয়ে (নির্দেশনা)
হযবরল (নির্দেশনা)
ঋত্বিকের অসমাপ্ত কাজ
ফিচার:
অরূপকথা/বেদেনী (১৯৫০-৫৩)
কত অজানারে (১৯৫৯)
বগলার বাংলাদর্শন (১৯৬৪)
রঙের গোলাম (১৯৬৮)
ডকুমেন্টারি:
উস্তাদ আলাউদ্দিন খান (১৯৬৩)
ইন্দিরা গান্ধী (১৯৭২)
রামকিঙ্করঃ এ পারসোনালিটি স্টাডি (১৯৭৫)
©somewhere in net ltd.
১| ০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সন্ধ্যা ৬:৫৭
০৬ ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সন্ধ্যা ৬:৫৭
আরণ্যক রাখাল বলেছেন: ভাল জিনিস বেশি লাগেনা| ঋত্বিক তার প্রমাণ| অনেক তথ্যবহুল পোস্ট| জানলাম অনেক কিছু| ধন্যবাদ