| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
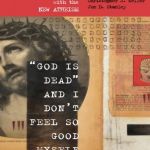 Titanic
Titanic
এক সময় আমরা সবাই মানুষ ছিলাম।হঠাৎ করে তখন এক ভণ্ডু খোদার আবিষ্কার হল।শুরু হয়ে গেলে ধর্মের/খোদার দলের দালালী(মানুষের মধ্যে মারামারি হানাহানি)ভণ্ডু খোদার এক বিশেষ দালাল হল ইসলামধর্মের নবী মুহাম্মদ।ধর্মিয় বই নাকি আসমান থেকে এসেছ,আরে বোকার দল তাহলে তদের মালিককে বল আমাকে একটি আইটির বিশেষ বই দিতে।আমি আইটির ব্যবহার ও উন্নত মান দিয়ে তোদের খোদা হওয়ার দাবী করব।তোমরা বল কোরান,বাইবেল, গীতা আরও কত্তকিছু উপর হতে এসেছে।তোমরা কি দেখনা এখন মানুষ উপর(চন্দ্র,মংগল ইত্যাদিতে ভ্রমণ করছে)চোখ খুল মানুষ, চোখ খুল।
সামাজিক/সমষ্টিগত জীবনে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের অপরিহার্যতা এখন প্রায় সর্বত্র’ই স্বীকৃত। ‘আধুনিকতা’ বলতে যে ধ্যান-ধারনা বোঝায় তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিক গণতন্ত্র, এবং এই উপলব্ধি, যে গণতন্ত্রের সফলতা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ধর্মের হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার ওপর নির্ভর করে। মধ্যযুগে, সামন্ততন্ত্রের গোধূলি পর্যায়ে এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাধান্য স্থাপনের শুরুতে বিশাল কলকারখানা ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন করার প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় অগণিত ভূমিহীন উদ্বাস্তু কৃষক ও খেত মজুরকে কর্মসংস্থানের খোঁজে শহরে আসতে বাধ্য করা। সামন্ততন্ত্রের শিকল মুক্ত নব্য পুঁজিপতি শ্রনী রাষ্ট্র পরিচালন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ গ্রহণের দাবী তোলে।স্বাধীন শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হতে থাকে । শহর অঞ্চলে জন সংখ্যা বাড়তে থাকে, এবং তার ফলে ধর্ম, জাতী, শ্রেণী, নারী-পুরুষ, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিশিষ্টতায় বিভাজ্য মিশ্রিত নাগরিকের সংখ্য বাড়তে শুরু করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন শ্রমিকের অবারিত চালান । ভূমির মালিকানা সংশ্লিষ্ট আইনকানুনের অপব্যবহার করে অথবা জোর-জবরদস্তি করে অগণিত ছোট কৃষক এং কৃষি-শ্রমিক ভূমিচ্যূত করা হয়। নিজের শ্রম-শক্তি ছাড়া অন্য আয় অর্জনে ব্যবহার্য্য অন্য কোন সম্পদ হীন এই জনগণ’ই আধুনিক শ্রমিক শ্রনির অগ্রজ । সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকল মুক্ত মিশ্রিত-নাগরিক সমৃদ্ধ সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়। ইয়োরোপে ষোল-সতের শতাব্দীর সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততন্ত্রের সর্বশেষ সেকল ছিন্ন করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য স্থাপন বিঘ্নহীন করা । ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্রীক শোষণ ও বিধিনিষেধ বলবৎ করণে এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শে’র সম্প্রসার ও রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে সে আধিপত্যের অবসানের প্রয়োজনে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আবশ্যকীয় লক্ষ ও অনিবার্য পরিণতি । গনতন্ত্রেরতার সাফল্যের জন্যই রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় প্রভবের উৎখাত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । পরবর্তীকালে ব্যাপক শিল্পায়ন, আধুনিক শ্রমিক শ্রনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিশ্বযুধ্ব, ইত্যাদির চাপে সমাজ ও সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় সনাতনী ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ দ্রুত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় । বলা বাহুল্য, ফলে ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায় নি; বরং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে তার উপযোগী ভূমিকা যথারীতি প্রচলিত থেকেছে ।
তবে বিশ্বাসীদের সংখ্যার নিম্নগামী প্রবণতা উপেক্ষা করা সম্ভব নয় । (গ্রাফ দেখুন; Source: Click This Link) । ধর্ম বিশ্বাসে এই অবনতি অংশত আজকের প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ ব্যবহারিক জীবনে বিশ্বাস-নির্ভর যুক্তিহীন ধ্যনধারনার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফল এবং প্রায় সমস্ত পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবশ্যকতা বৃদ্ধির এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের ফল, সেটা ও অনস্বীকার্য। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, বিশাল বিস্ফোরণে (big bang) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট, জীবাশ্ম-জ্বালানীর ক্রম বর্ধমান ব্যাবহারের সঙ্গে বিশ্ব-আবহাওয়ার ভীতিকর পরিবর্তনের সম্পর্ক, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় (concepts) জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত । তদুপরি, প্রায় সারা পৃথিবীতে স্বল্প সংখ্যক নীতি জ্ঞানহীন সুবিধাবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনজীবনে ধর্ম রাজনীতির ও রাজনৈতিক ধর্মের অপব্যবহার ও তার ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া’ও অবিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে বলে মনে হয়।
ধর্ম সংশ্লিষ্ট এই প্রপঞ্চের প্রসারের এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবিশ্বাসীদের সংখ্যা যে ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে, তার পরিসংখ্যনতত্ব সমর্থিত নিদর্শন প্রজ্ঞাপিত (publicized) হওয়ার ফলে বিশ্বাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হবে, সেটা স্বাভাবিক। এমনকি সুদূর ঢাকা শহরের প্রজন্ম চত্বরের বিপ্লবীদের মধ্যে’ও নাস্তিকদের সংখ্যাধিপত্য নিয়ে বাংলাদেশে মুসলমান ধর্মের বিশুধ্বতার স্বনিযুক্ত রক্ষক জামাত-ই-ইসলামের নেত্রীবৃন্দ উদ্বিগ্ন । অন্যদিকে উৎস-ধর্ম নির্বিশেষে ধার্মীকদের নাস্তিকে রূপান্তরের দ্রুত বৃদ্ধিতে কিছু সমস্যা (!) ও দেখা দিয়েছে। লন্ডনে অভিষিক্ত প্রথম নাস্তিক ‘মন্দিরে’ অত্যধিক ভিড়ের ফলে অনেককে ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে ! এই সমাবেশের জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে সন্দেহ অভিমত অবশ্য ভিন্ন ।
Untitled
প্রতিবেদনে অনুযায়ী, এই মন্দিরের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা এবং অনুষ্ঠান শেষে খাঁটি বিলেতি কায়দায় (বিনামূল্যে) চা বিতরণ, ইত্যাদি ! নাস্তিক মন্দিরে ভিড়ের সেটা একটা কারণ হতে পারে, তা অস্বীকার করা মুশকিল ।
নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীদের প্রধান অভিযোগ – নাকি সন্দেহ ? – যে তারা নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান হীন, স্বেচ্ছাচারী, লম্পট, ব্যাভচারী; তাদের ব্যবহার কোনরকম নিয়ন্ত্রণে সীমিত নয়, ইত্যাদি । যারা দৈনন্দিন জীবনে পাপ-পুণ্যের বিবেচনায় অসংকুচিত, পরলোকে ইহলোকের অপকর্মের পরিণতিতে যারা ভীত নয়, তাদের পাপকর্মে কোন বাধা নেই, ফলে তারা দায়িত্বজ্ঞান হীন হবে, সেটা অনিবার্য । যেহেতু ধর্ম আমাদের নেতিবাচক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালনে সুদীর্ঘকাল যাবত নিয়োজিত, অনেকরই ধারনা যে নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান ধর্ম-উদ্ভূত । বলা বাহুল্য, এই ধারার মতবাদের পেছনে রয়েছে একটা মৌলিক ত্রুটি-গ্রস্ত (পূর্ব) ধারনা, যে ধর্ম ব্যতীত নৈতিকতা ও ন্যায় জ্ঞান সম্ভব নয় । মানুষের ‘সাধারণ প্রবৃত্তি’ স্বার্থপরতা ও লোভ-প্ররোচিত ব্যবহার, এবং তার সংযমের জন্য ধর্ম আবশ্যকীয় – এই ভাববাদী ভিত্তিক ধারনাও জনপ্রিয়। বস্তুত, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনঐতিহাসিক। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী অথবা অনিশ্চিত-মনা, অপকর্মে কারো’ই একাধিপত্য নেই।
শিরোনামার তিনটি বাংলা পরিভাষা নিন্মের তিনিটি ইংরেজি শব্দের পরিভাষার বাচ্যার্থ বলে ধরে নেয়া হয়েছে : নৈতিকতা, নীতিতত্ব – Ethics; ন্যায়জ্ঞান, (ব্যক্তিগত) নৈতিকতা; – Morality; এবং, ধর্ম – Religion. উপরোক্ত বাংলা পরিভাষা ইংরেজি শব্দগুলোর অর্থ সূক্ষ্ম ও সঠিক ভাবে ব্যক্ত করে কিনা সে বিষয় সংশয় আছে বলে এই আলোচনায় কোথাও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলে ইংরেজিতে ব্যক্ত উপলব্ধির ওপর নির্ভর করা হবে । আর এটাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান এর মধ্যে পার্থক্য ব্যখ্যা করা সহজ নয়। তবে নৈতিকতা সাধারনতঃ সমাজ বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এবং ন্যায়জ্ঞান ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেয়া যায়। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুধ্বে কৃষ্ণ কোন পক্ষকে তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শে উপকৃত হতে সক্ষম করেছিলেন সেটা তাঁর নৈতিকতার অভিব্যক্তি । ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আপন সন্তানদের সমর্থন’ও ছিল সঠিক ন্যায়জ্ঞানের প্রয়োগ ।বৈদিক ঐতিহ্যে ধর্ম শুধু আচার অনুষ্ঠানে সীমাবধ্ব নয়, এর বৃহত্তর অর্থ ‘কর্তব্য’, সে কারণে সনাতনী অর্থে ধর্মপালন, নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান, সবই কর্তব্য পালনে সার্থকতার জন্য আবশ্যক ।
নৈতিকতা, ন্যায়জ্ঞান ও ধর্ম – এই তিন প্রত্যয়ের সম্পর্ক দর্শনের বিবেচ্য বিষয় । সেই দুর্বোধ্য বিতর্কের বিশাল সমুদ্রে অবগাহনের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি এবং নৈপুণ্যের অভাবে উপরুক্ত তিন বিষয়ের সম্পর্কের দার্শনিক বিবেচনা এড়িয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হবে । আমাদের প্রাগ-ইতিহাস বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার ফলে এ’বিষয়ে আমরা মোটা মোটই নিশ্চিত যে এক দিকে জৈবিক বিবর্তনের ক্রমবিকাশ’ই মানুষ কে যেমন ‘সামাজিক’ প্রজাতিতে পরিণত করেছে, সামাজিক জীবন’ই আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশে ইন্ধন যুগিয়েছে । বেঁচে থাকার তাগিদে – খাদ্য সংগ্রহের জন্য, হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য – অর্থাৎ প্রাণ রক্ষার জন্য’ই হোক কিম্বা আনন্দ-উৎসব উপভোগ করার জন্যই হোক, প্রায় সব কাজে (বৃহৎ অর্থে) আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল; এটা প্রাণী জগতে ‘মানুষ’ প্রত্যয়’এর নির্ধারক । তবে সমাজ ভিত্তিক জীবনধারণের অবিসম্ভাবি পরিণতি ছিল দ্বন্দ্বের আবির্ভাব, সম্ভবত: যার শুরু খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে। নির্ভরতা ও ব্যক্তি স্বতন্ত্রতার সহবস্থান মানব-অস্তিত্বের অংশবিশেষ । সমষ্টিগত ব্যবস্থা রক্ষার জন্য এই দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রয়োজনেই ক্রমশ সীমাবদ্ধতার সচেতনতার অবির্ভাব হয়। এবং তা সামাজিক আচার ব্যবহারে অন্তর্ভুক্ত হয় সমষ্টি’র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী । সম্ভবত: এই সীমাবদ্ধতার উপলব্ধির ফলেই মানব সমাজে নীতিজ্ঞান ও নৈতিকতার অবির্ভাব ।
মোদ্দা-কথা, নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞানের উৎপত্তি মানব প্রজাতির আবির্ভাবের সমকালীন, তা আমাদের জৈবিক প্রক্রিয়া বিবর্তনর আঙ্গিক । এর পদ্ধতি অনুযায়ী যা প্রয়োজন শুধু তাই রক্ষিত থাকে । অন্য সব, যা অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর , মেয়াদ-অতিক্রান্ত, তা পরিত্যক্ত হয় । আমাদের বিবর্তনের আদি-ইতিহাস দীর্ঘ, এবং এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি দুর্লভ জীবাশ্ম (fossil) ভিত্তিক । নৈতিকতা, ন্যায়জ্ঞান ও ধর্মের ভিত্তি যদিও আধিভৌতিক, জীবাশ্মে তাদের অস্তিত্ব খোঁজা অর্থহীন । শুধু ভাষা আবিষ্কার ও আখ্যান সৃষ্টিতে দক্ষতা অর্জনের পর কোন কোন আখ্যান আমাদের পূর্বসূরিদের নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান নিয়ে জল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । স্যার চার্লস ডারউন তাঁর Descent of Man গ্রন্থে আমাদের জৈবিক-সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে ন্যায়-নীতি বোধের আবির্ভাব ও বিকাশের সম্পৃক্ততা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এ বিষয়ে সমকালেও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে । উৎসাহী পাঠক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এডওয়ার্ড উইলসনের লেখা পড়ে দেখতে পারেন ।
নৈতিকতা ও ন্যয়জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষ-প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, ধর্ম আবিষ্কারের এবং তার প্রয়োজনের অনুভবের অনেক আগে । নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞানের অনুপস্থিতি তে মানুষ-প্রজাতি বিবর্তনের সুদীর্ঘ যাত্রায় সফল হত কি না তা সন্দেহ জনক । সেই প্রয়োজনের কারণেই নৈতিকতা ও ন্যায়জ্ঞান ধর্ম-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অসংশয়ে বলা যায় যে সামাজিক জীবনে বিশ্বাসের প্রভাব কমতেই থাকবে । তবে তার পরিণাম সামাজিক অরাজকতা, এমনকি সভ্যতার বিলুপ্তি – বিশ্বাসীদের এই ভীতির কোন যৌক্তিকতা নেই। ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব প্রশমিত হবার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজে নৈতিকতা ও ন্যয়জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বাড়বে, তা নিশ্চিত। আর ধর্মের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কার্ল মার্কসের নিরীক্ষা’ই প্রযোজ্য। তাঁর প্রায়শ উদ্ধৃত মন্তব্য “ধর্ম জনগণের আফিং” অনেকেরই অবগত আছেন। কিন্তু পরবর্তী নিরীক্ষণ, যেটা সাধারণত উদ্ধৃত হয়না, অথচ যার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, তা হল “এই হৃদয়হীন পৃথিবীতে কেবল ধর্ম’ই হৃদয়-সম্পন্ন”। তাই যদ্দিন হৃদয়হীন শোষণ, অত্যাচার ও অবিচার চলবে, ততদিন অনেক অসহায় মানুষ হৃদয়ের খোঁজে ধর্মাশ্রীত’ই থাকবে ।
©somewhere in net ltd.