| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
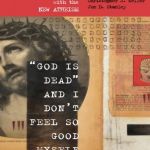 Titanic
Titanic
এক সময় আমরা সবাই মানুষ ছিলাম।হঠাৎ করে তখন এক ভণ্ডু খোদার আবিষ্কার হল।শুরু হয়ে গেলে ধর্মের/খোদার দলের দালালী(মানুষের মধ্যে মারামারি হানাহানি)ভণ্ডু খোদার এক বিশেষ দালাল হল ইসলামধর্মের নবী মুহাম্মদ।ধর্মিয় বই নাকি আসমান থেকে এসেছ,আরে বোকার দল তাহলে তদের মালিককে বল আমাকে একটি আইটির বিশেষ বই দিতে।আমি আইটির ব্যবহার ও উন্নত মান দিয়ে তোদের খোদা হওয়ার দাবী করব।তোমরা বল কোরান,বাইবেল, গীতা আরও কত্তকিছু উপর হতে এসেছে।তোমরা কি দেখনা এখন মানুষ উপর(চন্দ্র,মংগল ইত্যাদিতে ভ্রমণ করছে)চোখ খুল মানুষ, চোখ খুল।
প্রাচীন মানুষ ঝড় বন্যা বা কঠিন অসুখ-বিসুখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ত। তখন মানুষের গড় আয়ু ছিল আঠার বছর। অকাল মৃত্যুর কারণ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হতে হত তাদের। অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে তাদের তখনো কোন ধারণা গড়ে উঠা দূরে থাক, তাদের জীব জগৎ সম্পর্কেও কোন স্পষ্ট ধারণা তখন গড়ে উঠেনি। তখনকার মানুষের জীবন যাত্রা তো আর এখনকার মত ছিলনা। তখন তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ত। ঝড় বন্যা বৃষ্টি বজ্রপাত আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আর অন্য সব প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ তারা বুঝতো না। বলা হচ্ছে ‘হোমো স্যাপিয়েনস’ মানুষদের কথা, যারা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন।
নিজেদের চারদিকে ঘিরে থাকা প্রকৃতিকে ‘হোমো স্যাপিয়েনস’ মানুষ ঠিক সেই রকমই ভয় পেতো, যেমন ভয় পেতো তারও বহু পূর্বে পৃথিবীর আদিম মানুষেরা। এমন মানুষ আজও আছে পৃথিবীতে কোথাও কোথাও আছে, যারা এখনো অনুসরণ করে প্রাচীন মানুষের জীবন যাত্রার ধরণ। আদিম মানুষের সাথে ‘হোমো স্যাপিয়েনস’ মানুষের তফাৎ হল, হোমো স্যাপিয়েনসরা প্রকৃতির ক্ষমতা জানতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক রহস্যের কার্য-কারণ সম্পর্ক তারা বুঝতো না বলে, প্রাকৃতিক ঘটনাকে তারা ব্যাখ্যা করতো, তাদের তখনকার অর্জিত ধারণা অনুসারেই, নিজেদের মত করে, নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি আর বিবেচনা অনুসারে।
তারা তাদের তৎকালীন পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে, নানা রকমের যুক্তি খাড়া করতে শুরু করেছিল এক সময়ে। তারা ঐ সময়ে ধরে নিয়েছিল, ওই সব ঘটনা ঘটছে, তাদের অজ্ঞাত কোন গুপ্ত অলৌকিক শক্তির ফলে। তখন তারা চেষ্টা করতে লাগল, কিভাবে এই সমস্ত গুপ্ত অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তা নিজেদের উপকারে কাজে লাগানো যায়।
এই ধরণের ধারণার অনুসারি হয়েই, শিকারে যাওয়ার আগে, তারা পশুর ছবি মাটিতে আঁকত এবং সেই ছবিকে হত্যা করেই শিকারে যেত। তারা মনে করত যে, এভাবে কাঙ্খিত শিকারকে সহজেই কাবু করতে পারবে। দলবদ্ধ হয়ে এই কাজ করতে করতে, ধীরে ধীরে তা প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। যে কোন সমাজে, কোন প্রথা সৃষ্টির পেছনে প্রতিটি জনসমষ্টির মধ্যে অবস্থানকারী সকলের সম্মিলিত প্রায়াস কার্যকরী থাকে। আর সুদূর অতীতে, বেঁচে থাকার এবং জীবনযাত্রা আরো উন্নত করার সামাজিক তাগিদ তথা প্রয়োজনীয়তা থেকেই, নানা রকমের প্রথার উদ্ভব হয়েছে। খাদ্য আহরণের যৌথ প্রয়াস মানুষকে এসব করতে বাধ্য করেছে। আর সেই প্রচেষ্ঠারই ফলশ্রুতি হচ্ছে স্ব স্ব জনগোষ্ঠির নিজস্ব প্রথা। এমনও দেখা গেছে, এক একটা পরিবারে তাদের নিজস্ব প্রথা প্রচলিত ছিলো। এসবের চিহ্ন এখনো বিশ্বময়, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এমন যৌথ শিকার ব্যবস্থা প্রতিটি জনগোষ্ঠিতেই, কোন না কোন সময়ে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক তথা ভৌগোলিক তারতম্যের কারণে, বিভিন্ন সময়ে এসবের আলাদা আলাদা অর্থাৎ স্বকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পর্যায়ে তারা মনে করত যাদু করে তাদের প্রয়োজনীয় পশুর উপর সম্মোহন প্রভাব বিস্তার করলেই পশুকে পরাস্ত করতে পারবে।
আমাদের মত তারাও ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখত। স্বপ্ন দেখত হয়ত এমন সব লোকজনকে, যারা তাদের থেকে দূরে কোথাও রয়েছে। অথবা এমন কাউকে দেখত, যে মারা গেছে। ঘুম এবং স্বপ্নের কারণ না জানা থাকায়, তারা যুক্তি খাঁড়া করে কল্পনা করেছিল যে, দেহের ভিতরে থাকে আত্মা। ঘুমের সময় সেই আত্মা বেড়িয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই আত্মাগুলো অন্যদের আত্মার সাথে যোগাযোগ করে, দেখা সাক্ষাৎ হয় ইত্যাদি। আর ভাবত, কেউ মারা গেলে, তার আত্মা তার দেহ ছেড়ে বেড়িয়ে যায় এবং ঘুরে বেড়ায়।
প্রাচীন মানুষ মনে করত মানুষের যেমন আত্মা আছে, ঠিক তেমনি সমস্ত জীবজন্তু পশুপাখী গাছপালারও আত্মা আছে। তারা ভাবত প্রকৃতিতে আত্মা নামে এক অলৌকিক সত্তা ছড়িয়ে দেয়া আছে, তাই সমস্ত কিছুতেই আত্মা থাকে। তবে তারা এটাও ভাবত যে, আত্মা দুই ধরণের। একটা ভাল, আরেকটা মন্দ। তখনকার মানুষেরা মনে করতে শুরু করেছিল যে, শিকারের সময়, ভাল বা মন্দ আত্মাই শিকারের ভাল মন্দ স্থির করে। আবার মানুষকে রোগাক্রান্তও করে, সেই মন্দ আত্মারাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের নামটি এসেছে এই ধারণা থেকেই। মনে করা হয়েছিল, মন্দ আত্মা আর গ্রহ নক্ষত্রের কু প্রভাব তথা influence থেকেই এই রোগ সৃষ্টি হয়।
এই ধরনের কাল্পনিক ধারণা থেকেই মানব সমাজে চালু হয়েছিল রোগীকে ঘিরে নানা রকমের অদ্ভুত কাজকর্ম। কোথাও রোগীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে চিৎকার করত। কোথাও লাঠিসোটা নিয়ে রোগীকে ভয় দেখাতো। কোথাও বা ধোঁয়া দিয়ে একাকার করে ফেলত। অনেক সময় চেঁচামেচি করত। এই ভাবেই ঝাড়ফুঁকের সৃষ্টি হয়েছে, যা এখনো সমাজে বিদ্যমান। সৃষ্টি হয়েছে নানা রকমের আচার আচরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদির।
বেঁচে থাকার ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য মানুষের যা দরকার হয়, তার কোনোটাই প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় থাকে না। আদিম মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে পশু শিকার করেছে, মাছ ধরেছে, ফলমূল আহরণ করেছে, খাদ্য ও পরিধেয় তৈরি করেছে। যুগ যুগ ধরে খাদ্য, পরিধেয়, আবাস, ওষুধ, আনন্দসামগ্রী ইত্যাদি সবকিছু তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রয়াসে উৎপাদন করতে হচ্ছে। উৎপাদনের জন্য চিরকাল মানুষ তার চিন্তাশক্তি এবং শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে মানুষকে প্রকৃতির নানা উপাদান নিয়ে চিরকাল কাজ করতে হয়েছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। এই উৎপাদন কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার তাগিদেই, মানুষ সর্বদা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে উপলব্ধি করতে লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে চলেছে।
মানুষ যা জানে তাই তার জ্ঞান। জানা ও করার প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। পূর্ববর্তী জেনারেশন পরবর্তী জেনারেশনকে জানিয়ে যায় তার অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা। আর পরবর্তী জেনারেশন পূর্ববর্তী জেনারেশন থেকে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা। চিন্তার মধ্য দিয়ে যুক্ত করে তার নিজের নতুন অর্জিত জ্ঞান। এইভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে চলছে মানবজাতির সার্বিক জ্ঞানভান্ডার।
শিকার, পশুপালন ও কৃষি জীবন ভিত্তিক সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে, জীবিকা এবং জীবন সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত কঠোর ও শ্রম সাপেক্ষ। তথাপি জীবিকা ও জীবনযাত্রা সংক্রান্ত শিক্ষা মোটেই জটিল ছিল না। কৃষির উন্নতির পর্যায়ে, কিছু লোক কঠোর শারীরিক শ্রম থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হয়। তারা চিন্তামূলক ও ব্যবস্থাপনামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে শুরু করে। ঠিক তখনই সমাজ বিভক্ত হয়ে যায় শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীতে।
ঠিক তখনই মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাসও। প্রকৃতির যেসব জিনিসের উপর তখন তাদের জীবন নির্ভরশীল ছিল, সেইসবের অনুমান নির্ভর “আত্মা” তাদের কাছে অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দেয়। যেমন, সূর্যের আত্মার তাপে ফসল পাকে, মেঘের আত্মার বারিধারায় জমি আর্দ্র হয়, শস্যবীজের আত্মা মাটি বুকে ফসল ফলিয়ে তোলে ইত্যাদি। আদিম মানুষ প্রকৃতির ক্ষমতাকে জানার চেষ্টা করেছিল। প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ সম্পর্ক তারা বুঝতে না পারায়, তারা সেইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতো নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে। তারা ব্যাখ্যা করতো, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ঘটছে তাদের অজ্ঞাত কোন গুপ্ত অলৌকিক শক্তির ফলে। ঐ সময়েই আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে এই ধারণার সৃষ্টিও হয় যে, “আত্মা” নিশ্চয়ই বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতাদের দান, যাদের ইচ্ছায় পৃথিবীতে বসন্ত আসে, বৃষ্টি পড়ে, ফসল ফলে। তারা আরো ভাবতো যে, এই দেবতারা মানুষ বা পশুর রূপ ধারণ করেই বিরাজ করে। এই ধারণার বশবর্তি হয়েই তারা তাদের কল্পনার দেবতাদের আদলে ছবি আঁকতে ও মূর্তি বানাতে শুরু করে। ডালপালা, কাঠ বা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে কাল্পনিক দেবতা বানাতো। বিভিন্ন উপযোগী স্থানে, যেমন গুহার গায়ে, বড় গাছে, খোদাই করে দেবতার প্রতিমূর্তি গড়ত। এইসব কল্পিত দেবতাদের ভয়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে থাকত। কালক্রমে তারা এইসব কল্পিত দেবতাদের কাছে, করুণা ভিক্ষা করতে শুরু করে। করুণা আদায়ের উদ্যেশ্যে তারা কল্পিত দেবতার ছবি ও মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণত হতে লাগলো। দেবতাদের মূর্তির সামনে বিভিন্ন ধরণের উপহার সামগ্রী দিয়ে যেত, তুষ্ট করার জন্যে। এই উপহার সামগ্রিকে আমরা অনেকেই বলে থাকি নৈবদ্য। সমস্ত ধরণের ফলমূল থেকে শুরু করে পশু-পাখীও হয়ে উঠলো এই নৈবদ্য। এত করেও যখন কিছু কিছু বিপদ থেকে রেহাই মিলছিলো না, তখনই এই নৈবদ্যে মানুষও যুক্ত হয়ে গেলো। পশু-পাখি আর মানুষকে হত্যা করেই তাদের দেবতাকে নৈবদ্য দেয়া চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে, বলি প্রথা সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছিল। তখন বলির সময়ে সজোরে শব্দ করার রেওয়াজ চালু হয়। এই ভাবেই সমাজে ধর্ম বিশ্বাসের গোড়াপত্তন ঘটে। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় রিলিজিয়ন।
এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অতীত কালের অতশত, এখনকার মানুষ জানলো কিভাবে। এখন সেদিকেই একটু আলোকপাত করা যাক। প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন সমাধি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, আদিম মানুষ তাদের সমাধিতে খাদ্যদ্রব্য, সাংসারিক প্রয়োজনের উপকরণ, গয়নাগাটি ইত্যাদি দিয়ে রাখতো। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, প্রাচীন মানুষ ভাবত মৃতের আত্মা আবার মৃতদেহে ফিরে আসতে পারে। যদি ফিরে আসে, তাহলে জীবিত মানুষের যা যা প্রয়োজন, মৃত মানুষেরও সেইসব প্রয়োজন হবে। এইসব আদি কালের ধ্যান-ধারণা সমাজে এখনো রয়ে গেছে। ধার্মিক মানুষ আজও মৃত মানুষের উদ্দেশ্যে পিন্ড দান করে। শ্রাদ্ধ কালে সাংসারিক প্রয়োজনের উপকরণ, কাপড়চোপড় এমনকি লেপ তোষকও নিবেদন করে।
প্রাচীন সমাজে ধারণা করা হত বিশ্ব সনাতন। পৃথিবী কিভাবে, কবে, সৃষ্টি হয়েছে তা তারা জানত না। এর আদি নেই অন্তও নেই, বলেই মনে করা হত। প্রাণীর সৃষ্টির রহস্য তারা জানত না। তারা মনে করত, একটা আত্মা একটা দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই মৃত্যু। এই ধারণা সমাজের অনেকেই এখনো বিশ্বাস করে। বিশ্বাস হচ্ছে একধনের ধারণা, যা অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, কিন্তু তার বাস্তব ভিত্তি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।
সীমিত জ্ঞান নিয়ে যখন কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, তখন অনেক কাল্পনিক তত্ত্ব গজিয়ে উঠে অনুমানের উপর ভিত্তি করে। একে শুদ্ধ ভাষায় বলে ভাববাদ। চাক্ষুষ ঘটনাও অনেক সময় সত্য নয়। তা মায়াও নয়। যেমন, আমরা চাক্ষুষ করি অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরছে। আর তার ফলেই দিন-রাত হচ্ছে। আর মনে করি, তার ফলেই দিনরাত হয় পৃথিবী নিজে ঘুরছে বলে। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে। এই সত্যটা জানতেই শতসহস্র বছর মানব সমাজকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু কোন এক সুন্দর ভোরে হঠাৎ করে এই সত্যের উপলব্ধি ঘটেনি। কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিওর অক্লান্ত পরিশ্রমে তা সম্ভব হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর পিছনে ছিল মানবজাতির জ্ঞান আহরণের ধারাবাহিকতা। তিলে তিলে সমাজের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। এর উপর নির্ভর করেই নূতন নূতন আবিস্কার সম্ভব হয়। তাঁর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, প্রতিটা আবিস্কারের পিছনে সমগ্র মানব জাতির অবদান থাকে এবং সেই অবদান ঐতিহাসিক। যাইহোক, পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে, এই সত্যটা এখনকার ছেলেমেয়েরা ছোট বয়েসেই জেনে গেলেও, বাস্তব জীবনে কতজন মেনে চলে তা সকলেরই জানা আছে। বিপরীতে অনবরত তাদের মাথায় মিথ্যা ধারণা ঢোকানো হয় নানাভাবে। স্কুল কলেজের পড়া স্মৃতি পটে রাখা হয় শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে, পাশ করে রুজি রোজগার করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। নিজের অন্তর্জগতে তথা মননে, এসব রেখাপাত করেনা বললেই চলে। আমাদের জীবনযাত্রায়, পারিবারিক ও তার বাইরের প্রভাবটাই প্রায় সমগ্র মননকে গ্রাস করে ফেলে। সেভাবেই আমাদের মানসিকতাও তৈরী হয়ে যায়। এই প্রভাব স্কুল-কলেজের শিক্ষার কাছে নগণ্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষা কোন ছাপই ফেলতে পারেনা, উপরন্তু ভাষা শিক্ষার বইগুলোতে কতগুলো আজগুবি ঘটনা গল্পাকারে সুসজ্জিত করে রাখা হয়, যা কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত। এর বাইরের শিক্ষার সাথে যেসব বিষয় মিলে যায়, সেইসব অশিক্ষা বা কুশিক্ষা তখন এমন ভাবে মাথায় চেপে বসে, যার মূল উৎপাটন করা যায় না, বা করা হয় না। তা নিয়েই আমরা প্রাত্যহিক জীবনকে চালনা করি।
একদিকে আদিম মানুষ জানত না সৃষ্টির রহস্য। অপরদিকে তারা এটাও জানত না যে, এই পৃথিবীটাও একদিন ছিলনা। এসব অনেক কিছুই এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও জানে। ‘জানি না’ আর ‘জানা যাবে না’ কথা দুটো এক নয়। আজ যা জানি না তা কোনদিন জানা যেতেই পারে। একজন একটা কিছু না জানলেও অন্য একজন জানতেই পারে। মানুষের বাঁচার তাগিদেই, তাকে জানার কাজটি চালিয়ে যেতে হয়। এই জানার কাজটি করা হয় দুই ভাবে। একটা হচ্ছে সরাসরি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে, যাকে চলতি কথায় বলে চাক্ষুষ জ্ঞান। একে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক জ্ঞান। আরেকটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরিক্ষা নিরীক্ষা।
একজন যা জানে না, তা নিয়ে তাকে পরিহাস করা ঠিক নয়। আবার একজন যা জানে, তা নির্ভুল নাও হতে পারে। পরিক্ষানিরিক্ষায় যা প্রমানিত নয় তা নিয়ে, কোন প্রশ্ন না তুলে মেনে নেয়াকেই বলে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস গড়ে উঠে অনুমানের উপর ভিত্তি করে। ভাষার মাধ্যমে একজনের বিশ্বাস অন্যের কাছে পৌছায়।
বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সভ্যতার বিকাশের প্রথম দিকে, প্রত্যেক ধর্মের ভূমিকাই ছিল বাঁচার তাগিদে। এটা ভুল বলা হয়ে থাকে যে, ধর্ম প্রগতিশীল। প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে আদিম মানুষ প্রবৃত্ত হতে পারেনি তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্যই। এতক্ষণ যে সময়ের কথা বলা হল, তা প্রাক সামন্ততান্ত্রিক যুগের সময়ের কথা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ক্ষমতাসীনেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সূচনা করে। পরবর্তিতে রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা সমাজে দেখা দিলে, রাজারা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। তাদের স্ব স্ব স্বার্থে। এই ব্যবস্থা এখনো সমাজে বিদ্যমান। এর ফলাফল সবাই দেখতেই পাচ্ছে। তাই বলা চলে, ধর্ম কোনদিনই প্রগতিশীল নয়।
©somewhere in net ltd.