| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
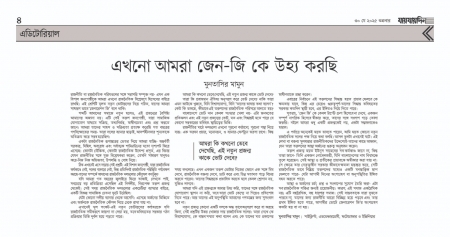
রাজনীতি বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে আমরা এখনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণে হিসেবের বাইরে রাখছি। এই শ্রেণিটি মূলত নতুন ভোটারদের নিয়ে গঠিত, যাদের আমরা সাধারণভাবে ‘জেনারেশন জি’ বলে থাকি।
শব্দটি আমাদের সমাজে নতুন হলেও, এই প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য আমাদের অজানা নয়। এটি সেই তরুণ জনগোষ্ঠী যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়, তথ্যনির্ভর, স্বাধীনচেতা এবং প্রশ্ন করতে জানে। আমরা তাদের সাহস ও সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেছি গত বছরের গণবিক্ষোভের সময়—তারা দলের ব্যানার ছাড়াই, আদর্শহীনতার শূন্যতাকে অতিক্রম করে সরব হয়েছিল।
একটা রাজনৈতিক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, মিছিল, অবরোধ, এবং সর্বাত্মক শাটডাউনের মতো দৃশ্যপট ফিরে এসেছে। কোনটা যৌক্তিক, কোনটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত, এর বিচার যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিশ্লেষকেরা করেন, তেমনি সাধারণ মানুষও করে—নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বোধ নিয়ে।
এবং ঠিক এইখানেই এসে দাঁড়ায় সেই প্রশ্নটি—এই বিশাল জনগোষ্ঠী, যারা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নেই, দলের ব্যানারে নেই, কিন্তু প্রতিদিনই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে—তাদের সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কৌতূহল কতটুকু?
যদি আমরা গত বছরের জুলাইয়ে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়া এসেছিল এই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তরুণ প্রজন্ম থেকেই। সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলোর একচেটিয়া ব্যাখ্যার বাইরে, একটি বিকল্প সামাজিক চেতনা ফুটে উঠেছিল।
যা কোনো দলীয় ব্যানার থেকে আসেনি। এসেছে অর্জনের ভিত্তিতে। এবং অর্জনকে রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।
এখানেই মূল সংকট—এই নতুন ভোটারদের কণ্ঠস্বরকে যদি রাজনৈতিক সমীকরণে জায়গা না দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতের সরকার গঠন প্রক্রিয়ার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।
আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, এই নতুন প্রজন্ম কাকে ভোট দেবে?
তারা কি প্রবাহমান ঐতিহ্য অনুসরণ করে ভোট দেবে? নাকি তারা এমন কাউকে খুঁজবে, যিনি বিশ্বাসযোগ্য, যিনি ‘তাদের ভাষায় কথা বলেন’? কেউ কি ভাবছে, কিভাবে এই তরুণদের রাজনৈতিক পরিসরে আনতে হয়?
বাংলাদেশে ভোটদান কেবল সংখ্যার খেলা নয়—এটা জনমতের প্রতিফলন। এবং এই নতুন প্রজন্মের ভোট, মত এবং সিদ্ধান্তই হতে পারে যে কোনো সরকারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্বের ভিত্তি।
রাজনীতির মাঠে দলগুলো এখনো পুরোনো কাঠামো, পুরোনো পন্থা নিয়ে ব্যস্ত। এক তরফা প্রচার, মনোনয়ন, ও ব্যানার-ফেস্টুনে ভরসা রাখে। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন একজন তরুণ ভোটার নিজের ফোনে একসঙ্গে মিম দেখে, রাজনৈতিক বক্তব্য দেখে, চ্যাট করে এবং ভিন্ন মতামত পড়ে বিচার করতে পারেন। তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে হলে কেবল শ্লোগান নয়, যুক্তিও লাগবে।
আমরা যদি এই প্রজন্মকে আবার উহ্য করি, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন না করি, তবে তারা ভোট কেন্দ্রে না গিয়েও প্রতিশোধ নিতে পারে। আর তাদের এই অনুপস্থিতি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য সুসংবাদ হবে না।
নতুন প্রজন্ম কোনো একটি দলকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে বা করছে কিনা সেই প্রশ্নটির উত্তর খোজার দায় রাজনৈতিক দলের। তারা
দেখে কে বিশ্বাসযোগ্য, কে বাস্তবসম্মত কথা বলেন, এবং কে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করেন।
এবারের নির্বাচনে এই তরুণদের সিদ্ধান্ত হয়তো প্রভাব ফেলবে কে ক্ষমতায় যাবে, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ—তাদের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের সরকার কতদিন স্থায়ী হবে, তার ইঙ্গিতও দিয়ে দিতে পারে।
সুতরাং, ‘জেন জি’ কে কেবল টার্গেট গ্রুপ হিসেবে না দেখে, একজন সম্পূর্ণ নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে, তাদের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলা জরুরি। নইলে আমরা শুধু একটি প্রজন্মকেই নয়, একটা সম্ভাবনাকেও হারাব।
এ পর্যায়ে অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, আমি হয়তো কোনো নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিয়ে কথা বলছি। আসল ভুলটা এখানেই ঘটে। এই লেখা বা বক্তব্য মূলধারার রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যেই—তাদের কাছে আহ্বান, যেন তারা তরুণদের আস্থা অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন।
তরুণ প্রজন্ম হয়তো ইউনুস সাহেবের সব কর্মকাণ্ড জানে না, কিন্তু তারা জানে—তিনি একজন নোবেলজয়ী, যিনি বাংলাদেশের নাম বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন। সেই আস্থা ও প্রতীকের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে তার নেতৃত্বাধীন সরকার কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, সেটি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় তরুণদের মাঝেও একটি মনস্তাত্ত্বিক ছাপ ফেলতে পারে—যা আগামী দিনের অংশগ্রহণ বা অনুপস্থিতির ইঙ্গিত বহন করতে পারে।
আস্থা ও অর্জনের চর্চা, প্রশ্ন ও সংলাপের সুযোগ তৈরি করা—এটা সকল রাজনৈতিক শক্তির জন্যই প্রয়োজনীয়। কারণ এই সমাজ একরৈখিক নয়; এটি বহুরৈখিক, বহুধারণার সমাজ। সেই বাস্তবতাকে যারা বুঝতে পারবে না, তাদের জন্য রাজনীতি আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।
এবং তার প্রথম ইঙ্গিত হতে পারে, আগামীর ভোটে জেনারেশন জি’র অংশগ্রহণ কতটা হয়—বা না হয়।
প্রকাশিত
সম্পাদকীয়, যায়যায়দিন, ৩০ মে ২০২৫
![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:১১
০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:১১
মুনতাসির বলেছেন: এই পার্থক্য রাজনৈতিক মতবিরোধের থেকে তো ভালই মনে হয়! নতুন ভোটারদের মধ্যে ভোট দেয়ার প্রবণতা কখনও কি ছিল? যদি না থাকে বা কম থাকে, তার কোনো কারণ থাকে নিশ্বয়ই।
২| ![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:৪৩
০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:৪৩
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: শুনেন জেন-জিদের মনোভাব গঠন করে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাদের হিরো বানানো হয় তারাই জেন-জির চোখে হিরো আর যাদের ভিলেন বানানো হয় তারাই জেন-জির চোখে ভিলেন।
আমাদের মিডিয়া বলি আর সোশ্যাল মিডিয়া বলি এরাই কনসেন্ট ম্যানুফাকচারিং করে। আর এই কনসেন্ট ম্যানুফাকচারিং অবশ্যই কোনো একটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পারপাস সার্ভ করতে ব্যবহার করে।
জেন-জির ৮০ ভাগ চায় দেশ ছেড়ে পালাতে।
![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ১২:২১
০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ১২:২১
মুনতাসির বলেছেন: আপনার মন্তব্যের সাথে সহমত প্রকাশ করেই বলা সম্ভব - বর্তমান দুনিয়াতে সোশালমিডিয়ার গুরুত্ব সর্বাধিক বলা যেতে পারে। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ বা ভারত, যেখানের কথাই বলা হোক। এই যে আমরা এখানে লেখছি, পড়ছি - সবই কিন্তু মাধ্যম। এখানে আপনার আমার পছন্দ অপছন্দের ব্যপার থাকতে পারে। কিন্তু বস্তবতা ভিন্ন।
জেন জি রা হয়তো দেশের জন্য লায়াবিলিটি হতে চায় না। দেশে কত শতাংশ মানুষ এসেট এবং কত শতাংশ লায়াবিলিটি, সেটা আপনি হিসাব কষে বলতে পারেন। সক্ষমতা সম্পন্য ব্যক্তি তার সক্ষমতার পূর্ন প্রকাশের সুজক পায় বিদেশে। যে কোনো বিষয় হোক সেটা। সবাই ওয়াইট কলার জব যদি নাও করে তবে তারা হয়তো এমএ পাশ পিওনা হওয়ার থেকে উবার চালানো বেশি প্রেফার করতে পারে।
আর আপনি যদি প্রথম সাড়ির মেধাদের কথা ধরেন - স্বাধীন বাংলাদেশের কোন সময়কালে কি ধরনের ইন্ফাস্টাকচার তৈরি হয়েছে যেখানে শত শত প্রকৌশলিরা কাজ করতে পারবেন? এদেশে কোন সময় থেকে গবেষনায় মনযোগ দেয়া হয়েছে? আপনােকে আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারব কেন এরা দেশে থাকবে না। থাকা উচিতও নয়। এই ৫০ বছরে কোনো সরকার দেশের মেধাস্বত্ত্ব ভিক্তিত কোনো অবকাঠামো তৈরিতে কাজ করেনি। উদাহরণ দিতে পারলে মেনে নিব।
তাই মনে হয় নতুন প্রজন্য যারা ১৯৮০ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা কিছুটা হলেও নিজের মর্যাাদা নিয়ে বাচতে চায়। তারা দেশে থাকার মতন কোনো পরিবেশ পায়নি। সামনেও পাবে না বলে ধরে নেয়া যায়। তাই রাজনীতিতে কম্পিউটার সাইন্সের, মাইক্রোাবয়োলজির, এপলাইড ফিজিক্স, ফলিত বিষয় বা প্রকৌশলী বিদ্যাতে পড়া জনগনের সংখ্যা নিতান্ত কম।
কারণ, তারা যানে, এই গেড়া কলে পরে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয়না। এই নীচতার জন্য যে মানসিকতার দরকার পরে তা অনেকটা বংশগতির মতন। কিন্তু এই বংশগতি বিদ্যা রহিত করার চেষ্টা হয়তো নতুন প্রজন্মই করছে। তাই নিজ মেধায় যারা বিদেশ যায়, তারাই দেশের এসেট হবার সম্ভবনা রাখে।
আপনাকে ইদের শুভেচ্ছা।
৩| ![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ১:৩৩
০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ১:৩৩
আধুনিক চিন্তাবিদ বলেছেন: আপনার বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত।
![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ২:০৪
০৮ ই জুন, ২০২৫ দুপুর ২:০৪
মুনতাসির বলেছেন: যারা বিদেশ যায় বা যাবার চেষ্টা করেণ তাদের আমরা অনেক তকমা দেই। সেটা না করার সময় এখন। ভেবেদেখেছেন যারা প্রবাসি, মুটে, মজুর, ওয়ালস্ট্রিটের ক্যাপিটালিস্ট, সিলিকর ভ্যালির খরখুটো আকরে থাকে, ট্যাক্সি চালায়, দোকানে গোস্ত কাটে, আলু ভাজে তারা যদি ভোট দিতে পারে - খেলা আসলেও অন্য দিকে যাবে। আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি, তারা জানিই না নাগরিক সুবিধা কি, সরকাররের প্রয়োজনীতা কি, নাগরিক দায়িত্ব কি!
যে দেশে মেধার কোনো সম্মান নাই সেখানে মেধাবীরা থাকবে কেন?
৪| ![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ বিকাল ৪:২৮
০৮ ই জুন, ২০২৫ বিকাল ৪:২৮
ফেনিক্স বলেছেন:
আপনি নিজে কি Gen-Z, নাকি Gen-প্রশ্নফাঁস?
![]() ০৮ ই জুন, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:১১
০৮ ই জুন, ২০২৫ সন্ধ্যা ৭:১১
মুনতাসির বলেছেন: আমার নাম লিখে গুগল করেন ![]()
৫| ![]() ১১ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:১০
১১ ই জুন, ২০২৫ সকাল ১১:১০
রাজীব নুর বলেছেন: আমাদের দেশে জেন জকি নাই। আছে কিশোর গ্যাং।
©somewhere in net ltd.
১| ০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ৯:০৯
০৮ ই জুন, ২০২৫ সকাল ৯:০৯
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: জেন-জি'র মধ্যে অনেক ভাগ রয়েছে। অনেকে আনসোশ্যাল ও ইন্ট্রোভার্ট। সারাদিন ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে। গেইম খেলে। আরেক অংশ ধর্ম কর্ম পালন করে গভীরভাবে। সবশেষ অংশ সোশ্যাল, বন্ধুপ্রতিম ও আউটগোয়িং।