| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রমাণ মেলে ছান্দোগ্যই সর্বপ্রথম পুনর্জন্মের উদ্ভব ঘটায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্ভাবিত পুনর্জন্ম বিষয়ক সর্বপ্রাচীন সেই শ্লোকটি হলো–
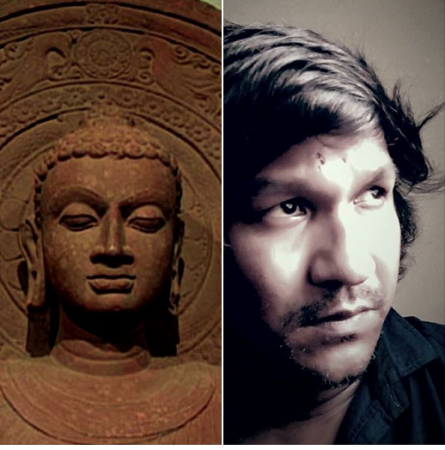
"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ । ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়াযোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চন্ডালযোনিং বা।। (ছান্দোগ্য-৫/১০/৭)।।
অর্থাৎ :
তাদের মধ্যে যারা (পূর্বজন্মে) রমণীয় আচরণ বা পুণ্যকর্ম করে তারা দেহান্তরে শীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোগিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। আবার যারা (পূর্বজন্মে) কপূয়াচরণ অর্থাৎ কুৎসিত বা অশুভ কর্ম করে তাদের শীঘ্রই কুকুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে পুনর্জন্ম হয়।"
এ নবোদ্ভাবিত পুনর্জন্ম ধারণার সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর দর্শন-দিগদর্শন গ্রন্থে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য মনে করছি। তিনি বলেছেন-
‘ঐ যুগের প্রথম প্রচারক সম্ভবত ভাবেননি, যে সিদ্ধান্ত তিনি প্রচার করছেন ভবিষ্যতে তা কত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়ার শক্তিকে রুদ্ধ করে সমাজকে স্রোতহীন এক বদ্ধ জলায় পরিণত করবে। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভের প্রলোভন দেখানো দুঃখপীড়িত মানুষকে আশার কুহক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। এর একমাত্র অভিসন্ধি হলো মানুষ যাতে তার দুরবস্থার জন্য দায়ী এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মুখর না হয়ে ওঠে; একে সংযত রাখার জন্যই এই পুনর্জন্মের প্রলোভন। কিন্তু পুনর্জন্ম তো কষ্ট নিপীড়িত মানুষের কাছে আরও ভয়ঙ্কর। এখানে শুধু বর্তমানের দুঃখ ভুলে যেতে উপদেশ দেওয়া হয়নি, বরঞ্চ আরও বলা হয়েছে যে, সামাজিক বৈষম্য কিছু অন্যায় নয়, কেন না তোমারই গতজন্মের কর্মফলে আজ এই অবস্থা। সামাজিক বৈষম্য না থাকলে আজ যে কষ্ট তুমি করছ, পরজন্মে তার পুরস্কার পাবে কি করে?’- (দর্শন-দিগদর্শন-২, পৃষ্ঠা-২২)।
অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারছেন পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মন্তব্যটি কতো নিরমোহ সত্য বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি বহন করছে।
কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ মানুষের জন্য এক অনন্ত কারাগার-চক্রের সূচনা করেছে। তা কেবল দুর্দশাকে চিরস্থির করে না, সেই চিরস্থায়ী দুর্দশাকে পূজার থালায় সাজিয়ে পূজার্চনা করতে সুবাধ্য করে রাখে মানুষকে।
তাই আমরা প্রত্যেক ধর্মের নির্দেশনায় দেখতে পাই, পরকাল বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস যে ব্যক্তি করে না, সে ব্যক্তি ধার্মিক নয়, নাস্তিক। অর্থাৎ ব্যক্তি হিশেবে সে চোর, বদমাশ, ধর্ষক, খুনির থেকেও নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট।
কিন্তু কেনো?
তার কারণ আমাদের বুঝতে হবে।
একজন লোক, তিনি যদি কারো ক্ষতির উদ্দেশ্যে মিথ্যা না বলেন,
চুরি না করেন, ঘুষ না খান, ধর্ষণ না করেন, এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী পরোপকার করেন, তাহলে শুধু পরকাল বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না বলে, তিনি কেনো নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট হবেন?
এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রীদের কেউ দেবে না। উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে দেবে।
নিন্দা করবে এবং প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে, তাদের শক্তি প্রদর্শন করবে। ক্ষেত্রবিশেষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার মুখ বন্ধ করবে। যারা তাদের অন্ধ ভৃত্য, চ্যালাচামুণ্ডা আছে, সবগুলোকে লেলিয়ে দেবে আপনার পেছনে।
আমরা আবার সেই প্রশ্নে ফিরে যাই, ব্যাক্তিগত জীবনে সৎ একজন ব্যক্তি শুধু পরকাল বা জন্মান্তর বিশ্বাস না করার কারণে কেনো নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট হিশেবে নিগৃহীত হবেন?
এর সোজাসাপ্টা উত্তর, মোল্লা-পুরোহিত-পাদ্রীসহ সমাজ-রাষ্ট্রের কর্তা মশায়দের হাতে চিরকালের শাসন আর শোষণ অব্যাহত রাখা। পরকাল / পুনর্জন্ম না মানলে এবং অতীত জন্মের কর্মের কারণ আপনার বর্তমান জন্মের ফলে বিশ্বাস মেনে না নিলে, আপনার মাথার উপর তাদের উচ্চাসন, মহাসন অটুট থাকবে কি?
টলে যাবে না?
“ভারতীয় দর্শনের বিকাশ-০৫: কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ” রচনায় লেখক ও গবেষক রণদীপম বসুর এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্যগুলো আছে, তার থেকে বেশ কিছু অংশ উদ্ধৃতি করছি।
“যে মোক্ষ বা নির্বাণ ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে চরম লক্ষ্য হিসেবে নির্দেশিত, তাকে বিশেষ কোন জন্মমৃত্যুর পরিসরে আবদ্ধ জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। ফলে এই লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রস্তুতি হিসেবেই স্বীকৃত হয়েছে নির্দিষ্ট কোন জীবনের আগে এবং পরে জীবের আরও বিভিন্ন জন্ম-পুনর্জন্মের অস্তিত্ব। এই জন্মগুলিতে ভোগের মাধ্যমে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করে জীবকে যেতে হয় মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে এবং জন্ম থেকে জন্মান্তরের এই সুদীর্ঘ পথের অতিক্রমণে যাত্রী হলো জীবের দেহাতীত সত্তা। এ প্রসঙ্গে কর্মফলবাদেরও উল্লেখ করতে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলবাদ– এ দুটি ধারণা পরস্পরের পরিপূরক। এই জন্মান্তর আর কর্মফলের স্বীকৃতির ভিত্তির উপর ভারতীয় দর্শনের যে বিশাল সৌধ দণ্ডায়মান, তার প্রাথমিক ধারণার ঔপনিষদিক উন্মেষও ঘটেছিলো উপনিষদীয় ঋষির কোন এক কৌতুহল-মুহূর্তে। অবশ্যই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে প্রথমকালের অন্যতম প্রাচীন উপনিষদ ছান্দোগ্যই সর্বপ্রথম পুনর্জন্ম বিষয়ক ধারণার অবতারণা করে।
বলার অপেক্ষা রাখে না, পুনর্জন্মের সাথে পুর্বজন্মের কর্মফল নামক এক অভূতপূর্ব কল্পনাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে অব্যর্থ ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন ছান্দোগ্যের প্রখ্যাত ঋষি উদ্দালক আরুণি, তারই অব্যর্থ প্রভাব অন্যান্য উপনিষদে তো বটেই, কালক্রমে সেটাই অপ্রতিরোধ্য গতিতে পল্লবিত হতে হতে পরবর্তীকালের গড়ে ওঠা দর্শনগুলোরও অবিচ্ছেদ্য তত্ত্বীয় অংশে পরিণত হয়েছিলো। ভারতীয় দর্শনগুলিতে এই জন্মান্তর ও কর্মফলের স্বীকৃতির অংশীদার কেবল বেদ ও উপনিষদনুসারী ষড়দর্শনই নয়, তার সম অংশীদার বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনও। কেননা বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধ নিজেই বোধিসত্ত্ব রূপে বিভিন্ন জন্ম অতিবাহিত করার পর শাক্যবংশীয় অন্তিম জীবনে বুদ্ধত্ব বা বোধিজ্ঞানের অধিকারী হন।“
উপসংহারে বলতে চাই- অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে তাই সেসব ধর্মের অনুসারীগণ ঈশ্বর-আল্লাহ বা স্রষ্টার পরম অস্থিত্বে বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন। বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থে ওরকম কোনো স্রষ্টার অস্থিত্ব স্বীকৃত নয়, বৌদ্ধরা তাতে বিশ্বাস করেন না। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে আত্মা স্বীকৃত হয়েছে, সেসব ধর্মের অনুসারীরা আত্মার পরম অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, কিন্তু বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থে আত্মা স্বীকৃত নয়, তাই বৌদ্ধদের আছে আত্মায় অনাস্থা। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের মতই পরকাল বা পুনর্জন্ম বা অতীত জন্মের কর্মফল বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে স্বীকৃত, এবং তাতে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন।
এতে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকে তাদের জন্মসুত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় গ্রন্থের উপর বাছবিচারহীন অজ্ঞাত বিশ্বাস দ্বারা চালিত হচ্ছেন। যখন এসো, দেখো, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে গ্রহণ-বর্জন করো" বুদ্ধের মহান আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ মুক্তচোখে দেখতে চাইছে, মুক্তস্বরে বলতে চাইছে সার আর অসার সম্পর্কে মূল্যায়ন ধর্মীকথা, তখন পর্যবেক্ষণবিবর্জিত বিশ্বাসীর দল শিঙ উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে, কুৎসা রটাচ্ছে তাদের নামে, অহরহ হুমকি ধামকি দিচ্ছে।
কেউ কি ভেবে দেখছেন, এতে বোধিচিত্ত অসহায় বোধ করে কি না? গণতন্ত্র আর বাকস্বাধীনতার প্রতিনিধিত্বকারী বুদ্ধ বেঁচে থাকলে আজ মানুষের প্রতি এই দলবদ্ধ পেশীবল ব্যবহার আর নিক্ষিপ্ত নোংরামুখো পচন দেখে আবার পারিল্যেয় নামক বনের মনোরম নির্জনতায় প্রন্থান করতেন না?
©somewhere in net ltd.