| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
 কালনী নদী
কালনী নদী
সিলেট থেকে দিরাইর একটি বহমান নদী, আব্দুল করিমের কালনী।
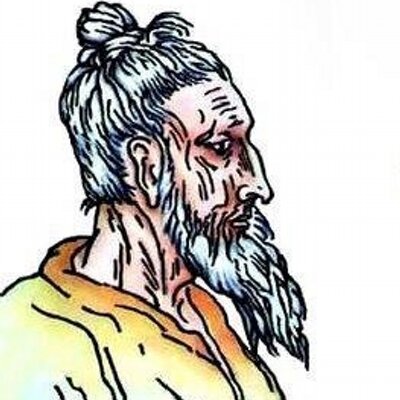
লালনের জাত-ধর্ম নিয়ে বিতর্ক-কৌতুহল-আগ্রহ গত কয়েক দশকের ব্যবধানে বেশ জমে উঠেছে। এতে করে তাঁর গানের ভাব ও শিল্পমূল্য নির্ধারনের চেয়ে ব্যক্তিলালনের আচার-গুপ্তসাধনাই মূলত প্রাধান্য পাচ্ছে। জন্ম-মৃত্যু-জাত-ধর্ম নিয়ে ধূসরতা ও সংশয় থেকে গেলেও লালনের গান ঘাঁটলে তাঁর দর্শন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারনা পরিস্ফুট হয়। জাত নিয়ে গবেষকদের নানা মতান্তর-বাহাস প্রায়শই বিভিন্ন বই-পুস্তক-সাময়িকীতে চোখে পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে এমনটা চলতে-চলতে বছর দুয়েকের মধ্যে সেটাও থিতু হয়ে পড়েছে। এখন চলছে লালন ভাষা অনুষন্ধান এবং তার গানের দর্শনগত ব্যাখ্যা-আলোচনা-বিশ্লেষণ। আর এটাই হওয়া প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিক।
লালনের গানের অন্তর্গূড় তত্ত্ব হচ্ছে মানুষ ভজনা। অথচ জাত-ধর্ম-বর্ন, ভাষা-দেশ-কালের ভিন্নতায় পৃথিবীজুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে দ্বন্ধ-সংঘাত-ভেদাভেদ তৈরি হয়ে আসছে। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্ভবও ওই একই কারনে। আর সেখানটাতেই সোচ্চার ছিলেন লালন সাঁই। ধর্ম-বর্ন-গোত্র-জাতির বিদ্বেষ-হিংসার বিপরীতে তাঁর ছিলো সুস্পষ্ট উচ্চারণ: 'মানুষের নাই জাতের বিচার/এক এক দেশে এক এক আচার'। আবার এ-ও বলেছিলেন- 'যখন তুমি ভবে এলে/তখন তুমি কি জাত ছিলে/যাবার বেলায় কি জাত নিলে/এ কথা আমায় বলো না।' লালন যখন নিজেই জাতপাতকে প্রাধান্য দেননি তাই অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি অব্ন্তরই বলা যেতে পারে।
এক/
মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা-এটাই লালন দর্শনের প্রধান মতবাদ। তবে এ সৃষ্টিকর্তার সন্ধান পেতে হলে আগে নিজের স্বরুপ ভালোভাবে অনুসন্ধান করতে হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাঁর মতবাদ অনুযায়ী, 'আপন খবর না যদি হয়/যার অন্ত নাই তার অন্ত কিসে পাই।' নিজের দেহের মধ্যে 'সাঁইর বারামখানা' রয়েছে উল্লেখ করে লালন জানাচ্ছেন, দেহভান্ডে 'অরুপরতন' কিংবা 'পরমেশ্বর'-এর সন্ধান পাওয়ার জন্য গুরু ভজতে হবে। গুরু না-ধরলে 'আত্না আর পরমআত্না'র ভেদাভেদ কিংবা 'আপ্ততত্ত্ব' জানা সম্ভব নয়। আর 'আপ্ততত্ত্ব' না-জানলে ভজনও হবে না।
ঠিকভাবে ভজন না-হলে 'পারে' যাওয়া অসম্ভব। আর 'পারে' না-যাওয়া মানেই পুরো সাধনজীবন বৃথা। এতে করে একজন সাধকের পতন ঘটে। পতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে একজন সাধককে কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করতে হয়। ব্যবহারিক জীবনাচার, করণ-কারণ, বস্তু নিয়ন্ত্রণ ও নানাবিধ বন্ধুর পথের ন্যায় সাধককে বারংবার বাধাগ্রস্ত করে। আর এসব বাধা ঠেলে গুরু-নির্দেশিত পথে সাধক উজান পথে তরি বাইতে থাকেন। তবে 'কামসাগর'-এর মায়াবী ঢেউয়ের উতরোলে প্রতিনিয়ত তরি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়। 'কামসাগর'-এ অধিকাংশ সাধকের তরি ডুবে যাওয়ার নজিরও রয়েছে। এক্ষেত্রে যারা সুদক্ষ-মাঝি, তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে 'কামকুম্ভীর'-কে বশে এনে কামমোহ বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। এমনটা হলেই তিনি সার্থক ও সফল সাধক হিসেবে বাউল-ফকির সমাজে পরিগণিত হন।
লালন তার একাধিক গানে কামকে নিয়ন্ত্রনে রাখার ওপর সাধকদের প্রতি জোরারোপ করেছেন।গুরু প্রদত্ত নিজের দেহে 'বিন্দুরুপী' যে 'বস্তু' রয়েছে, সেটার ক্ষয় যেন না-হয় সেক্ষেত্রেও খেয়াল রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। কারন যখনই এই 'বস্তু' রুপী 'বিন্দু'-র ক্ষয় হবে তখন থেকেই সাধকের পতনকাল হিসেবে গণ্য করা হবে। তাই যে সাধক যত বেশি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে 'বস্তুু' ধরে রাখার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন, তিনিই বড় সাধক হিসেবে আবির্ভুত হতে পারবেন। এক্ষেত্রে লালনের সাবধান বাণী : 'মায়াতে মত্ত হলে/গুরুর চরণ না চিনিলে/সত্য পথ হারাইলে/খোয়ালে গুরু বস্তু ধন/ মহতের সঙ্গ ধরো/কামের ঘরে কপাট মারো/লালন ভনে সে রুপ দরশনে/পাবি রে পরশ রতন।
লালনের এ-রকম সতর্কবাণী রয়েছে একাধিক গানে। তিনি বলছেন-'কত কত মহাশয়/সেই নদীতে মারা যায়'। 'মহাশয়' মানে 'সাধক'। অর্থাৎ সেই সাধকেরা নারীদেহে সঙ্গমের সময় শুক্রপতন ঘটিয়ে প্রকৃত সাধুসত্তার বিনাশ ঘটান। এরুপ যাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে তাঁদেরকে জীবনভর 'অসাধক' স্বীকৃতি নিয়ে থাকতে হচ্ছে। কারন বাউল-ফকিরদের সঙ্গমকালীন স্খলন হওয়া মানেই গুরু-নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।সিদ্ধসাধুপুরুষরুপে সাধক-সমাজে আখ্যায়িত হতে হলে কখনই শুক্র স্খলন করে এ ধরনের 'অসাধক' পর্যায়ে নামা যাবে না। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বস্তু সাধনা সম্পূর্ণরুপে না-শিখে কখনও 'কামকুম্ভীর'-এর অক্টোপাশে জড়ানো ঠিক নয়। এরকম আভাস পাওয়া যায় লালনের পঙক্তিতে: 'ও মন বাতাস বুঝে ভাসাও রে তরী'। আর বুঝে-শুনে কামসাগরে তরি ভাসাতে চাইলে গুরু সাধন-ভজনের বিকল্প নেই। তাই লালন জানাচ্ছেন :
কবে সাধুর চরণধূলি মোর লাগবে গায়।
বসে আছি আশা-সিন্ধুর তীরে সদাই।।
ভজন-সাধন আমাতে নাই
কেবল মহৎ নামের দেই গো দোহাই
নামের মহিমা জানাও গো সাঁই
পাপীর হও সদয়।।
চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
অহর্নিশি চেয়ে আছে মেঘ ধিয়ানে
তৃস্নায় মৃত্যু গতি জীবনে
হলো সেই দশা আমায়।।
শুনেছি সাধুর করুণা
সাধুর চরণ পরশিলে হয় গো সোনা
আমার ভাগ্যে তাও হলো না
ফকির লালন কেঁদে কয়।।
দুই/
বাউল-ফকির পদাবলি মূলত তত্ত্বভিত্তিক রচনা। সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব পর্যায়ভুক্ত শারীরিক আদল এসব পদাবলির মুখ্য প্রান। লালনের গানও তত্ত্বাশ্রিত রচনা। এসব গানের অধিকাংশের কাঠামো সৃষ্টি ও দেহনির্ভর। সৃষ্টি ও দেহের রহস্যময়তা ও গূড়তত্ত্বভিত্তিক বিষয়াদি নিয়েই গানগুলো রচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর গানে রয়েছে উদার সমন্বয়বাদ। মানবজীবনের রহস্যময়তা এভাবেই ধরা পড়ে লালনের গানে : 'কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়/হলোনা জনম ভরে তার পরিচয়। আঁখির কোণে পাখির বাসা/দেখতে নারে কি তামাশা/আমার এ আঁধলা দশা/কে আর খুঁচায়।। কিংবা যখন লালন রহস্যসংকুল মানবদেহের আবিষ্কার করেন এ-রকম:
কে বানালো এমন রংমহলখানা।
হাওয়া দমে দেখে তারে আসল বেনা।।
বিনা তেলে জলে বাতি
দেখবে যেমন মুক্তামতি
জলময় তার চতুর্ভিতি
মধ্যে থানা।।
তিল পরিমাণ জায়গা সে যে
হদ্দরুপ তাহার মাঝে
কালায় শোনে আঁধলায় দেখে
ন্যাংড়ার নাচন।।
যে গড়েছে এ রংমহল
না-জানি তার রুপটি কেমন
সিরাজ সাঁই কয় নাই রে লালন
তার তুলনা।।
লালনের সংকেতবহুল গানের মধ্যে যে অন্তর্বাণী রয়েছে, তা অনেকটাই ভাবাত্নক। নারীর রজেঃর জোয়ার-ভাটা, নুর-নীর-শুক্র, দম-মৈথুন, পূর্ণিমা-অমাবস্যা-চাঁদ এসব রহস্যদ্যোতক শব্দগুলো অর্থবহ হয়ে গানের পঙক্তিগুলোকে ধারন করে রেখেছে। সাধারন মানুষের কাছে শব্দগুলোর যথার্ত অর্থ দুর্ভেদ্য হলেও সাধনসংশ্লিষ্টরা এ জাতীয় গূঢ় সংকেতের তত্ত্বতালাশ ঠিকই জানেন-বোঝেন।লালনের ইঙ্গিতবহ এসব গানের তত্ত্বই বাউল-ফকির পন্থিদের শাস্ত্রতুল্য উপাদান।
গবেষকদের অভিমত, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরার সঙ্গে লালন রচিত পদাবলিগুলোর যোগসূত্র থাকলেও সেগুলো বাঙালির গানের ভুবনে স্বতন্ত্রমাত্রা যুক্ত করেছে। বাংলার বাউল-ফকির মতবাদ ও দর্শনের যে বিকাশ এবং উত্থান, তার পেছনে লালনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেবল লালনের হাত ধরেই বাউল-ফকির মতবাদ প্রসারিত হয়েছে- এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।
আগেই উল্লেখ করেছি-বাউল সাধনা যেহেতু গোপনসাধনা বিশেষ, তাই সাধকেরা ওই দর্শনের মতবাদ তাদের সাংকেতিক পঙক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। লালনও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারনের কাছে তাঁর রচিত সাংকেতিক পঙক্তিগুলো বোঝা দুরুহ হলেও শিষ্য-দীক্ষিত-রসিকদের জন্য এসব গানের অন্তর্নিহিত ভাব নিরুপন আয়াসসাধ্য নয় মোটেই।
লালন দেহের মধ্যে বিশ্বব্রক্ষান্ডের যাবতীয় উপকরণ লুকিয়ে রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সাধনসংক্রান্ত গানগুলো এ-কথার বিপরীতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি তাঁর দৈন্য ও গোষ্ঠ পর্যায়ভুক্ত গানগুলোও বাউল মতবাদের চারিত্র্য ধারন করে রেখেছে। তাঁর গানেতেই পাই-একজন মানুষের মধ্যেই লোকিয়ে রয়েছেন 'মনের মানুষ' অথবা 'সহজ মানুষ'।ওই মানুষের সাধন-ভজনাই বাউলদের প্রধান কর্তব্য। লালন তাঁর পদাবলিতে মূলত এটাই বারবার বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর দর্শন পুরোপুরিই একটি মানবতাবাদী ধারা। তাঁর গান থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায় :
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।
এই মানুষে মানুষ গাঁথা
গাছে যেমন আলেকলতা
জেনেশুনে মুড়াও মাথা
ও মন যাতে তরাবি।।
দ্বিদলে মৃণালে
সোনার মানুষ উজলে
মানুষ-গুরু নিষ্ঠা হলে
তবে জানতে পাবি।।
এই মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শূন্য কার
লালন বলে মানুষ আকার
ভজলে তারে পাবি।।
লালন ব্যক্তিজীবনে সম্প্রদায়-বর্ন-রোজা-পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে খোজে বেড়াতেন। তাই তাঁর কাছে মানুষই হচ্ছে উপাস্য-দেবতা। পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রচন্ড গুরুবাদী মানুষ। সিরাজ সাঁইয়ের কাছে ফকিরিপন্থায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় গানের পঙক্তিতে গুরুর নাম জুড়ে দেওয়াটাও গুরুবাদী শ্রদ্বার বহিঃপ্রকাশ।
তিন/
'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' বাউল-ফকিরিধারায় অতিপরিচিত শব্দযুগল। এ দুটি শব্দ একটিকে ছাড়া অপরটি কোনভাবেই পরিপূর্ণ নয়। সাধনায় 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ' একে অপরের পরিপূরক ও 'নিরবচ্ছিন্ন প্রানবন্ত সত্তা'। এ দুটি সত্তার মিলনকালীন মহাযোগের সময় যে 'সহজ মানুষ' আবির্ভুত হন, তাঁকে ধরতেই বাউল-ফকিরেরা সাধনা করে চলেছেন। লালন যেমন তাঁর গানে 'সহজ মানুষ' 'অধর মানুষ' কিংবা 'মনের মানুষ' খোঁজার প্রচেষ্টায় ব্যাকুল ছিলেন, তেমনই সেসব অনুসরণ করে তাঁর শিষ্য-ভাবশিষ্যরা একই ধারা অব্যাহত রেখেছেন।
লালনকে আজকাল নানা অভিধায় চিহ্নিত করা হচ্ছে। 'ফকির', 'বাউল', 'সুফি সাধক','ভাববাদী পদকর্তা'-নানাভাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন গবেষকেরা। এঁরা নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে একান্তই তাঁদের মতো করে নানা বিষয়াদি বিশ্লেষণ করছেন। তবে প্রত্যেকেই অন্তত একটা বিষয়ে একমত যে- লালন ছিলেন একজন উঁচুস্তরের দার্শনিক। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার কালে বাংলায় নিজেস্ব দর্শনচর্চা খোব একটা ছিল না। এ অবস্থায় লালন তাঁর সময়ে 'নিরক্ষর' হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে 'স্বশিক্ষিত' হয়ে তৈরি করেছেন নিজস্য মতবাদ, নিজস্ব দর্শন। সে মতবাদ ও দর্শনের গাঁথুনি এতটাই পাকাপোক্ত ছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
লালন প্রবর্তিত মতবাদকে ঘিরে যুগ-যুগ ধরে অজস্র মানুষ উজ্জীবিত হয়ে দীক্ষিত হয়েছেন। লালনের তত্ত্বাশ্রিত গানের মন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্য, জাতপাত ও কুসংস্কারের শিকার ভুক্তভোগী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা দলে দলে লালনের 'সমন্বয়বাদী মানবধর্মে' নাম লিখিয়েছেন। এটি ঠেকাতে তৎকালীন কট্রর ধর্মীয় নেতারা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেউ কেউ নানা কায়দায় 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' দিয়ে লালনের মতবাদ ব্যর্থ করার বৃথা চেষ্ঠাও করেছিলেন!
দর্শন কিংবা তত্ত্বগত বিচারে লালনের গান এতই প্রভাববিস্তারী যে শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তা স্বমহিমায় চির-উদ্ভাসিত। দুশতাধিক বছর পর এখনও তাঁর রচিত গানগুলো ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে বাঙালির ভাব পিপাসা মিটিয়ে চলেছে।
লালনের বিপুল গানের রাজ্যে প্রবেশ করলে এক ধরনের আত্নমগ্নতা তৈরি হয়। এমনতর গভীর, নির্জন, চির রহস্যময় ও আত্নমগ্নতার সমন্বয়ে তৈরি লালনের গানের বিচিত্র ভুবন। এ ভুবনের মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে তাই লালন-অনুরাগীরা বলি কেন দেশবিদেশের সংগীত-পিপাসুরা আত্ন-আস্বাদনের জন্য এক আলাদা পথের সন্ধান করে চলেছেন নিরন্তর।
মহাত্মা লালন ফকির - শ্রী বসন্তকুমার পাল এই বইটি লালন ফকিরের আসল জীবনী গ্রন্থ। বইটি পেতে এখানে ক্লিক করুন
মূল লেখক সুমনকুমার দাশ (লালন, তাঁর গান, তাঁর কথা)
তথ্যসুত্র-
১ সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত লোকায়ত লালন(কলকাতা: পুস্তক বিপনি,১৯৯৮ দ্বি.সং)
২ শক্তিনাথ ঝা, লালন সাঁইয়ের গান (কলকাতা: কবিতা পাক্ষিক,২০০৫)
৩ আবুল আহসান চেীধুরী (সম্পা.), লালনসমগ্র(ঢাকা:২০০৮, পাঠক সমাবেশ)
৪ ফরহাদ মজহার, ভাবান্দোলন (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮)
![]() ০৫ ই এপ্রিল, ২০১৬ সন্ধ্যা ৭:৪৬
০৫ ই এপ্রিল, ২০১৬ সন্ধ্যা ৭:৪৬
কালনী নদী বলেছেন: ঠিক বলেছেন ভাই, এই লিখাটা দুইবার চেস্টা করার পরেও প্রথম পাতায় যায় নি! সেই সময়।
©somewhere in net ltd.
১| ১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১০:৪৬
১৯ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সকাল ১০:৪৬
বিদ্রোহী ভৃগু বলেছেন: মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।
এমন মানববাদী সাধুক আর ২য়টি কই?????????????????
+++++++++