| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
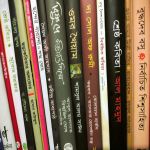 মেহেদী হাসান তামিম
মেহেদী হাসান তামিম
কবিতা ব্যক্তিগত মত নয়, বেদনাঘাত বা আনন্দৌন্মুখতা হতে যে উচ্চারণ বেরিয়ে আসে তাই কবিতা। -কাহলিল জিব্রান
♥ রবীন্দ্রনাথ vs নজরুল; ইতিহাসের আলোয়, সত্যের দামামায়♥
---------মেহেদী হাসান তামিম
(নীচের হ্যাসট্যাগে ক্লিক করে পূর্ববর্তী পর্বগুলো পড়া যাবে)
পর্ব - ৬
নজরুল-রবীন্দ্রকে নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে প্রচুর কাজ পেয়েছি। সবচেয়ে আশার বিষয় হলো অন্তত আমরা তাঁদেরকে ভুলে যাইনি। সেগুলো পড়তে গিয়ে দেখেছি, উনারা যা লিখছেন, যে রেফারেন্স দিচ্ছেন সবই সত্য কিন্তু কেন জানি কোন রচনাতেই আমার প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর শতভাগ সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। গভীর থেকে উত্তর পাব আশায় আরো গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি। এই একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে আমার পাঁচটি বছর কেটে গেল।
তবে সময় গেলেও আমার ভাবনাতে হয়ত কিছুটা ম্যাচিওরিটি এসেছে, কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে আর কিছু প্রতীতি জন্মেছে।
আজকের রবীন্দ্র-নজরুল বিতর্ক শুধু কিছু রেফারেন্স, কিছু দলিল, ইতিহাস দিয়ে প্রমান করতে চাইলে সমাজ যে তা বিশ্বাস করবে, আমি তা মনে করিনা, কারন সমাজের বিশ্বাসগুলো যে বহুদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে, মিথ্যেগুলো যে নিজ শক্তিতেই আজ আমাদের অন্তরে তেজোদীপ্ত পদচারণ করছে, আমরা সে বিশ্বাসগুলো যে জন্ম থেকে বয়ে নিয়ে চলেছি। সেই সমাজের অংশ যে এই আমি মেহেদী হাসান তামিমও।
কলকাতার ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার আগস্ট, ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ড. আহমদ শরীফের এক লেখার জবাব দিতে গিয়ে গবেষক- কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম. ১৯৪৩) বলছেন : ‘কিন্তু তুলনা যদি কাউকে ছোটো করার জন্যে, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের, তখন ব্যাপারটা অশ্লীল ও অরুচিকর হয়ে ওঠে। সাহিত্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, প্রত্যেকে তার স্বাতন্ত্রিকতায় চিহ্নিত। ... একুশ বছর বয়সে কবি জীবন সমাপ্ত করেছেন—ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সদ্য-উন্মীলিত। লোরকার আটতিরিশ-ঊনচল্লিশ বছর বয়সে জীবন ও কবিজীবন শেষ হয়েছে—ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি রবীন্দ্রনাথ?
রবীন্দ্রনাথ ক্রমপরিণত, নজরুলের উন্মীলন ও নিমীলন দুই-ই দ্রুত। উদ্দাম ও বিদ্যুচ্চকিত।
(‘বরং নিজেই তুমি’, চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬১)।
রবীন্দ্রনাথ নেহায়েত রাজকপালে, শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের গতি প্রকৃতি ধারা নজরদারি করার জন্য আছে। কোথাও সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই তা সাথে সাথে শুধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দুখু মিয়ার কপাল তো চিরজীবী দুখে ভরা। নজরুলের লেখার যারা প্রকৃত অনুরক্ত গবেষক-লেখক তারা ছাড়া আর কাউকে শান্তিনিকেতনী ভূমিকায় যে দেখা যায় না। হয়ত সে কারণেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যরাজ্য যতটুকু সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন হবার কথা তার সিকিভাগও এখনো হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে তা যে হবে না, তাও বা কে নিশ্চিত করবে!
বিভিন্ন বিদগ্ধ সাহিত্য আলেচনায় পড়েছি নজরুলের তুলনা করা হয় বিদ্রোহী ব্রিটিশ কবি লর্ড বায়রনের (১৭৮৮-১৮২৪) সঙ্গে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-’৭৪) তাঁর নজরুল সম্পর্কিত লেখায় তাঁর কাব্যধারার তুলনা করেছেন রুডইয়ার্ড কিপলিঙের (১৮৬৫-১৯৩৬) সঙ্গে। অথচ কেউ কখনও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বায়রন বা কিপলিঙের সঙ্গে তুলনা করেননি।
রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক দর্শন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে, হবে। তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি নিজেই মহাশক্তির প্রেরণা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতেন, কেউ তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে।
তবে সেই মহাশক্তিটা কী?
জগত-সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্ত্রক, তিনিই। তিনি মানব মনের কবিরূপের সত্যের পূজা কতখানি তা সন্ধান করেন। কবিতা কবির কাছে তখন হয়ে ওঠে শাস্বতসুন্দর। Poetic truth, বাংলায় হল কাব্যসত্য। এই সত্যকে খুঁজেই প্রকৃত কবি একজীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কেউ জীবনে মাত্র চার'টি লাইন লিখেও সত্যকবি হয়ে উঠতে পারেন, কেউবা একটি শব্দ না লিখেও কবি হয়ে উঠেন- শুধু সত্য আর সুন্দরের ধারক হয়ে। কবিতা তাই চিরযৌবনা, অম্লান থাকে শতবর্ষ পেরিলেও।
কাব্যসত্য বা Poetic truth বৈজ্ঞানিক সত্য বা scientific truth-এর পরিপূরক, প্রতিস্পর্ধী নয়।’
- কবিতা ও আধুনিকতা, কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৭।
‘‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ (১৩১০) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উত্সারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগত্সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির-আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।’
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্যের প্রায় পুরোটাই আধ্যাত্মিকতা ও ভাবের মিশ্রণ। কেউ কেউ বাউল কবি লালন শাহ’র (১৭৭৪-১৮৯০) প্রতিরূপ দেখতে পান রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালে লন্ডনে তাঁর বক্তৃতামালায় লালন শাহকে একজন ‘আধ্যাত্মিক কবি’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছিলেন,
" তিনিই ‘আত্মা’কে আবিষ্কার করেছেন এবং ‘মানুষ’-এর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। 'I discovered that 'man' from the songs of Lalon who said that "
(এই মানুষে আসে সে মন ...)" the 'man' is within yourself where are you searching Him?"
বিশ্বসৃষ্টির গৌরবজ্জ্বল বেয়েচলা রবির বিভিন্ন রচনাতে ঘুরেফিরে এসেছে। ‘গীতাঞ্জলি’র (১৯১২) ভাববাদ ইউরোপীয় কবিদের একসময় আলোড়িত করেছিল, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভেতর খুঁজে পেয়েছিলেন ঐশ্বরিক প্রচ্ছায়া। রবীন্দ্রগবেষক আবু সয়ীদ আইয়ুবের ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৮) গ্রন্থে বলেছেন, এই ‘ভাববাদ’কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘আধুনিকতা’, তাঁর ভাষায় আধুনিকতা ‘কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।’ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর ভাববাদী চেতনার স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই এসে যায়।
নজরুল কিন্তু ভাববাদী দর্শনের কবি ছিলেন না, ছিলেন সমাজসংগঠক কবি। ব্রিটিশ তাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে তিনি তাঁর গানে-কবিতায় নাড়া দিয়েছেন সমাজকে, মানুষের চেতনা জগতকে।
রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনের ষাট বছর অতিক্রম করেছেন, নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়ে গেছেন, তখন সবে নজরুল কলম ধরেছেন। ফলে দু’জনের ভেতর তুলনা করাটা রীতিমতো অযৌক্তিক, অপাংক্তেয়, অশ্লীল এবং হাস্যকর তো বটেই।
যারা সম্প্রদায়গত কারণকে দাঁড় করিয়ে সমাজে অস্থিতিশীলতা, বিভাজন তৈরী করে রাখতে চেয়েছেন এতে করে তাদের লাভ হয়েছে কিন্তু পুরো বাঙ্গালি সমাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সে ঘা এখন এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যা হয় শুধু খারাপ হবে নতুবা শুধুই ভালো হবে, সেরে উঠবে। এর থেকে মাঝামাঝিতে অবস্থানে যাবার কোন সুযোগ নেই।
উত্তর প্রজন্ম অবশ্যই জানে, নজরুলের স্ত্রী ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং কবি নিজে ছিলেন বরাবর অসাম্প্রদায়িক। একজন ছিলেন ভাববাদের রাজা, আরেকজন সমাজবাদের।
আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধে বলছেন, ‘দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম - এরা সকলে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্র-আচ্ছন্ন বাংলা সাহিত্যে তা প্রথম ফাটল ধরিয়েছিল। গদ্য-পদ্যের সংক্রাম, সংস্কারমুক্তি, শারীরিকতা, দুঃখ, অমঙ্গলবোধ, সামাজিক সাম্য, বাস্তবতা-পরবর্তীদের জন্য এসব বিষয়ের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন তারাই। তবু এদের মধ্যে বিষয় ও বিন্যাসে যেটুকু রবীন্দ্রানুসৃতি ছিল, পরবর্তীরা তাও ছিন্ন করেছন। তারা এমন কিছু নিয়ে এলেন, যাকে বলা যায় অ-রৈবিক, উত্তর-রৈবিক, এমনকি প্রতিরৈবিক।’
- নির্বাচিত প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।
রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর উত্তরসূরিদের কাব্য-দর্শন এবং আধুনিক কাব্য সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। সে ধারায় নজরুল একজন অন্যতম সদস্য। তবে কি কারণে, কি আশাতে আমরা রবীন্দ্রনাথ - নজরুলের সাহিত্যের ‘তুলনামূলক’ বিচার করি, তা অনুধাবন করতে হলে বেশ গভীরে যেতে হবে।
সেই গভীর বিষয়ে প্রবেশ করবার আগে কিছু উদ্ভট ভ্রান্ত্র ধারণাগুলো খুব কম সময়ে শেষ করতে চাই। যে ভুল ধারণাগুলোর সমাধান আমরা চোখ মেললেই পেয়ে যাব, তাকে আমি বেশী সময় দিতে চাইনা। নোবেল পুরস্কার ও নজরুলের অসুস্থতা বিষয়ে মূর্খ কূপমণ্ডূক সমাজের যে সংশয়, যে গুঞ্জন তা না জেনেই, না বুঝেই - আরো কিছু সমগোত্রীয় প্রজাতির মুখনিসৃত বাণী, মানসিক বৈকল্যের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই তাদের মনোজগতের অন্ধ বিচরণ।
রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সম্পর্ক কিংবা অন্য কিছু অবান্তর প্রশ্নের উত্তরগুলো, যাদের ঘটে নেহায়েত এক ছটাক বা তা হতে আরো যৎকিঞ্চিত ঘিলু আছে তাঁরাও সামন্য কয়েকটি অকাট্য যুক্তি ও প্রমান পেলে সে ধারণাগুলো ঝরা পাতার মতো হাওয়াতে উড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন।
তবে!
হ্যা, তবে সমস্যা বলা হোক, সন্দেহ সংশয় যা-ই বলা হোক, সেটা অন্য জায়গায়। সেই বিষয়টি যেহেতু বাঙালির (বেশীভাগ ক্ষেত্রেই তা বাংলাদেশী বাঙ্গালি) মননে প্রোথিত হয়েছে, শিকড়-বাকড় ছড়িয়েছে- এটা শুধু কিছু অকাট্য দলিল, প্রমানাদি দিয়ে দেখালে তা অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে না। বিষয়টি যে-
"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকরণ।"
আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে কিছু তত্ত্ব, কিছু ধারনা, কিছু বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করব - আমরা গভীরে যাবার চেষ্টা করব তা দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদৌতে কোনরুপ বিরোধিতা করেছিলেন কি না!
(চলবে.....)
#রবীন্দ্র_নজরুল
#tamimbooks
#tagore_islam 
©somewhere in net ltd.