| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |
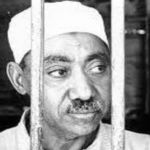 সৈয়দ কুতুব
সৈয়দ কুতুব
নিজের অজ্ঞতা নিজের কাছে যতই ধরা পড়ছে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি ততই অবিশ্বাস জন্মাছে!
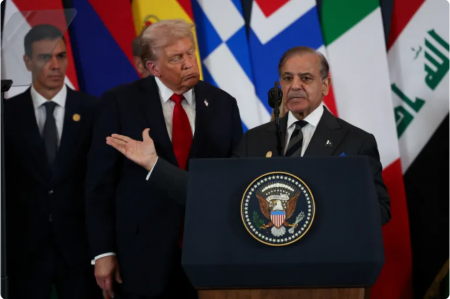
ওয়াশিংটনের করিডোরে এখন একটা কথা ঘুরছে : পাকিস্তান আবার কাজের হয়ে উঠছে। মার্কো রুবিও যখন বলেন যে ইসলামাবাদের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বাড়ানোর সুযোগ দেখছেন তারা, তখন এটা শুনতে যতটা সরল মনে হয়, আসলে ততটা নয়। কারণ ওয়াশিংটনের হিসাবটা কখনোই একমুখী থাকে না। এটা একটা পুরনো খেলা, যেখানে আমেরিকা তার প্রতিটি পদক্ষেপ মাপে অন্তত তিনটা বোর্ডে : দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য আর চীনের বিরুদ্ধে তার বৈশ্বিক অবস্থান। পাকিস্তানকে আবার কাছে টানার পেছনে আছে একটা বড় ভূরাজনৈতিক ফাঁক, যেটা তৈরি হয়েছে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার নাটকীয় প্রত্যাহারের পর।
কাবুল এখন তালেবানের হাতে, আর ওয়াশিংটনের সেখানে আর কোনো সরাসরি উপস্থিতি নেই। কিন্তু চীন আর রাশিয়া সেই শূন্যতা ভরাট করতে তৎপর, ইরান তার নিজের প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকার দরকার একটা প্রক্সি পয়েন্ট, এমন একটা দেশ যার মাধ্যমে সে এই অঞ্চলে তার কান খোলা রাখতে পারে, নাড়িনক্ষত্র বুঝতে পারে। পাকিস্তান ঠিক সেই জায়গায় বসে আছে ভৌগোলিক অবস্থানে, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে, আর আফগান রাজনীতির গভীর জ্ঞানে।
ট্রাম্পের বাগরাম এয়ারবেস ফেরত চাওয়ার দাবিটা এই হতাশারই প্রকাশ। সেটা ফিরে না পেলে তাকে দরকার হবে এমন কাউকে যে তালেবানের সঙ্গে কথা বলতে পারে, যে আফগান সীমান্তে নজর রাখতে পারে। পাকিস্তান সেই ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত, এবং ইসলামাবাদও জানে যে এই মুহূর্তে তার হাতে একটা দর কষাকষির সুযোগ আছে। তাই বিরল খনিজের নমুনা পাঠানো হচ্ছে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কথা উঠছে, আর রুবিও বলছেন যে অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। কিন্তু এই সম্পর্কের ভিত্তিটা হলো প্রয়োজন, বিশ্বাস নয়। ওয়াশিংটন পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না, কখনো করেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার পাকিস্তান দরকার : সেটাই আসল সত্য।
তবে আমেরিকার আরেকটা বড় সমস্যা আছে: ভারত। গত দেড় দশক ধরে ওয়াশিংটন নয়াদিল্লিকে তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের মূল স্তম্ভ বানানোর চেষ্টা করেছে। কোয়াড জোট থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা চুক্তি, সব জায়গায় ভারতকে সামনের সারিতে রাখা হয়েছে: মূল লক্ষ্য চীনকে ঘিরে ফেলা। কিন্তু সম্পর্কের মধ্যে এখন ফাটল দেখা দিচ্ছে। ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে, মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রেখেছে, আর মোদি বেইজিং সফরও করছেন। ওয়াশিংটনের কাছে এটা বিরক্তির কারণ হলেও তারা ভারতকে পুরোপুরি চাপ দিতেও পারছে না, কারণ চীন মোকাবিলায় ভারত তাদের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মেক ইন ইন্ডিয়া যখন পূর্ব এশিয়ার সস্তা রপ্তানি মডেল অনুসরণ করছে, তখন আমেরিকার উৎপাদন খাত ভারতকেও এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। ট্রাম্পের শুল্কনীতি আর ভিসা বিতর্ক এই অস্বস্তিরই উপসর্গ।
এখানেই পাকিস্তান হয়ে ওঠে একটা ভারসাম্যের হাতিয়ার।ওয়াশিংটন চায় ভারত বুঝুক যে সে একমাত্র বিকল্প নয়। যদি নয়াদিল্লি খুব বেশি স্বাধীনভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমেরিকা ইসলামাবাদের দিকে ঝুঁকতে পারে। এটা একটা পুরনো খেলা যেখানে দুই প্রতিবেশী শত্রুকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। রুবিও যখন বলেন যে "আমাদের অনেক দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়," তখন তিনি মূলত বলছেন যে আমেরিকা কাউকে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য মনে করে না, এবং সেজন্যই সবার সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে সম্পর্ক রাখবে। ভারত যতই পরিপক্ব হোক, আমেরিকা তার কৌশলে পাকিস্তানকে একটা চাপ সৃষ্টির উপাদান হিসেবে ধরে রাখতে চায়। এটা ঠান্ডা, হিসাবি কূটনীতি যেখানে আবেগের জায়গা নেই।
নয়াদিল্লি এই পুরো বিষয়টাকে কীভাবে দেখছে? ভারত জানে যে আমেরিকা-পাকিস্তান সম্পর্ক তার জন্য সবসময়ই একটা উদ্বেগের বিষয় ছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় থেকেই আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিয়ে এসেছে, যা শেষ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন যখন রুবিও বলছেন যে এই সম্পর্ক ভারত-আমেরিকা বন্ধুত্বের ক্ষতি করবে না, তখন ভারত সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। কিন্তু ভারত প্রকাশ্যে কিছু বলছে না, কারণ তার নিজের হিসাবও জটিল। ভারত চায় আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী থাকুক, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন তার কৌশলগত স্বাধীনতা খর্ব না করে।
রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, চীনের সঙ্গে বাণিজ্য, মধ্যপ্রাচ্যে নিজস্ব অবস্থান : ভারত এসব জায়গায় নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। তাই জয়শঙ্কর যখন রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করবেন, তখন তিনি সরাসরি কিছু বলবেন না, কিন্তু একটা বার্তা পৌঁছে দেবেন যে ভারত আমেরিকার জুনিয়র পার্টনার নয়, সে একটা স্বাধীন শক্তি। আর যদি আমেরিকা মনে করে যে পাকিস্তানকে কাছে টেনে ভারতকে চাপ দিতে পারবে, তাহলে ভারত তার নিজের বিকল্প খুঁজবে । হোক সেটা রাশিয়া, চীন বা অন্য কেউ।
কিন্তু ভারতের আসল উদ্বেগ হলো পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। আমেরিকা যদি আবার পাকিস্তানকে আধুনিক অস্ত্র দেয়, প্রযুক্তি স্থানান্তর করে, তাহলে সেটা সরাসরি ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। পাকিস্তান-সৌদি প্রতিরক্ষা চুক্তিটাও ভারত লক্ষ করছে, কারণ রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মানে পাকিস্তানের আর্থিক সহায়তা বাড়বে, যা তার সামরিক ব্যয়ে প্রতিফলিত হবে। তাই ভারতের কৌশল হলো নীরবে প্রস্তুতি নেওয়া : সীমান্তে সতর্কতা বাড়ানো, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা, এবং একই সঙ্গে আমেরিকাকে বোঝানো যে পাকিস্তান কখনো বিশ্বস্ত মিত্র হয়নি, হবেও না।
ইসলামাবাদ এই মুহূর্তে একটা সুযোগ দেখছে, যা সে নষ্ট করতে চায় না। দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তান আমেরিকার কাছে ছিল একটা সমস্যা , সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়দাতা, দ্বিচারী মিত্র। এখন হঠাৎ করে সে আবার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। পাকিস্তান জানে যে এই সম্পর্কটা ভঙ্গুর, যেকোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। তাই সে দ্রুত যা পারে আদায় করে নিতে চায় । অর্থনৈতিক সহায়তা, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর। বিরল খনিজ সম্পদ হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় দরকষাকষির হাতিয়ার। পাকিস্তান আমেরিকাকে বলছে, "তুমি যদি চীনের খনিজ নির্ভরতা কমাতে চাও, তাহলে আমার দিকে তাকাও।" এটা একটা শক্তিশালী যুক্তি, কারণ আমেরিকা সত্যিই চীনের খনিজ একাধিপত্য নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু পাকিস্তানের এই পরিকল্পনায় একটা মারাত্মক সমস্যা আছে আর সেটা হলো বেলুচিস্তান।
বেলুচিস্তানে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় খনিজ মজুত আছে, কিন্তু সেখানেই সবচেয়ে বড় বিদ্রোহও চলছে। স্থানীয় জনগণ দশকের পর দশক ধরে অভিযোগ করে আসছে যে তাদের সম্পদ লুট হচ্ছে, কিন্তু তাদের কিছুই দেওয়া হচ্ছে না। বেলুচিস্তান মাইনস অ্যান্ড মিনারেলস অ্যাক্ট এই ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, কারণ এটা ইসলামাবাদকে প্রাদেশিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী দল থেকে শুরু করে ধর্মীয় সংগঠন পর্যন্ত সবাই এর বিরোধিতা করছে। যদি পাকিস্তান স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই খনিজ উত্তোলন শুরু করে, তাহলে বিদ্রোহ আরও তীব্র হবে, এবং সেই অঞ্চল আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। আর অস্থিতিশীল অঞ্চল থেকে খনিজ সরবরাহ বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। তাই পাকিস্তানের যে সম্পদ দিয়ে সে আমেরিকাকে আকৃষ্ট করতে চাইছে, সেই সম্পদই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
পাকিস্তানের আরেকটা বড় সমস্যা হলো তার নিজের রাজনৈতিক অস্থিরতা। দেশটা দীর্ঘদিন ধরেই সামরিক বাহিনী আর বেসামরিক সরকারের টানাপোড়েনে ভুগছে। অর্থনীতি ভেঙে পড়ার পথে, আইএমএফের ঋণের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া। এমন পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতিতে বড় সাফল্য দেশের মানুষের কাছে খুব একটা অর্থবহ নয়। সাধারণ মানুষ দেখছে যে তাদের জীবনযাত্রার মান নিচে নামছে, কিন্তু সরকার বড় বড় চুক্তির গল্প শোনাচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকটকে আরও গভীর করছে। আর যদি দেশের ভেতরে স্থিতিশীলতা না থাকে, তাহলে বাইরে যত চুক্তিই হোক, তা টেকসই হবে না।
পাকিস্তান এটাও জানে যে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন মানে চীনের সঙ্গে সম্পর্কে একটা টান পড়া। চীন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী, সিপিইসি প্রকল্প তার অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ইসলামাবাদ খুব বেশি আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে বেইজিং অসন্তুষ্ট হবে। আবার যদি চীনকে খুশি রাখতে গিয়ে আমেরিকাকে দূরে ঠেলে দেয়, তাহলে এই সুযোগ হাতছাড়া হবে। এটা একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্যের খেলা, এবং পাকিস্তান এখন পর্যন্ত সেটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ধরনের ভারসাম্য দীর্ঘমেয়াদে বজায় রাখা খুবই কঠিন।
এই পুরো পরিস্থিতির ভেতরে একটা বড় প্রশ্ন লুকিয়ে আছে : এই সম্পর্কের ভিত্তিটা কী? ওয়াশিংটন পাকিস্তানের দিকে ফিরছে কারণ তার একটা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন আছে, ভারতকে একটু চাপে রাখা দরকার, আর আফগান শূন্যতা পূরণ করতে হবে। পাকিস্তান সাড়া দিচ্ছে কারণ তার অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, আর আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ভারত চুপ করে আছে কারণ সে জানে যে খোলাখুলি বিরোধিতা করলে আমেরিকা আরও বেশি পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে পারে। এই তিনটা দেশই তাদের নিজস্ব হিসাব মেলাচ্ছে, কিন্তু কেউই আসলে একে অপরকে বিশ্বাস করছে না। এটা একটা সম্পর্কের নাটক, যেখানে সবাই নিজের স্বার্থ দেখছে।
আর এখানেই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। যখন সম্পর্কের ভিত্তি হয় প্রয়োজন, বিশ্বাস নয়, তখন সেই সম্পর্ক যেকোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। আমেরিকা যদি আফগানিস্তানে অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়, বা ভারতের সঙ্গে তার মতপার্থক্য মিটে যায়, তাহলে পাকিস্তান আবার পুরনো সমস্যা তালিকায় ফিরে যাবে। পাকিস্তান যদি অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা আনতে না পারে, বা বেলুচিস্তানে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার খনিজ কূটনীতি ভেস্তে যাবে। আর ভারত যদি বুঝতে পারে যে আমেরিকা তাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, তাহলে সে তার নিজস্ব পথে হাঁটা শুরু করবে। এই তিনটা দেশই একটা নাজুক ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এবং যেকোনো একটা ভুল পদক্ষেপ পুরো খেলাটাই বদলে দিতে পারে।
ওয়াশিংটনের যা চাই আফগান অঞ্চলে প্রভাব, ভারতের ওপর চাপ আর চীনের খনিজ আধিপত্যে ফাটল । সেসব কি পাকিস্তানের মাধ্যমে আদায় হবে? পাকিস্তানের যা চাই: অর্থনৈতিক ত্রাণ, আন্তর্জাতিক বৈধতা আর সামরিক সহায়তা । সেসব কি আমেরিকার সাময়িক প্রয়োজনের ওপর ভর করে দীর্ঘমেয়াদে টিকবে? ভারতের যা চাই: কৌশলগত স্বাধীনতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা আর বৈশ্বিক মর্যাদা। সেসব কি এই ত্রিমুখী খেলায় নিরাপদ থাকবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনো পরিষ্কার নয়। যেটা পরিষ্কার, তা হলো এই তিন খেলোয়াড়ই একটা অস্থির মাঠে খেলছে, যেখানে নিয়ম বদলায়, মিত্র বদলায়, আর আজকের অংশীদার কালকের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে। খেলাটা চলছে, কিন্তু কে জিতবে সেটা সময়ই বলবে।
সূত্র: এই লেখাটি University of Hertfordshire-র একাডেমিক Eric Shahzar-এর Al Jazeera-তে প্রকাশিত "A Pakistan foreign policy renaissance? Not quite" (২৬ অক্টোবর ২০২৫) নিবন্ধ থেকে অনুপ্রাণিত।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:১৭
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:১৭
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: দেখা যাক।
২| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ৮:০২
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ৮:০২
মেঠোপথ২৩ বলেছেন: ভু রাজনৈ্তিক যত খেলাই হোক , জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হয়ে গেলে আর কোন রাজনৈ্তিক দল আর আমাদের দেশকে আরেক দেশের গোলামে পরিনত করতে পারবে না । বাংলাদেশের মানুষ হয়েও এই সব ব্লগার একাত্তর, কামাল এর মত প্রকাশ্যে আরেক দেশের গোলামী করার সাহসও দেখাবে না।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:১৮
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:১৮
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: আচ্ছা। কি হবে সামনে দেখি।
৩| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:২৯
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:২৯
রাজীব নুর বলেছেন: আন্তর্জাতিক বিষয় গুলো আমি বুঝি না।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩৪
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩৪
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: আপনার গুরু বুঝেন ।
৪| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩৪
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩৪
জেনারেশন একাত্তর বলেছেন:
পড়ে কি বুঝলেন? নাকি পড়ে দেখেননি?
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৫২
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৫২
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: পড়ার পরই শেয়ার করেছি। তবে মুল লেখা পড়ে আপনি দেখতে পারেন আমার লেখাটি কেবল লাইন বাই লাইন অনুবাদ নয় ।
ঘুম কম হয় আপনার দেশের টেনশনে মনে হয়; এদিকে কেউ একজন টিকে থাকার লড়াই করছে সামুতে । আপনার বদদোয়ার কারণে উনার ভিউ কমে গেছে । ![]() ।
।
৫| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৫
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৫
জেনারেশন একাত্তর বলেছেন:
আমাকে অকারণে কটু কথা যে বলে, সে অবশ্যই অপদার্থ; অপদার্থরা সামুতে এসে তাদের ২য় শ্রেণীর জ্ঞানের গার্বেজ ছড়ায়, ওরা নিজেই বুঝে না কি লিখছে!
পাকিস্তান আমেরিকান ডিপ্লোমেটদের একটি খেলনা ও প্রমোশান পাবার যায়গা। পাকিস্তান আমেরিকাকে দিয়ে আমাদেরকে ইডিয়ট জাতিতে পরিণত করেছে। শেষে ইউসুসও পাকিস্তানকে সাহায্য করলো আমাদেরকে ধ্বংস করতে।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৮
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৮
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: থাক আর মন খারাপ করিয়েন না ।,
৬| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৭
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৩৭
জেনারেশন একাত্তর বলেছেন:
ট্রাম্প নিজের ছেলেদেরকে ব্যবসার জন্য আফগানিস্তানে যেতে চায়; ওর ছেলে দুটো তারেক ও কোকোর মতো।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪০
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৪০
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: ট্রাম্প যতই খারাপ হউক পুতিন থেকে ভালো। রাশিয়া ওয়ার করাতে বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়েছে ।
৭| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৫৯
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৪:৫৯
জেনারেশন একাত্তর বলেছেন:
রাশিয়ায় লোক পাঠানোর জন্য ২ আদম বেপারী ব্লগার নিশ্চয় কাজে লেগে গেছে!!
রাশিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছে পুটিন: মানুষকে চোর ডাকাতে পরিণত করেছে; রাশিয়ানরা এখন ইউক্রেনের লোকদের মতো চোর ও মাফিয়া।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:৪৬
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:৪৬
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: বাংলাদেশের Passport ও ভিসা খারাপ সুচকে যাওয়ার পিছনে রাশিয়া- ইউক্রেনের ওয়ারে লোক যাওয়া , টিটিপির হয়ে ওয়ার করা পাকিসতানে একটা দায় আছে । সব জায়গায় মুজাহিদ তকমা লেগে যাইতেসে।
৮| ![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:১১
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:১১
জেনারেশন একাত্তর বলেছেন:
সামুর ইডিয়টরা ( তথাকথিত কবি, গল্প লেখক, মুক্তিযোদ্ধা ও পংগুরা ) খেয়াল করেনি যে, আমি মানুষকে গালি দিই না, আমাকে গালি দেয়া সঠিক নয়।
![]() ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:৪৯
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫:৪৯
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: আপনি সোশাল মিডিয়া ইউজ করতে জানেন । ।
৯| ![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:৩৭
৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১০:৩৭
আদিত্য ০১ বলেছেন: লেখক বলেছেন: বাংলাদেশের Passport ও ভিসা খারাপ সুচকে যাওয়ার পিছনে রাশিয়া- ইউক্রেনের ওয়ারে লোক যাওয়া , টিটিপির হয়ে ওয়ার করা পাকিসতানে একটা দায় আছে । সব জায়গায় মুজাহিদ তকমা লেগে যাইতেসে।
বাংলাদেশের Passport ও ভিসা খারাপ সুচকে যাওয়ার পিছনে রাশিয়া- ইউক্রেনের ওয়ারে লোক যাওয়া নয়। ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের Passport ও ভিসা খারাপ সুচকে গেছে। নিরপেক্ষ আর হইতে পারবেন না। দেশের অর্থনীতি এত তলানীতে, আইনশৃংখলা এত খারাপ। এখনও আপনারা জাশি জঙ্গিদের সাপোর্ট দিয়েই যাচ্ছেন, আপনাদের সাপোর্টের কারনে আজ দেশে জাশি পাকি বীর্যদের হাতে যা দেশের সাধারন মানুস এর কুফল ভোগ করছে খুব বেশি খুব বেশি।
আপনারা তথা গেঞ্জিদের ওপর ভর দিয়ে জাশি জঙ্গীরা পাকিদের আর্মীদের কাছ থেকে ট্রেইনিং নিয়ে স্নাইপার জুলাইয়ে এতগুলা মানুস মেরেছে, তা বাইরের সব দেশ জানে বাংলাদেশ এখন হায়েনা তথা জাশি জঙ্গীদের হাতে। বিএনসিসি নাম করে ৫০ হাজার স্নাইপার ট্রেইনিং দিচ্ছে জামাতের টীম, যে অস্ত্রগুলো থানা থেকে লুট হইছিলো
![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১১:১৫
৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ১১:১৫
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: আপনি ভুল জানেন।
১০| ![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ২:৫৫
৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ২:৫৫
রাজীব নুর বলেছেন: পোষ্টে আবার এলাম। কে কি মন্তব্য করেছেন সেটা জানতে।
![]() ৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৪০
৩০ শে অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৪০
সৈয়দ কুতুব বলেছেন: জয় পাকিসতান ।
©somewhere in net ltd.
১| ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১:৫০
২৯ শে অক্টোবর, ২০২৫ রাত ১:৫০
কামাল১৮ বলেছেন: ভারত বাগরামে শক্ত ঘাঁটি বানিয়েছে।ভারত এখন পরাশক্তির পর্যায়ে আছে।আমেরিকাকে ছেড়ে কথা বলছে না।