| নির্বাচিত পোস্ট | লগইন | রেজিস্ট্রেশন করুন | রিফ্রেস |

পৃথিবীর সব রোগের চিকিৎসা নেই। সব রোগ নির্ণয় করা যায় তাও ঠিক নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে ‘ডিউ টু আন নোন ইটিওলজী’। অর্থাৎ কেন হলো শনাক্ত করা যাচ্ছে না। এখানেই একজন চিকিৎসকের সীমাবদ্ধতা তা তিনি যত বিজ্ঞ ডাক্তারই হন না কেন। তিনিতো আর দেবতা নন।
এখন যদি আপনি একজন চিকিৎসককে প্রশ্ন করে বসেন, ‘আপনি কিসের চিকিৎসক, আমার কি রোগ হলো সেটাই আপনি বলতে পারলেন না। কত আশা ভরসা নিয়ে আসলাম।’
সেটা হবে আপনার দুর্ভাগ্য। আর বলতে হবে আমাদের নিতান্তই সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
‘ডিউ টু আন নোন ইটিওলোজি’, টার্মটি মেডিকেল শিক্ষার্থীরা শুরু থেকে জেনে আসে। ক্ষেত্র বিশেষ এ কোন কোন রোগের কারন কী, বা কিভাবে ওষুধ কাজ করে, বা কেনো এমন হয় এসব রহস্যময় ব্যাপার চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল দেখে প্রথমে পরিচিত হয় থার্ড ইয়ার থেকে ইন্টার্ন লাইফে। এমনকি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্তও এই রহস্যময় অনিবার্য কারণ ‘আন নোন অরিজিন’ মাথায় রাখতে হয়।
যেমন ছোট একটা উদাহরণ দেই ব্রেইনের এপিলেপসি বা মৃগী রোগ নিয়ে। এক্সেক্টলি ঠিক কী কারণে ব্রেইন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে রোগী কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যায়, তার সঠিক কারণ স্পষ্ট করা নেই। যদিওবা এর অনেক হাইপোথেসিস আছে।
এ রকম একটা টপিক প্রথম প্র্যাকটিক্যালি পরিচিত হই ঢাকা মেডিকেলে ইন্টার্ন করার সময়। পঁয়ত্রিশ উর্ধ্ব এক ভদ্র মহিলা বারবার চিকিৎসা করে পরে একদিন মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হলেন। মাঝে মধ্যে তার পা ফুলে যায় বলে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছুই পাওয়া গেল না।
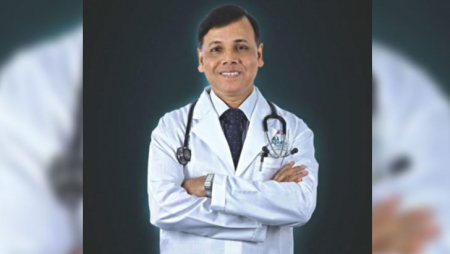
অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান স্যার
আমরা তখন ট্রেনিং নিচ্ছি প্রয়াত অধ্যাপক মেডিসিন ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান স্যারের কাছে। স্যার রাউন্ডে এসে বিস্তারিত পড়ালেন পেশেন্টকে নিয়ে। আমি ছিলাম বেড ডক্টর। স্যার বললেন, ‘ইডিয়প্যাথিক ইডেমা’। তুমি এটা কাল ডেবিডসন থেকে পড়ে আসবে।
আমি আদ্যপ্রান্ত পড়ে গিয়ে প্রেজেন্ট করলাম। সব আউড়ে শেষতক বললাম, ‘ডিউ টু আননোন ইটিওলজি’। অর্থাৎ কেনো হচ্ছে জানা সম্ভব হয়নি আজও।
স্যার এরকম আরো দু একটা আন নোন ইটিওলজি নিয়ে প্রশ্ন করলেন, আলোচনা করলেন।
স্যারের সঙ্গে এই আমার পরিচয় শুরু। স্যার কেন জানি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি গর্ববোধ করতাম দেশ সেরা একজন মেডিসিন ও লিভার বিশেষজ্ঞ আমাকে সঙ্গে রেখে যত্ন করে পড়াচ্ছেন।
একদিন ভাইরাল ফিভারে আমি দুই দিন ওয়ার্ডে যেতে পারিনি। স্যার খবর করেন। আমি পরে জ্বর নিয়ে স্যারের রাউন্ড ক্লাসগুলোতে এটেন্ড করি। স্যার হেসে হেসে বললেন, ‘ভাইরাল ফিভার একটা অসুখ হলো? ওষুধ খেলে সাত দিনে কমবে, নইলে এক সপ্তাহ লাগবে। ’
স্যারের রাউন্ড কখনো মিস করিনি আমরা।
আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা লাগতো স্যারের রাউন্ডে। প্রতিটি বেডে গিয়ে নিঁখুতভাবে বেড ডক্টরের কাছ থেকে হিস্ট্রি আদায় করতেন। আদ্যোপান্ত পড়িয়ে দিতেন। বেড সাইড ডায়াগনোসিস ও মেডিকেশনে উৎসাহিত করতেন। বলতেন, ‘এখন রিফ্লেক্স গ্রো আপ না হলে আর হবে না।’
রিফ্লেক্স মানে হলো রোগী রিসিভ থেকে শুরু করে সুস্থ করে তোলা ডিসচার্জ দেয়া পর্যন্ত সব ধাপ ‘রোল অব থাম্ব’ অনুযায়ী একের পর এক অনুসরণ করা।
রাউন্ড শেষ হলে আমাদের যে দুই-তিনজনকে স্যার পছন্দ করতেন তাদের নিয়ে মেডিসিন ওয়ার্ডের পাশে ছোট্ট এন্ডোসকপি রুমে যেতেন স্যারের সঙ্গে এন্ডোসকপিতে এটেন্ড করতে।
ভিডিও এন্ডোসকপি তখন কেবল প্রথম ঢাকা মেডিকেলে শুরু হয়েছে। স্যার বাংলাদেশের একজন এক্সপার্ট এন্ডোস্কপিস্ট।
কখনো কখনো স্যার ক্যামেরায় ধরা পড়া রোগীর পাকস্থলীর ক্ষতস্থান ক্যানসার গ্রোথ, আলসার, স্টেনোসিসগুলো আমাদের বড় মনিটরে দেখাতেন। সেগুলো পড়া দিতেন। পরের দিন পড়া আদায় করতেন।
একবার আমার আম্মার এন্ডোসকপিও করেছিলেন তিনি। আম্মা মুজিব স্যার সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘এতো ভালো মানুষ, এতো ভালো ব্যবহার ডাক্তারদের কখনো দেখিনি’।
সে সময় স্যার দুর্লভ কঠিন কঠিন কিছু পেশেন্ট নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্যারের সরকারি বাসভবনে নিয়ে যেতেন। সঙ্গে থাকতো স্যারের প্রিয় ও মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রেসিডেন্ট স্যার নিজে ক্লাস নিতেন। এতো ব্যস্ততার মাঝেও তিনি এই শিক্ষাদানের সময়টা বের করে নিতেন।
মুজিব স্যার সবার সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। খুব সোশ্যাল ছিলেন। নানান সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতেন।
একদিন তিনি আমাদের ক'জনকে নিয়ে বেইলি রোডে একটি জনপ্রিয় মঞ্চ নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি ভুলার মতো না। এটাই ছিলো আমার প্রথম কোন মঞ্চ নাটক দেখা।
ইন্টার্নের সময় একদিন খুব সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় হঠাৎ করে ওয়ার্ড পরিদর্শন এ আসলেন। ডেঙ্গু জ্বর ও আতংকে পুরো রাজধানী আতংকিত। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তখন খোলা হয়েছে টুয়েন্টিফোর আওয়ার ইমার্জেন্সি সার্ভিস কর্নার । সাড়ে ছ'টা বাজে। ওয়ার্ডে কেউ নেই। ডেঙ্গু কর্নারে আমার নাইট ডিউটি ছিলো।
ফ্রেশ হতে যাবো অমনি দেখি পুলিশ, প্রটোকল, সাংবাদিক সঙ্গে স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়। সঙ্গে সঙ্গে এপ্রোন লাগিয়ে আমি মন্ত্রী মহোদয় স্যার কে প্রতিটি বেড ঘুরে ঘুরে ব্রিফ করে। তখন সব ইন্টার্ন কে নিজের বেড পেশেন্ট ছাড়াও বাকি সব বেড পেশেন্ট এর হিস্ট্রি জানা থাকতে হতো।
খানিকক্ষণ পর সকাল ৮টায় বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তোফায়েল স্যার এসে বিষয় জেনে খুব খুশি হন। বাংলাদেশ টেলিভিশন রাত ৮টার প্রচারিত সংবাদে আমাকেও দেখায়। এটা দেখে হঠাৎ মুজিব স্যার হঠাৎ ফোন করলেন, ‘সাঈদ তোমাকে টিভিতে দেখলাম, তুমিতো হিরো হয়ে গেলে! এটাই হলো তোমার পাওনা। সেবা করলে এভাবেই প্রতিদান পাওয়া যায়।’
ইন্টার্ন শেষের পরও স্যারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো। সময় সুযোগ হলে স্যারের চেম্বারে যেতাম। স্যারের রোগী দেখার স্টাইল দেখতাম। স্যারের এতো রোগী আর এতো জনপ্রিয়তা ছিল যে, স্যারকে অনেক জায়গায় গভীর রাত অবধি চেম্বার করতে হতো। এর মধ্যে কয়েকটা চেম্বার ছিলো গরিব রোগীদের জন্যে।
সেই গাজীপুরের পাড়া গাঁ থেকে শুরু করে সদরঘাটের সুমনা ক্লিনিক, পুরান ঢাকার ঢাকা ক্লিনিক, ধানমণ্ডির ল্যাবএইড এবং এপোলো হসপিটালে স্যার নিয়মিত রোগী দেখতেন।
তাছাড়া ঢাকা মেডিকেল ও সাবেক পিজি হাসপাতালে নিখুঁতভাবে সরকারি দায়িত্ব পালন তো ছিলই। সবখানেই প্রায় দেড়শতাধিক রোগী স্যারকে দেখতে হতো। কেউ কেউ এমনি আসতো স্যারের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে। আমি দেখতাম স্যার এতো ক্লান্ত তবুও কী সুন্দর হাসিমাখা মুখে সবাইকে দেখছেন।
আশ্চর্য প্রতিটি রোগী এতো প্লিজড থাকতো স্যারের ওপর। রোগীদের কাছে তিনি ছিলেন ফেরেশতা সমতুল্য।
আমি স্যারকে বলতাম, ‘স্যার কিছু কিছু রোগী তো এমনি আসে, কেবল আপনাকে দেখতে।’
স্যার মৃদু হেসে বলতেন, ‘আমি জানি। তোমাদেরও হবে। আমাকে ফলো করো।’
স্যার খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন। স্যারকে কখনো রাগতে দেখিনি। তবে রাগলে স্যার কিছু বলতেন না। চুপ থাকতেন। প্রসঙ্গ পাল্টে নিতেন। তখন আমরা বুঝে নিতাম স্যার রাগ করেছেন।
যেদিন ইমার্জেন্সি এডমিসন থাকতো স্যার নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। স্যার বলতেন, এখন শেখার সময়। জেনে নেয়ার সময়। এ সুযোগ তোমাদের আর আসবে না। আমাদের গাইড করতেন আইএমও, রেজিস্টার ও সিএ স্যারেরা।
দিন-রাত টানা এডমিশন চলতো। পরদিন সবাইকে নিয়ে শুরু হতো স্যারের মেগা রাউন্ড। জাস্ট আটটায় শুরু হয়ে দুপুর দুইটা, একটানা।
আমরা স্যারের পেছন পেছন ডায়েরি বা হ্যান্ডনোট নিয়ে বেডে বেডে গিয়ে রোগী দেখছি আর স্যারের প্রতিটি কথা লিখছি। সবার যার যার কেইস হিস্ট্রি, ফাইন্ডিংস মুখস্থ বলছে, গায়ে সাদা এপ্রোন, গলায় স্টেথো।
মাঝখানে একবার হয়তো বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক তোফায়েল স্যার আসতেন। তোফায়েল স্যারকে সবাই যেমন ভালবাসত তেমনই ভয় পেতো। সবাই দোয়া করতো মেডিসিন ফাইনাল ভাইবা পরীক্ষায় অধ্যাপক তোফায়েল স্যার যাতে সারাক্ষণ বসে থাকেন।
অনেক রোগী থাকতো পোস্ট এডমিশনে। সারা বাংলাদেশের হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ থেকে রেফার্ড হওয়া সব ক্রিটিকেল রোগীতে ওয়ার্ডের বেড ফ্লোর এমন কি বারান্দা সয়লাব হয়ে যেত। তার মধ্যে আবার ভি আই পি, সি আই পি এমনকি ভি ভি আই পি পেশেন্ট ও।
২৪ তম বিসিএস দিয়ে গ্রামে জয়েন করলাম। একেবারেই গ্রাম। জয়েন করেই স্যারকে ফোন দিলাম। স্যার বললেন মন দিয়ে সেবা করো। গ্রামের মানুষদের এরকম সেবা করার সুযোগ আর কখনো পাবে না। আমরাও গ্রামে সেবা করে এসেছি। এর সুফলও পাবে।
কঠিন কেইস পেলে সরাসরি স্যারকে ফোন দিতাম। স্যার খুশি হতেন টেলিফোনে বুঝিয়ে দিতেন। আমার চেম্বারের কিছু ক্রিটিকেল কেইস স্যারের এড্রেস দিয়ে ঢাকা পাঠাতাম। স্যার যত্ন করে সে গুলো দেখে দিতেন। পরে টেলিফোনে সে বিষয়ে ডিসকাস করতাম।
সাইকিয়াট্রিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এ চান্স পাবার পর ফোন দিলাম স্যার কে। স্যার বললেন, ‘এটা আমার প্রিয় সাবজেক্ট অবশ্যই পড়বা। আমি চাই তুমি পড়’।
তারপর আর পেছন ফিরে তাকাইনি। ওই সাবজেক্টেই পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি। আমার ইন্টারেস্টিং কেইসগুলো নিয়ে মাঝেমধ্যে স্যারের সঙ্গে ডিসকাস করতাম। ফেইসবুকে আমার কেইস হিস্ট্রিগুলো স্যার পড়তেন। স্যার চাইতেন আমি যেনো কেইস হিস্ট্রি লিখি। মানুষ যাতে সাইকিয়াট্রি নিয়ে সচেতন হয়।
স্যারের সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয় এই কদিন আগে। হেসে হেসে বলেছিলাম, স্যার এপোলোতে চেম্বার করবো। সাইকিয়াট্রি কেইস দেখবো।
তিনি বললেন, ‘শিওর, তবে এখানে দুজন আছেন। সমস্যা নাই, তোমার হবে। কিন্তু তার আগে তোমার পোস্টিং ঢাকায় আনতে হবে। এখানে প্রতিদিন চেম্বার করতে হয়।
 ’
’
আচমকা সেদিন বেলা এগারোটার দিকে ফেসবুকে এক ডিএমসিয়ান অগ্রজ হঠাৎ এক পোস্ট দিলেন, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান স্যার নেই। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে অপারেশন জটিলতায় মারা গেছেন।
এটা পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে আমি চুপ হয়ে যাই। বিশ্বাস করতে পারিনি। ওয়েট করতে থাকি ফেসবুকের পরবর্তী আপডেট। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে চোখ বুঝে দোয়া করছিলাম, আল্লাহ নিউজটা যেনো ভুল হয়। ফেসবুকে তো কত ভুয়া মৃত্যু সংবাদ থাকে।
না, মুজিব স্যার সত্যি মারা গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এক ইতিহাসের মৃত্যু হলো।
মুজিব স্যার ছিলেন দেশের সম্পদ। তাঁর সঙ্গে যাঁদের মেশার সৌভাগ্য হয়েছে কেবল তারাই বলতে পারবেন, তিনি কী ছিলেন, কেমন ছিলেন। ফেরেশতাতুল্য মানুষ। আমার ক্লিনিকেল এক্সামিনেশন ইন্টার্নের সময় তাঁর কাছ থেকেই শেখা।
প্রতি ঈদ, পুজা-পার্বনে স্যারের সঙ্গে আমাদের শুভেচ্ছা কথাবার্তা, এসএমএস আদান প্রদান হতো। মৃত্যু সংবাদ শুনার পর থেকে আমি মোবাইলে স্যারের পাঠানো সেই এসএমএস গুলো পড়তে থাকলাম এক এক করে। চোখের পানি সংবরন করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস হচ্ছিলো না স্যার আর শুভেচ্ছা মেসেজ আমাকে দেবেন না। দূর আকাশের ‘তারা’ হয়ে স্যার তাঁর অগণিত ছাত্রদের দেখছেন।
সারের মৃত্যু হয়েছিলো অপারেশন টেবিলে অপারেশন জটিলতায়। মেডিকেলের ভাষায় একে বলে "মেডিকেল ইরর" (Medical_Error)। এটা চিকিৎসকদের কাছে একটা তিক্ত সত্য। এই তিক্ত সত্য সবাইকে মানতে হবে, মানতে হয়।
চিকিৎসায় ভুল কেন হয়?
মেডিকেল ইরর (Medical Error) ইচ্ছে করে কোন চিকিৎসক করেন না। হঠাৎ করে ভুলক্রমে এটি হয়ে যায়। একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত, অকল্পনীয়।
ডাক্তাররাও তো মানুষ। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই তারাও ভুলের উর্ধ্বে নন। কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসা করতে গিয়ে এরকম কিছু হলে (যদিও বা তা খুব কম) রোগী বা তার স্বজনরা মানতে চান না। ব্যাপক সহিংস আচরণ করেন। ডাক্তারকে মারধর থেকে শুরু করে,হাসপাতাল ভাংচুর, গুম, হত্যা, ফেসবুক কাঁপিয়ে তুলা এহেন কিছু নাই যে করেন না। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো বিভ্রান্ত হয়ে ও হুজুগের বশে এসব করেন।
ভুল চিকিৎসায় ক্ষতিপূরণ
বাইরের দেশে এরকম মেডিকেল এরর এর প্রতিক্রিয়ায় রোগীর স্বজনদের এসব কিছুই করতে দেখা যায় না। এমন অভিযোগ হলে বা এমন কিছু হলে প্রথমেই চিকিৎসকরা নিজেরা এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তদন্ত করেন, প্রমান পেলে স্বীকার করেন, ক্ষমা চান। ফুল রেসপন্সিভিলিটি নেন, ক্ষতিপূরণ ও দেন। এমনকি যেকোন শাস্তি মাথা পেতে নেন।
এটা নির্ধারিত হয় মেডিকেল এররের কোয়ালিটি ও টাইপ দেখে। এ ব্যপারে রোগী বা তার স্বজনরা কখনোই আইন হাতে তুলে নেন না। মারামারিতে লিপ্ত হন না। তাদের সে সুযোগটিও নাই।
বাংলাদেশে চিকিৎসকদের নিয়ে বিভ্রান্তি
কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। এখানে কিছু কিছু রোগী ও তার স্বজনরা শুরুতেই ডাক্তার সম্পর্কে প্রচণ্ড অবিশ্বাস, সন্দেহ আর নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে আসেন। মনে করেন এই বুঝি ডাক্তার ইচ্ছে করেই তাকে বা তার রোগীকে ভুল চিকিৎসা দিয়ে মেরে ফেলবেন। কেবল চিকিৎসা ক্ষেত্রেই নয়, বলা যায় কম বেশি সব ক্ষেত্রেই এখন কিছু কিছু সেবাগ্রহীতা দের মাঝে এরকম প্রচণ্ড অবিশ্বাস বিরাজমান।
দৈনন্দিন জীবনে কম বেশ আমাদের সবাই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাই। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই আমাদের চোখেমুখে দেখা যায় ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক উপর এক ধরনের অবিশ্বাস/শত্রুতামূলক মনোভাব । সারাক্ষণ এ নিয়ে আমরা থাকি উদ্বিগ্ন। আর সে জন্যেই এ ব্যপারে চুন থেকে পান খসলেই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই আমরা, ডাক্তার ও নার্সদের উপর রোগীর স্বজনরা চরমভাবে চড়াও হয়ে যাই, লাঞ্ছিত করতে শুরু করে।
ভুল তথ্যে চিকিৎসক ও নার্সদের ওপর নির্যাতন
বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি উপজেলা জেলা সদর এবং এমনকি মেডিকেল কলেজে যে পরিমাণ ডাক্তার, নার্স নির্যাতন, লাঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তা রীতিমত আশংকাজনক। এমন কি কখনো কখনো ডাক্তাররা হত্যা, গুম, ধর্ষনের ও শিকার হচ্ছেন অহরহ । মোবাইল কোর্ট বসিয়ে জেল জরিমানা, কোর্টে হাজির করা ডাল ভাত হয়ে গেছে।
আর সবক্ষেত্রেই এর কারণ হিসেবে দাবি করা হয়, ইচ্ছে করে চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অবহেলা, ভুল ওষুধপাতি, ভুল চিকিৎসার প্রয়োগ,গাফিলতি, অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি যাবতীয় মনগড়া অভিযোগ, আর গুজব। অথচ তদন্ত করলে দেখা যায় এগুলোর শতকরা ৯৯ ভাগ মিথ্যা, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এমনও নজির আছে, ওয়ার্ডে ফ্যানের সুইচ চালু করে দেয়নি বলে লেডি ডাক্তারকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের আর কোথাও এমনটি হচ্ছে বলে আমার জানা নেই।
বিদেশে চিকিৎসায় ভুলে প্রতিদিন গড়ে কতজনের মৃত্যু হয়?
অথচ ইউরোপ-আমেরিকার চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা ধরেন। আমেরিকার এক স্টাডিতে গবেষকরা দেখেছেন, তাদের দেশে কেবল মাত্র "মেডিকেল ইরর" (অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স, যন্ত্রপাতির ভুল ব্যবহার, অপারেশনে এক অঙ্গ কাটতে গিয়ে ভুলক্রমে অন্য অঙ্গ কেটে ফেলা, ছুরি কাঁচি পেটে রেখে সেলাই করা ইত্যাদি) এর কারনে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ রোগী মারা যায়..!
অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ছয়শতাধিক রোগী মারা যাচ্ছে চিকিৎসাজনিত জটিলতায়। অথচ শুনেছেন বা দেখেছেন আমেরিকার কোথাও মাথায় ব্যাজ লাগিয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে, দল বল নিয়ে হামলে পড়তে কোন ডাক্তার বা ক্লিনিকে কিংবা কোন প্রফেসর এর চেম্বারে? দেখেছেন কোন সাংবাদিককে তদন্তের আগেই কোন নিউজ করতে? তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করতে।
চিকিৎসায় ভুলে হুমায়ূন আহমেদ ও ডা. মুজিব স্যারের মৃত্যু
এই যে সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত গ্যস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, আমাদের অতি প্রিয় শিক্ষাগুরু মহান ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভুইঞা স্যার মারা গেলেন সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে অপারেশন জটিলতায়, আপনারা কি দেখেছেন সিঙ্গাপুরের কোথাও কোন সাংবাদিক বা সাধারণ মানুষ হাসপাতাল বা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের ওপর হামলে পড়তে? কান্নাকাটি, চিৎকার, আহাজারি করে কোন সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য বা বিবৃতি দিতে? দেখেননি।
কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে এটার তদন্ত করছেন। কারন এমনটি হবার কথা না ছিল না। মুজিব স্যার ছিলেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন প্রখ্যাত লিভার বিশেষজ্ঞ। তার অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে ফরেইন কান্ট্রির।
তিনি অনলাইনেও বিভিন্ন দেশের রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। তাছাড়া সিঙ্গাপুরের ওই হাসপাতালের অনেক স্পেশালিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন মুজিব স্যারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠজন। যা ঘটেছে হয়ে গেছে তা এক্সিডেন্ট।
একই ঘটনা ঘটেছে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ এর চিকিৎসার বেলায়। ধারণা করা হয়ে থাকে মেডিকেল ইররেই তার মৃত্যু হয়েছে। কই আমেরিকার রাস্তায়তো বাঙালি বা আমেরিকান কাউকে তো ঝাড়ু, লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিল মিটিং করতে দেখা যায়নি। ইনফ্যাক্ট তাদের কাউকে তো হাসপাতালে গেটের কাছেই ভীড়তে দেয়নি পুলিশ, ভিতরে ঢুকে কিছু বলাতো দূরে থাক।
রোগীর সুস্থতা ডাক্তারের কাছে গর্বের
একটা ব্যাপার বলি, কোনো চিকিৎসকই চান না তার রোগীটির বিন্দু মাত্র ক্ষতি হোক। রোগীর সুস্থতা ডাক্তারের কাছে গর্বের বিষয়। চ্যালেঞ্জের বিষয়। তাছাড়া চিকিৎসকদের একটা থ্রিল থাকে কিভাবে কত সহজে রোগীর দেহটাকে রোগ মুক্ত করা যায়।
আরেকটি কথা চিকিৎসা সেবা একটি ইবাদত। ডাক্তাররাও এটা ইবাদত হিসেবেই নেন। তারপরও এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যায়, ঘটে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে। তাই বলে কি আপনি অবিশ্বাসী হয়ে ডাক্তারকে মেরে ফেলবেন, হাসপাতাল ভেঙে ফেলবেন, গুম করে ফেলবেন, নারী ডাক্তারকে ধর্ষন করবেন?
আমরা দিন দিন কেন এতো অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছি? মনে রাখবেন, আবারো বলছি কোনদিন কোন ডাক্তার ইচ্ছে করে বা জেনে শুনে বুঝে তার রোগীর ক্ষতি করে না। যেটুকু হয়ে যায় তা স্রেফ একটা এক্সিডেন্ট। তাদের মাধ্যমেও এক্সিডেন্ট হতে পারে। আর এর জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে মেডিকেল আইন আছে।
মানুষের আয়ু নির্ধারিত
শেষ একটি কথা, মানুষের আয়ু নির্ধারিত। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বা ভগবান একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আপনাকে আমাকে পাঠিয়েছেন এবং সময় শেষ হলে তিনি আপনাকে উঠিয়ে নিবেন। তা হয়তো কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে। সুতরাং কিছু বলতে হলে আগে তাকেই বিনীতভাবে বলুন। তার কাছেই প্রার্থনা করুন। কারণ তিনিই তো আপনাকে রোগাগ্রস্ত করে চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়েছেন।
ডাক্তার পিটিয়ে কার লাভ?
অবিশ্বাসী মন নিয়ে কেবল ডাক্তারকে গালিগালাজ আর পেটালে কোন লাভ হবে না। আপনি হয়তো বলবেন ডাক্তারকে পেটালে তারা সতর্ক হবে, ভুল কম হবে। কিন্তু আপনার ধারণা নিতান্তই বোকামি। এভাবে ডাক্তার পেটাতে থাকলে, ডাক্তারের প্রতি অবিশ্বাস বাড়তে থাকলে, কিংবা কৌশলে বাড়াতে থাকলে, মানুষ পঞ্চাশ বা একশো বছর পর আর ডাক্তারি পড়তে আসবে না। এতে ক্ষতি কার? আমার, আপনার বা আগামী প্রজন্মের সবার।
লেখক: ডা. মো. সাঈদ এনাম
(ডিএমসি, কে-৫২), সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যান্ড ইউএইচএফপিও, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
প্রকাশিতঃ দৈনিক যুগান্তর
©somewhere in net ltd.